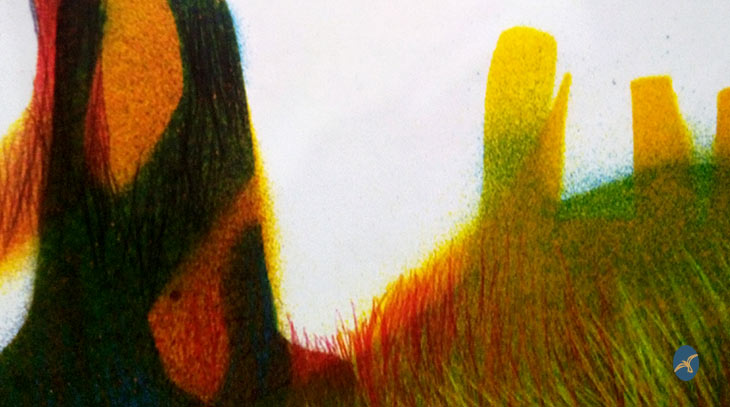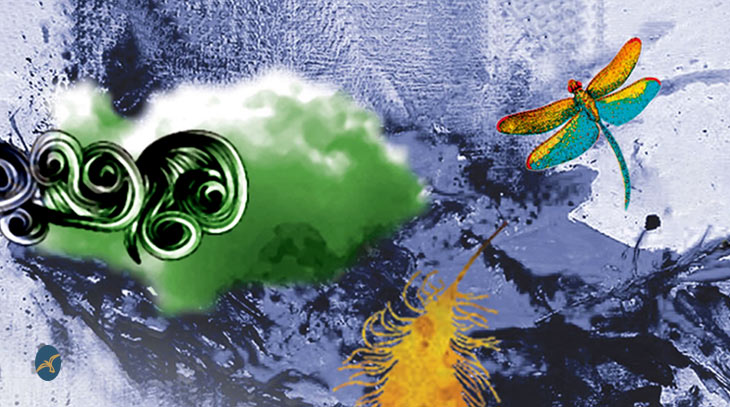নিমগ্নতা ও ঐশী প্রেমের কবি মির্জা গালিব
ইংরেজি সাহিত্যে শেক্সপিয়ারের স্থান যেখানে, উর্দু ভাষায় মির্জা আসাদউল্লাহ খান গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯) স্থান নিঃসন্দেহে সেই একই উচ্চতায়। মির্জা গালিব ছিলেন এমন এক অত্যাশ্চর্য কবি, যাকে তাঁর কবিতার মতোই চর্চা করা যায়।
তুর্কি বংশোদ্ভূত এই কবি যদিও নিজেকে ফারসি কবি হিসেবেই পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন, তবু তার উর্দু শের শায়েরি তাঁকে অমরত্ব দান করেছিল। মূলত দুটি কারণে তাঁর উর্দু গজলগুলোকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নজির হিসেবে ধরা যায়। এর একটি হলো তাঁর গজলের স্বাভাবিক আবেগ সৃষ্টির ক্ষমতা এবং অন্যটি হলো এর অন্তর্ভুক্ত গভীর ভাব ও দর্শন, যা পূর্ব বা পশ্চিমের যেকোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয়। একটি ভাষার অদ্ভুত সুন্দর ব্যবহার, যা আবেগ সৃষ্টি করতে পারে এবং একটি দার্শনিক মন, যা তৈরি হয়ে থাকে গভীর পাঠাভ্যাস ও চিন্তাশীলতা থেকে– এ দুটিই ছিল আমাদের আলোচ্য কবির প্রধানতম গুণ। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তাঁর কাব্যের এক স্বতন্ত্র ধরন, যার কারণে তাঁকে আলাদা করে চেনা যায় অন্য হাজারো কবিদের ভিড়ে। হালকা সরল বাক্যের মাঝে গভীর দর্শন, একই গজলে প্রেমের বিভিন্ন স্তর বর্ণনা, যা নিছক মানবপ্রেম থেকে ঈশ্বরপ্রেম পর্যন্ত পৌঁছায়, হৃদয়ের বিভিন্ন হাল বা অবস্থার বর্ণনা; এই ব্যাপারগুলো তার গজলে গভীর রহস্যময়তা তৈরি করতে পারে এবং পাঠকের মনে কাব্যের অর্থের এক অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে।
গালিবের গজলের ভাষাগত সৌন্দর্যকে তুলনা করা যায় তাজমহলের সাথে। উর্দু গজলের ক্ল্যাসিক্যাল ধরনকে তিনি একটি চরম পরিণতিতে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, যেমনটি পেরেছিলেন অ্যারিস্টটল গ্রিক দর্শনের ক্ষেত্রে।
শুরুর দিকের গালিব ছিলেন প্রায় দুর্বোধ্য এক কবি, যিনি বোধের অগম্য উপমার দ্বারা আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলতেন। তবে পরিণত বয়সে তাঁর সেই দুর্বোধ্য কথাগুলো আপাত-সহজবোধ্য বাক্যে প্রকাশিত হতে থাকে, যার ফলে সাধারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতিতেও তীব্র আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়।
তাঁর গজলগুলোর বিশদ পঠনপাঠনের মাধ্যমে এর অন্তর্নিহিত এক সুগভীর দর্শনের খোঁজ পাওয়া যায়, আর সত্যিকার অর্থে এই দর্শনই তাঁর গজলের মূল আকর্ষণ।
সমগ্র জগৎ এক অদৃশ্য উৎস থেকে ক্রমশ প্রকাশমান। অনন্ত সম্ভাবনার সেই অদৃশ্য উৎস থেকে ক্রমেই প্রকাশিত হচ্ছে স্থান ও কালে আবদ্ধ আমাদের জগৎ। তাই কবি বলেছেন-
‘অল্প কিছু গোলাপ ফুলেই সৌন্দর্যের প্রকাশ হলো
আরও কত রূপের ডালি মাটির তলায় রয়ে গেল।’
কবি প্রকাশিত জগতের সূত্র ধরে চিনে নিয়েছেন সেই অদৃশ্য উৎসকে। সম্ভবত সৃষ্ট জগৎকে তিনি অদৃশ্য উৎস বা স্রষ্টার প্রকাশ বলেই ভাবতেন।
অনেকগুলো শেরে গালিব খোদার সৃষ্টির সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। এই সৌন্দর্য তিনি দেখেছেন প্রিয়ার চাহনিতে, চোখের পাতায়, বসন্তকালীন সবুজ প্রকৃতিতে, পাহাড়, নদী, সাগরে। মোটকথা সমগ্র সৃষ্টিতে। তবে এই সৌন্দর্যের মাহাত্ম্য তিনি পরিপূর্ণ বুঝে উঠতে পারেননি, তার নিজের দৃষ্টি শক্তির অক্ষমতায়। তাই গালিবের আক্ষেপ-
‘হাজার রূপের ঝলক দেখি যদি আমার চোখটা তুমি
এমন শক্তি কোথায় চোখের এমন বোঝার ভারটা তুলি।’
এর সাথে যুক্ত হয়েছে তাঁর কাব্যের এক স্বতন্ত্র ধরন, যার কারণে তাঁকে আলাদা করে চেনা যায় অন্য হাজারো কবিদের ভিড়ে। হালকা সরল বাক্যের মাঝে গভীর দর্শন, একই গজলে প্রেমের বিভিন্ন স্তর বর্ণনা, যা নিছক মানবপ্রেম থেকে ঈশ্বরপ্রেম পর্যন্ত পৌঁছায়, হৃদয়ের বিভিন্ন হাল বা অবস্থার বর্ণনা; এই ব্যাপারগুলো তার গজলে গভীর রহস্যময়তা তৈরি করতে পারে এবং পাঠকের মনে কাব্যের অর্থের এক অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে।
অন্যত্র তিনি বলেন, এই সৌন্দর্যের অবলোকনে তাঁর চোখ জ্বলে যাওয়া উচিত-
‘জ্বলল না তো দুচোখ আমার এমন রূপের ঝলক দেখে
নিজেই জ্বলি নিজের চোখের, এমন সহ্যশক্তি দেখে।’
যদিও এই রূপের প্রকাশ হচ্ছে সর্বত্র, তবু সেই অরূপ, যা সকল রূপের অস্তিত্বের মূল, তা থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। অগণিত বহুত্বের মূল সেই একত্বকে চেনা সম্ভব নয়। তাই তো গালিব বলেন-
‘কেই-বা তাকে চিনতে পারে সেই অলঙ্ঘ্য একক একাই
দুইয়ের ছিটেফোঁটাও থাকলে হয়তো কিছু চেনা হতো।’
অর্থাৎ সৃষ্টির সেই উৎস বা খোদা সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়ের অতীত। সৃষ্টির মাঝে থেকেও তিনি সৃষ্টির ঊর্ধ্বে।
গালিবের এই দর্শনকে সহজেই সর্বধরেশ্বরবাদ বা Panetheism হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ইসলামের প্রথাগত সুফিরা এই মতবাদেই বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের মূল শিক্ষা ছিল এই যে- আল্লাহ এই cosmos বা সৃষ্টিজগতের সর্বত্র বিরাজমান, সৃষ্টির মাঝেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন এবং সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে তাঁর অস্তিত্বে ধরে রাখেন। এভাবেই আল্লাহ জগতের অন্তর্বর্তী বা Immanent হয়ে থাকেন। কিন্তু এই অন্তর্বর্তীতাই আল্লাহর সবটা নয়। আল্লাহ অতিক্রম করে যান তাঁর সৃষ্টিকে আর এই অতিক্রমনীয়তাই তাঁর পরবর্তী রূপ (TRANSCENDENTAL), যদিও অতিবর্তীতাকে রূপ (Form) বলা পুরোপুরিই একটি ভাষাগত সীমাবদ্ধতার ফল। অর্থাৎ আল্লাহ সৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল নন, বরং সৃষ্টিই তাঁর দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে। মির্জা গালিবের কবরের এপিটাফের এই শেরটি এই ব্যাপারটি ব্যক্ত করছে-
‘কিছুই যখন ছিল না তো খোদা ছিল
কোনো কিছু না হলেও তো খোদা হতো,
হয়ে যাওয়াই ডুবিয়ে দিল বন্ধু আমায়
নাই-বা যদি হতাম কী আর ক্ষতি হতো?’
মির্জা গালিব উপরিউক্ত বর্ণিত দর্শনটিই প্রচার করেছেন মানবীয় প্রেমের আবরণে জড়িয়ে। আর তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর গজলের প্রিয়া কেবল একটি প্রতীক (SYMBOL) মাত্র, যাকে তিনি ব্যবহার করেছেন সার্বিক প্রেমতত্ত্বকে বর্ণনার প্রয়োজনে। শরীর থেকে অশরীরী প্রেম, সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এই বিষয়টিই বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, গালিবের এত সব জটিল দর্শনের মাঝেও তাঁর কবিতার মানবীয় আবেদন ক্ষুণ্ণ হয় না। আপামর জনসাধারণ নিছক মানবীয় প্রেম হিসেবেও তাঁর গজলের উক্তিগুলোকে ধরে নিতে পারেন।
ছলনাময়ী প্রিয়া বরাবরই গালিবের সাথে প্রতারণা করেছে, বিচ্ছেদের অনলে তাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, অথচ কবি আশা ছাড়েন না-
‘প্রেমের পথে শেষ চেষ্টার শেষ না হওয়াই উচিত, আসাদ
কাজ যদি আর না হয় তবু চেষ্টা থাকুক সেও ভালো।’
প্লেটোনিক দর্শনে বিরহ বা অভাববোধ থেকেই প্রেমের উৎপত্তি, আর এই বিরহ-অভাববোধ সুন্দরের প্রতি, পূর্ণতার প্রতি। প্রেমিক মন প্রেমাস্পদকে কাছে পেতে চায় তখনই, যখন সে প্রেমাস্পদ থেকে দূরে থাকে। এই দূরত্বই সৃষ্টি করে প্রেম। যেকোনো বিশেষ বস্তু কিংবা মানবের পূর্ণতা থেকে সার্বিক বা সাধারণ পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারলে আমরা বুঝতাম যে যিনি আমাদের সকল প্রেমের উৎস, আমরা তাঁর থেকেই সবচেয়ে দূরে। মির্জা গালিব এই দূরত্বকেই বারবার স্মরণ করেছেন তাঁর করুণ গজলগুলোতে। অর্থাৎ তাঁর গজলগুলো হয়ে উঠেছে বিরহকাতর মানবের বিলাপের মতো।
অনেক শেরে তিনি সুন্দরী প্রিয়াকে বুত বা প্রতিমা বলেছেন, অর্থাৎ যেন এগুলো প্রতীক মাত্র, যার পেছনে আছে গূঢ় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য।
কবির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিষ্য আলতাফ হোসেন হালির রচিত ‘ইয়াদগারে গালিব’ বা গালিবের স্মৃতি পাঠ করলে এক অদ্ভুত চিত্তাকর্ষক মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। আমুদে, কৌতুকপ্রিয় অথচ পাণ্ডিত্যের অধিকারী আমাদের কবি মদ্য পান করতেন। যদিও ধর্মীয় বিশ্বাসে তিনি আন্তরিক ছিলেন, তবে ধর্মজীবনযাপনে, অর্থাৎ ইসলামের রীতিনীতিগুলো পালনে তাঁকে তেমন আগ্রহী দেখা যায়নি। হয়তোবা তাঁর ভেতরের কোনো গহিন দুঃখ তাঁর জীবনযাপনে প্রভাব ফেলেছিল।
কোনো কোনো শেরে গালিবের নীতি-দর্শনেরও পরিচয় পাই আমরা।
এক শেরে নিজের হৃদয়ের হাল বয়ান করতে গিয়ে যেন পুরো মানবজাতির সাধারণ হাল বয়ান করেছেন-
‘অবিশ্বাসের পড়লে ফাঁদে ইমান আমায় আটকে ধরে
কাবা ঘরের সামনে আমি, মন্দিরটা আমার আগে।’
অর্থাৎ দৈহিক কামনা-বাসনা, যা অহংবোধ থেকে আসে, তা মানবসন্তানকে অধঃপতিত করতে চায়। যদিও উচ্চতর আদর্শ ও বিবেক তাকে নিতে চায় মহত্ত্ব ও পূর্ণতার দিকে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এই দ্বিমুখী টানের মাঝখানে পড়ে থাকে। ভালো ও মন্দের দ্বন্দ্বে কেটে যায় জীবন। চিরন্তন এই নৈতিক সমস্যার সমাধানে গালিব যা বলেন, তা সুফিবাদেরই পুনরাবৃত্তি।
তিনি বলছেন-
‘কম সাহসের প্রদর্শনীর পরিণাম হয় হতাশাজনক
‘না’ বলো এই দুনিয়াদারির যতই কঠিন হোক না কেন।’
অর্থাৎ বৈরাগ্য ও যথার্থ আধ্যাত্মিক প্রেরণাই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে, যদিও তা সহজ নয়।
আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম, সে তো কবির সৃষ্টি নিয়ে, কিন্তু ব্যক্তি গালিব কেমন ছিলেন?
কবির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিষ্য আলতাফ হোসেন হালির রচিত ‘ইয়াদগারে গালিব’ বা গালিবের স্মৃতি পাঠ করলে এক অদ্ভুত চিত্তাকর্ষক মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। আমুদে, কৌতুকপ্রিয় অথচ পাণ্ডিত্যের অধিকারী আমাদের কবি মদ্য পান করতেন। যদিও ধর্মীয় বিশ্বাসে তিনি আন্তরিক ছিলেন, তবে ধর্মজীবনযাপনে, অর্থাৎ ইসলামের রীতিনীতিগুলো পালনে তাঁকে তেমন আগ্রহী দেখা যায়নি। হয়তোবা তাঁর ভেতরের কোনো গহিন দুঃখ তাঁর জীবনযাপনে প্রভাব ফেলেছিল। স্বাধীনচেতা এই মহান কবিকে উপার্জনের একমাত্র সম্বল পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া পেনশনের চিন্তায় যথেষ্ট কাতর হতে হয়। নিজ সন্তান কখনোই খুব বেশি দিন বাঁচেনি তাঁর। সিপাহি বিদ্রোহের ভয়াবহ দিনগুলোতে খুবই অসহায় অবস্থায় ঘরে অন্তরীণ থাকতেন কবি। এ সময়েই ইংরেজদের হাতে তাঁর ভাই মানসিক বিকারগ্রস্ত ইউসুফ নিহত হন। তাঁর স্ত্রীর বংশের দুটি অনাথ শিশুকে অপত্য স্নেহে মানুষ করতেন কবি। আর মনের গহিনে পুষে রাখতেন স্রষ্টার প্রতি একধরনের অভিমানী ভালোবাসা।
ভারতীয় কবি গুলজারের পরিচালনায় মির্জা গালিবের জীবন নিয়ে তৈরি ধারাবাহিক নাটকটি কবির প্রতি আবেগময় ভালোবাসা তৈরির জন্য যথেষ্ট।
আরও পড়ুন-
● মির্জা গালিবের সাতটি গজল
● মির্জা গালিবের গজল থেকে
প্রচ্ছদ : রাজিব রায়