
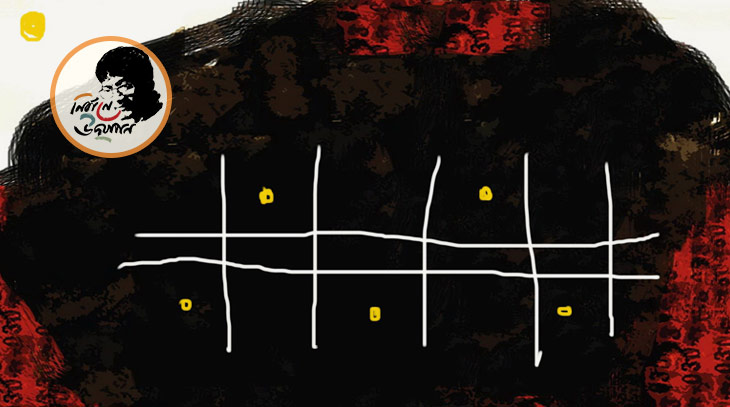
অনির্দিষ্ট ফ্রেমের আনন্দমঠ
সেলিম মোরশেদের গল্পভুবনের আনন্দমঠটি কোথায়, অথবা গল্পের জগৎবাড়ি কোন পুষ্পক বাগানের সম্মুখবর্তী— প্রশ্নের সুরাহা সহজ-সাধ্য নয়। কেননা তাঁর গল্প সময়ের ক্ষুধিত বাস্তবতাকে স্বীকার করেই পাষাণের মতো সময়-নিরপেক্ষতার দিকেও ধাবমান। এমনকি বর্তমানের আয়নাটাকে একটু পেছন ফিরে দেখা, ইতিহাসের তলবিন্দু ছুঁয়ে দেখা—ফলে এই লেখকের গল্পবাড়ি যে যে বাগানের সামনে নির্মিত, সেই বাগান নির্বাচিত হলেও তার ফুল একেবারেই নির্দিষ্ট নয়। তবে গাছ রোপণ পদ্ধতিতে যে ঐক্যমিল তা চেতনার।
গল্পগুলো লেখকের মনোচেতনার স্রোতে স্রোতে, বর্ণনাভঙ্গিমায় শরীর পেয়েছে আবার পায়ওনি। এভাবেও বলা যেতে পারে, লেখকের চেতনার রঙে প্রস্ফুটিত হতে গিয়ে গল্পগুলো কি আদৌ শরীর চেয়েছে কোনো, অন্তত গল্পের চিরায়ত শরীরকাঠামো? সেলিম মোরশেদের গল্পগ্রন্থ বাঘের ঘরে ঘোগ পাঠ করতে করতে পাঠকের মানসভূমের দরজায় এই ভাবনাগুলো কড়া নাড়তেই পারে। আর কড়া নাড়তে পারে এ জন্য যে মোরশেদের গল্পের যে জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি, এ গ্রন্থের গল্পগুলো সেই জগতকে জড়িয়েই তাঁর আনন্দমঠকে নিয়ে গেছে অন্য কোথাও—অন্য কোনোখানে। তবে কোন বিস্মৃতির প্রান্তসীমায় সেই বসতবাটি? সেলিম তাঁর সময়ের অস্থির ধ্বস্ত প্রবাহের সঙ্গী হয়ে নিজস্ব ভূগোলের চৌহদ্দিতেই হেঁটেছেন; কিন্তু বলনভঙ্গিতে শেষ অবধি তা আর ভূগোলবিশেষের ঘেরাটোপেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এক ধরনের কোলাজশৈলীর বুননে তার সঙ্গে একীভূত হয়েছে ইতিহাসযান, সময়ের পূর্বাপর পরিপ্রেক্ষিত এবং চেতনাস্রোত। আর চেতনাস্রোতের তরঙ্গে তরঙ্গে লেখকের অন্তর্লিপ্ত রাজনৈতিক বিবেচনাও অনুক্ত থাকেনি। সবকিছু মিলিয়ে বাঘের ঘরে ঘোগ-এর যে রন্ধনপ্রণালী তাতে যেন ধরা থাকে বিভিন্ন রঙের আয়নার দৃশ্যরূপ, দৃশ্যগল্প।
গ্রন্থভুক্ত পাঁচটি গল্পের মধ্যে প্রথম গল্প ‘রক্তের যতো দাগ’ শুরু হয়েছে বিশুকে কেন্দ্রে রেখে। ‘আকস্মিক এক প্রবল ধাক্কায় সামনে ছিটকে পড়ে জানোয়ারের মতো হাঁপাচ্ছিল বিশু।’ গল্প শুরু হয়। ধীরে ধীরে জানা যায়, ‘শ্রেণীশত্রু খতমের লাইনে’ অংশগ্রহণকারী এবং বর্তমানে রিমান্ডবন্দি বিশুর রাজনৈতিক সংশ্লেষণ। সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিক্লিষ্ট বিশুর মধ্যে তৈরি হওয়া পুঞ্জীভূত বিবেচনা গল্পের বর্ণনাকারী বয়ান করেন এভাবে—’১৯৭১-এ পার্টি বলল, পাকিস্তানের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে ভারতের আগ্রাসনবাদ মেনে নেওয়া স্বাধীনতায় আমাদের আস্থা নেই। দুই কুকুরের লড়াই; অথচ স্বাধীন রাষ্ট্রের যতটুকু সুফল গ্রহণ করতে বাধছে না। লাইনের ভুলগুলো নিয়ে বিশুরা কখনো আলোচনা করার অবকাশই পায়নি। সংশোধনবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল বলা হবে—তখন এটা বিশুরা জানে।’
বিশুর আড়াল থেকে সেলিম মোরশেদের চেতনা-প্রদেশের রোশনাই যেন উছলে ওঠে। মোটামুটি সরলরৈখিক বিন্যাস এবং অনুসৃত গল্পকাঠামোর পরম্পরায় গল্পটি শেষ হয় বিশুর মৃত্যু এবং ‘কদমগাছের ওপর কোকিলটা ডেকে উঠল!’ এই বলে। এর পর কিন্তু গল্পের আয়না আর একরৈখিকতায় স্থির থাকেনি। ডালপালা মেলেছে। কোলাজ-নির্ভরতায় পরবর্তী গল্পগুলোর পৃথক শরীরে একই আয়নার বর্ণিল দৃশ্যরূপকল্প জেগে উঠেছে বার বার।
বাঘের ঘরে ঘোগ-এর গল্পাবলি—বিশেষত ‘মৃগনাভি’ ও ‘পরম্পরা’ পাঠান্তে এই ধারণা আরও পক্ব হয়ে যে গল্পকাঠামো নয়, প্রথমত কোলাজবিন্যাস, পরে কোলাজের অনু ভেঙে তার পরমাণু অবধি পৌঁছতে চান লেখক এবং সেটিই তাঁর অভীষ্ট। যে কারণে অনেক ক্ষেত্রেই গল্পের চলনগতি সুনির্দিষ্ট স্পষ্টতার পথে হাঁটে না।
‘আদি অপেরা’ গল্পের পর্দা উঠেছে সংস্কৃতিকর্মী হোসেন ডাক্তারের মুখদর্শন করে। একসময় হোসেন ডাক্তার শরীফ শাহাদতের বউয়ের অনুরোধে যখন সিরাজউদ্দৌলা যাত্রাপালা থেকে ‘আলেয়া, যৌবনের উন্মাদনায় চেয়ে ছিলাম নারী, পেয়েও ছিলাম নারী, ভেবেছিলাম নারী শুধু ভোগের সামগ্রী…শেঠজি, আপনি যাচাই করেন মুক্তার মূল্য, আমি পরখ করি নারী রত্ন।…নন্দন কুমার আপনাকে সেলাম জানাচ্ছে বেগম সাহেবা।’ প্রভৃতি ডায়ালগসহ অভিনয় করেন, উপরন্তু মুকুন্দ রায়ের গানও দেখি হুবহু জায়গা করে নেয় গল্পভূমিতে, তখন এটি কি হোসেন ডাক্তারের গল্পমাত্র থাকে? আরও দেখি, ‘আদি অপেরা’য় ক্রমেই স্থান পেয়ে যাচ্ছে যশোরের ওয়ার্কার্স পার্টির কর্মী বারেক, টুটুল ও বারেকের ডায়েরির অনুপুঙ্খ বিবরণ; ‘আমি সত্যিকার অর্থে কর্মবিমুখ, গতিহীন আর নিরানন্দ এক জীবনের ভেতর আছি…আমার কোনো নৈতিকতা নেই—বিকৃত মন!… আমি টুটুলের মতো কখনো কমিউনিস্ট হতে পারব না। সার্ত্রেকে সারা জীবন শুনতে হয়েছিল কমিউনিস্টের জীবন এত মূল্যবোধহীন হয়?’
ক্ষণেক বিরতিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন—চেতনাস্রোত। কিন্তু হোসেন ডাক্তারের গল্পে সিরাজউদ্দৌলা যাত্রাপালার পাশাপাশি কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী টুটুল ও বারেক ঢুকে পড়ল কীভাবে! এই তো গল্পকার সেলিম মোরশেদ কোলাজ রূপান্তরের জাদু প্রদর্শন শুরু করলেন। এ ক্ষেত্রে এই গল্পের পটভূমিকায় তাঁকে দেখা গেল সূত্রধরের চরিত্রে। টুটুল-বারেকের বৃত্তান্ত উন্মোচনের আগে বর্ণনাকারীর ছদ্মবেশে বললেন, ‘এই হলো হোসেন ডাক্তারের গল্প; আসলে কি গল্প? টুটুল ও তার ভাই বারেক…? দুজনের সাপোর্টিং নোট রয়েছে; সমন্বয় তিনজনের।’ কয়েক বাক্য পরেই পুনরায় সেলিম মোরশেদের ভাষ্য, ‘গল্পের চেয়ে বরং গল্পের নোটে আছে ন্যারেশন, কনফেশন আর ইজ্যাকুলেশন।’ এই ন্যারেশন, কনফেশন ও ইজ্যাকুলেশনের বৃত্তপটেই সেলিমের গল্পপ্রকরণের উদ্ভাস।
ফলে ‘মৃগনাভি’, ‘পরম্পরা’সহ গ্রন্থবদ্ধ গল্পসমূহে দৃশ্যমান হয় বর্ণনার অধিক দৃশ্যের বুদবুদ। আর একটি দৃশ্য ফেনা তৈরি করতে-না-করতেই অন্তরালে শুরু হয় অপর দৃশ্যের সাজসজ্জা। এ ঠিক জাদুবাস্তবতা নয়, বড়জোর বলা যেতে পারে বাস্তবতার জাদু-কৌশল। যেমন ‘মৃগনাভি’তে জোসেফ ও বিকাশের বৈপরীত্যের বাস্তবতায় যে গল্প শুরু হয়, সেটি ঘটনা, ঘটনাসম্ভূত মানসিক চৈতন্যক্রিয়া এবং দৃশ্যচাঞ্চল্যে অস্থির। এর মধ্যে সেক্স ‘স্বর্গের প্রথম পরিকল্পিত পাপ’ যেমন দানা বাঁধতে উন্মুখ, তেমনি পরিপার্শ্ব তথা ‘টোটাল সময়টার’ অস্থিরতা—নৈতিকতা, এবাদত, শ্রেণিচেতনা, রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্বের সমষ্টি প্রভৃতি বিষয়কেও নতুন আলোয় প্রশ্নের সামীপ্যে এনেছে। এখানে সেলিম মোরশেদের ভাষাভঙ্গি এমন যে অবলীলায় এক বিষয়ের সঙ্গে আরেকটি চিন্তার অথবা বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ ঘটে যাচ্ছে! কিংবা বিচ্ছিন্নতা থাকলেই ক্ষতি কী? ‘মৃগনাভি’ থেকে উদ্ধার করা যাক—
‘বিকাশ বলেছে, আব্দুল্লাহ, জোসেফ বলেছে, লালু, বিকাশ বলেছে, পড়াশোনা আছে, জোসেফ বলেছে, লেখাপড়া জানিস? দুজনেই একটি ১৯/২০-এ থাকতে চেয়েছিল, চিন্তা হচ্ছিল জোসেফের অন্যটা; একটা বিষয় মেলাতে পারছিল না: শেষে তাদের থামতে হলো বিকাশ আর জোসেফ বলে। কাটাকাটি তারা চাচ্ছিল, ভিতটা দেখতে চাইল না? জোসেফের রাগ হলো, ভেতরটা কী—অস্পষ্ট এক শামা আপা না একটি ল্যান্ড? বিকাশ ভাবল, জোসেফ কখনো স্বর্গে যেতে চায় না, সাধনা-বাসনার পক্ষে যাবে না।’
তবে এই অস্থির দৃশ্যচিত্তগল্প এবং ভাষাভঙ্গির একটা বিপদও বিদ্যমান। বাঘের ঘরে ঘোগ-এর গল্পাবলি—বিশেষত ‘মৃগনাভি’ ও ‘পরম্পরা’ পাঠান্তে এই ধারণা আরও পক্ব হয়ে যে গল্পকাঠামো নয়, প্রথমত কোলাজবিন্যাস, পরে কোলাজের অনু ভেঙে তার পরমাণু অবধি পৌঁছতে চান লেখক এবং সেটিই তাঁর অভীষ্ট। যে কারণে অনেক ক্ষেত্রেই গল্পের চলনগতি সুনির্দিষ্ট স্পষ্টতার পথে হাঁটে না। বিপরীতে কাব্যবর্তী বিমূর্ততায় পাঠককে নিয়ে যায় খণ্ড খণ্ড দৃশ্যগল্পের আপাত বিচ্ছিন্ন অখণ্ডতায়। বিপদটা এখানেই। গল্পের শরীর যেখানে অটুট গল্পবন্ধনে স্থিত নয়, সে ক্ষেত্রে বর্ণিত দুই গল্পেপাঠককে কি অনির্দিষ্ট ফ্রেমের ভেতর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে না? প্রশ্ন থেকেই যায়। যদিও নামগল্প বাঘের ঘরে ঘোগ-এ পূর্বাপর কোলাজভ্রমণের মধ্য দিয়ে গল্পের নদী সার্থকভাবেই তর তর বয়ে যায়; তার পরেও কাটা সাপের মুণ্ডু ছেড়ে আসা সেলিম মোরশেদের গন্তব্য বোধ করি এবার বাস্তবতার জাদু-কৌশলে নির্মিত অনির্দিষ্ট প্রেমের দিকেই: যার নাম হতে পারে আনন্দমঠ।





