
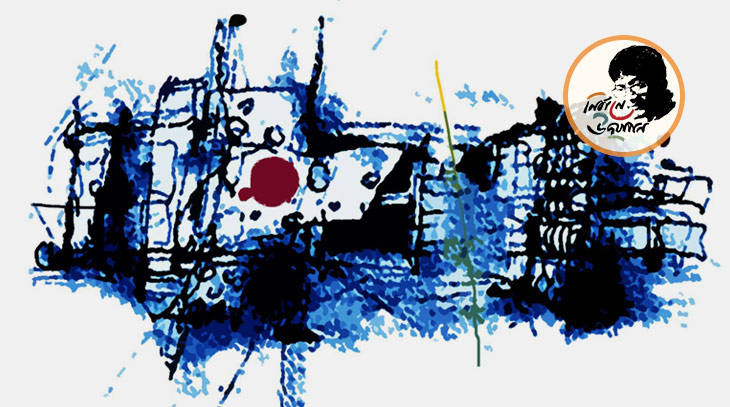
অবিন্যস্ত জার্নাল
সেলিম মোরশেদের সঙ্গে পরিচয় নদীর তৃতীয় তীরে। নিঃসঙ্গ বিকেলবেলায় ভেঙেপড়া বন্ধুর মুখ দেখতে গিয়ে, ততোধিক ভাঙনদুষ্ট আমি তাকে আবিষ্কার করলাম ভাঙা বইয়ের তাকে। সংক্ষিপ্ত এবং কাঁটাছেড়া অবস্হায়। কিন্তু সেই আধেক কাহিনি চেতনসত্তাকে নাড়িয়ে দিল আজীবনের জন্য। বইপড়া ছাড়া কিছুই ঠিকঠাক শেখা হয়নি। সুতরাং পড়ার রুচি, সূচি তৈরি হয়ে ওঠে শৈশব থেকেই। কখনও বড়দের তত্ত্বাবধানে। বিশেষত সেই সময়ে কারো কারো ক্লাসিকে আগ্রহ, লেখালেখি লেখার জাত চিনতে সহায়ক হয়েছে। লক্ষই করা হয়নি, কবে ফুটনোটে, মার্জিনে ভরে গেছে জীবন।
সেলিম মোরশেদের সঙ্গে পরিচয় ও নানা পরিসীমায় অন্য সম্পর্কগুলো একান্ত পারিবারিক আলোচনা ও নিষেধের বিষয়। সুতরাং এই বিধিবিধান মাথায় রেখেই কথামালার বিস্তার। শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতা আর ভালোবাসা দুই অনিবার্য সত্য ও পরস্পরের পরিপূরক। শিল্পের প্রতি ভালোবাসা এই পরম্পরার আগামী পথ তৈরি করছিল।
বন্ধুর বাড়ি হতে ফিরে কিছুদিন কেটে গেল ঘোরে। বিকেলের দেবদারু সেই খবর রাখত। খবর রাখত হেমাঙ্গিনী। সময়টা শীতের শেষ। পয়লা ফাল্গুনের রাতে একপশলা বিষ্টি নামল শহরে। তখনো চাদর-চাপানো চায়ের দোকানে গুটি মানুষের ভিড় আর চেনা বন্ধুদের আড্ডায় জমাট নিঃসঙ্গতা। মনখারাপের রাতে এক অগ্রজ কবি অদ্ভুত গল্প শুনিয়েছিলেন ‘নীল চুলের মেয়েটি যেভাবে তার চোখ দুটি বাঁচিয়েছিলো’—। কুয়াশার চাদরে হালকা সরের মতো চাঁদ সেই রাতের আকাশে। অতঃপর গল্পটার সব চোখহারানো বিকারগ্রস্ত মানুষের পাশে বহুক্ষণ বহু রাত, বসে থাকা চোখের আশায়। অদ্ভুত ব্যাপার হল, কাছাকাছি সময়ে এলেন সারামাগো তার শ্বেত অন্ধত্ব নিয়ে। বদলে যাওয়া বিকেলগুলো ভরিয়ে নিল অন্তহীন নীরবতা। একমাত্র করবীগাছ ছাড়া সকলেই যেন অন্ধ। দিন গুনছি দেড়খানা গল্প হাতে নিয়ে আলোর আশায়।
শূন্যদশক বিবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে। বিশেষত এই সময়ে যখন দেখি ঘোড়া কেনার আগেই মানুষ চাবুকে তেল মাখায়। চাবুক পুরস্কৃত হলে ঘোড়া জুড়ে দেয়া হয় গাড়ির সঙ্গে। সেই দশকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বসে বললাম ‘সেলিম মোরশেদের কথাসাহিত্য’ নিয়ে গবেষণা করতে চাই। থমকে দাঁড়াল ঘরের বাতাস। অন্তত: রক্ত ছলকে-ওঠা সব সাদা-কালো মুখ আজও স্পষ্ট মনে আছে। আপত্তি নিয়ে জানিয়ে দেয়া হল উনি নবীন লেখক। তাঁর লেখার ওপর কাজ করা যায় না। বিকল্প হিসেবে যাঁদের নাম এল তাঁরা স্বনামে খ্যাত সন্দেহ নেই, ভরসা বা ভালোবাসার মতো কারণ খুঁজে পাইনি কোনোদিন। সুতরাং আমার অমায়িক জেদে বিরক্ত অধ্যাপকগণ অল্প-সময় দেন তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা অন্বেষণের। কারণ আনুষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্নের মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা বাকি ছিল।
তখনো শাহবাগ অচেনা স্হল। প্রকাশনী খুঁজে বই কেনা কিছুটা অধরাই। কয়েকটা ঘণ্টা মাত্র হাতে। নমস্য লেখক, কয়েকজন অ-দরকারি অথচ পদ অলংকৃত করা লেখক-লেখিকার নামের ভিড়ে প্রিয় লেখকের অন্বেষণে ভারাক্রান্ত মন। কুষ্টিয়া বইমেলা, তার পর আরও আরও বই বিপণনের কাজে ন্যস্ত মানুষের দ্বারস্হ হওয়া। কোথায় আছেন তিনি? বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, সেমিনার কোথাও কোনো সংগ্রহসূচিতে তাঁর লেখা অনুপস্থিত!!!
অবশেষে মনে পড়ে অগ্রজ কবির কথা। যিনি নিজেকে তাঁর একান্ত এবং অকৃত্রিম অনুসারী হিসেবে সবসময় পরিচয় দিতেন। দ্বিধা ঘোচানো কষ্টকর হয়ে ওঠে। সত্যিই, একজন নবীন লেখক সন্দেহ নেই তাঁর গদ্য শক্তিশালী তবু নবীন আগমনে অনুসারীও বানিয়ে ফেললেন?
সময়ে জানা হল, মহামহিম অথবা সর্বোচ্চ আলোচিত গদ্য যার সংক্ষিপ্ত রূপ দেখেই চমকিত হয়েছিলাম ‘কাটা সাপের মুণ্ডু’ গল্পটি তিনি একুশ বছর বয়সেই লিখেছিলেন। আমায় তখন লেখক নয়, লেখা খুঁজে পেতেই হবে। সময় গড়িয়ে চলেছে। শরণাপন্ন হওয়া গেল অনুসারী অগ্রজের। অগ্রজ কবি যা বললেন তা শুনে বহুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে থাকতে হল। শুনলাম, আমার দেড়খানা গল্পের লেখক আর লেখেন না। তাঁর কোনো বই পাওয়া যায় না। এককালে বসতেন যশোরের ‘কালপত্রে’, এখন কোথায় কিভাবে আছেন কেউ বলতে পারে না। কিছুটা যেন সোমেন চন্দ’র তুলনা মনে এল। এই প্রতিভাবান মানুষটিও কি তবে হঠাৎ বিচ্ছুরিত আলোকমালা হয়ে কোথাও মিলিয়ে গেছেন?
আকস্মিক যুগপৎ বেদনায় যেখানে মন তৈরি ছিল ‘কান্নাঘরে’র যশোদা’র মতো অটল হয়ে। সেখানে শেষঅব্দি ভ্রাম্যমাণ দুইজনের উপলব্ধিতে কিছু অবাঞ্ছিত মানুষের অবজ্ঞার জবাবে ভর্তিক্রিয়া সম্পন্ন করা গেল। গবেষণার বিষয় নির্বাচনে উল্টোপুরাণ-এর মতো বেছে নিলাম গালবাজ একজন ভাষাবিজ্ঞানীর নাম। যিনি য ফলা-কে ফলার মতো ব্যবহার করলেও সাহিত্যিক নন কোনো ভাবেই। নিজে তখন সাহিত্য নিয়ে ভাবার মতো মানসিক অবস্হাতে নেই। পড়াটা সবসময়ই আত্মার খোরাক আমার কাছে। একজন লেখকের গুটিকয় গল্প মাত্র তখন পড়া বা শোনা হলেও স্বপ্নটা ছিল আকাশছোঁয়া। সেখানে তাঁর সাহিত্যকর্ম একটি উজ্জ্বল ধ্রুবতারার মতো সাহসী করে তুলেছিল গবেষণার পথে হাঁটতে। আশ্চর্যের বিষয়, তখনও মানুষকে ভগবান ভাবার মতো ভ্রম আমার কাটেনি। বিশ্ববিদ্যালয়কে মন্দিরই ভেবেছি, জেনেছি, সেখানে বিদ্যার্থীর অকুণ্ঠ অধিকার। শিক্ষকেরা পিতৃব্য-সম!!
পরবর্তীকালে ব্যাখ্যাও মিলেছে ধীরে-ধীরে জীবনের পাঠ নিতে নিতে। আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই— আর দশজন জেলা শহরীয় ছাত্র-ছাত্রীর মতো অযোগ্য অধ্যাপক শাসিত এই সাহিত্যাঙ্গনে অন্ধ আমিও সেই সময়ে তাঁদের ভগবান ভাবতে ভালোবাসতাম।
তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য তিনি ব্রাত্যজনের লেখক। মহাশূন্য স্টেশনে একটি মেয়ের আত্মহত্যার খবরের সঙ্গে সঙ্গে আবার তিনি খবর রাখেন সখিচানের আত্মমর্যাদার। সলোমানের বক্তব্যের মতো কথাগুলো বলা জরুরি বলেই কি উপলব্ধি হয়েছে সচেতন গদ্যের নির্মাণে কোথাও তিনি আসলে সাহিত্যের আসরে নিষ্ঠা এবং ভালোবাসায় নিজের কর্মকে সুশীলদা’র—ধুলোচ্ছাপের মতো কোমল এবং নান্দনিক একটি আড়ম্বরহীন সাধকের স্হানে রেখে যেতে চেয়েছেন।
জোনাথন লিভিংস্টোন-এর ডানায় ভর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধা বুলিতে মন বাঁধা পড়ল না কোনো ভাবেই। তবে একটা ভালো পরবর্তীকালে বইয়ের জগৎ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাবাজার পথ খুলে দিল সহজে। চেতনে-অচেতনে তখনও অন্ধ মানুষের শহর জুড়ে চোখের অন্বেষণ। কিছু স্বনামখ্যাত রথী-মহারথী উঁকি দিলেন দরজায়। শিখিয়ে দিতে চাইলেন কপিপেস্টের আঠার ফাঁকে গোঁজামিলের প্রবন্ধ ও নিবন্ধ। কোনও রথীকে দেখলাম নবরত্ন সভা বসিয়ে কপিপেস্টে গবেষণার ধুম। চোখের কুয়াশা একটু সয়ে আসছে। সময়ের সঙ্গে মানুষ দেখছি। এবং বিস্ময়ে লক্ষ করছি স্বল্পপঠিত গল্পের গল্প-কারের নাম উল্লেখ করলেই অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে যায় মানুষের মুখ। যা পরবর্তীকালেও সমান্তরাল।
মনে আছে এক সম্মানীয় হাস্যোজ্জ্বল ভাঁড় সদৃশ্য অধ্যাপক ধন্য করতে এলেন আমাদের শহর। বসার ঘরে যখন দুলে দুলে গান গেয়ে বাড়ির কনিষ্ঠ সদস্যকেও অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন তখন হঠাৎ কথাচ্ছলে বসেছিলাম-স্যার সেলিম মোরশেদের লেখা আপনার কেমন লাগে?
আপনি তো শিল্পরূপ নিয়ে লিখেছেন। ওনার লেখা?…
ভদ্রলোক এমন গম্ভীরভাবে তাকিয়ে, ভালো না, বলে চুপ হয়ে রইলেন। হয়তো সে রাতে তাঁর অসতর্ক ও স্বরচিত অগ্নিকাণ্ড না ঘটলে বাকরহিতই থাকতেন।
যেখানেই সেলিমের নাম উচ্চারিত হয়েছে, দেখেছি সকলের নীরবতা। যখন জেনেছি সেলিম মোরশেদের সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের সাহিত্যসাধনা তাঁর ঊনত্রিশটি গল্প, উপন্যাস, চিত্রকর্ম, ট্রাভেলগ, নাটক সহ কবিতা ও অন্যান্য রচনাবলি রয়েছে। সেসব লেখনী ও আঁকা ছবির সঙ্গে পরিচয় ঘটছে তখন আর যাই হোক তাঁকে নবীন বা কিশোর বলার অবকাশ নেই কোনো ভাবেই।
তাঁর সাহিত্য নিয়ে কাজ করতে চেয়েছি যে সময়ে, জানলাম, অনেক আগেই কথাসাহিত্য নিয়ে কাজ হয়েছে। দুই বাংলা জুড়ে লেখা ছাপা হয়েছে সাদরে। যখন একটা বই খুঁজে হন্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে তাঁর রচনাও অন্তর্ভুক্ত। অথচ নন্দিত হতে নিন্দিত কেউ তাঁর নাম উচ্চারণ বন্ধই রাখেননি। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গুম হয়ে গেছেন।
অনেকে নামের সঙ্গে একটা অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করেছেন—ভারী! ভারটা কিসে বুঝতে সময় লেগেছে। কলেবরে না সাহিত্যে?
প্রশ্ন জাগে দুর্যোধন বা দুঃশাসন নামকরণে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রতিভা বসু। কোনো পিতা-মাতা কি জেনে-বুঝে সন্তানের নাম দুর্যোধন রাখতে পারে? প্রকৃত কারণ আসলে রাজসিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী পুত্র যিনি জন্ম নিলেন তিনি ছিলেন খুবই সুদর্শন। সুদর্শন বিশেষণ শুনেই বিদুর চক্রান্ত করে সর্বত্র রটনা করেন সে দুর্যোধন এবং অবিলম্বে এই অশুভ শক্তিকে বধ করা হোক। বোধকরি আমাদের সমাজেও বিদুর-বাহুল্যেই আজও আমরা অকপট হতে শিখিনি।
সারামাগো-র কুয়াশা ততোদিনে সয়ে এসেছে চোখে। সহপাঠীকে বই, নোট সব দেবার পরেও পরীক্ষার সময় খাতা দেখতে না-দেয়ায় প্রবল তিরস্কারের ব্যথিত বিস্ময়ে বুঝতে পারি চামড়া কেটে দেবার বাধ্যতা না জানালে ফল জানতেও কতটা বিড়ম্বিত ও তিরস্কৃত হতে হয়। আড়ম্বরপূর্ণ তোষামোদ ও মেদযুক্ত উপহার দিয়ে বিশেষ আর হলাম কবে? বরং সেলিমের গল্পের বিশুর উপলব্ধি বার বার মনে পড়ে—
‘বিশু থাকে ভিন্ন জগতে, তার ভাবনার মূল এরকম: সক্রেটিসকে হেমলক দিলে পান করেছিলো, সক্রেটিসের সুযোগ ছিলো পালিয়ে যাবার। কিন্তু সিস্টেমের প্রতি আনুগত্য রেখেছিলো সক্রেটিস, তাই সে পালাতে চায়নি। সক্রেটিস সঠিক ছিলো, ফলে তার সমর্পণও যদি ভুলের কাছে হয় তাহলে সঠিকটাই জেতে; সক্রেটিস স্মরণীয়, কিন্তু বিশুর ক্ষেত্রে তার উল্টো। এই প্রেক্ষিতে দেখা যায়, পার্টির সামষ্টিকতায় একটা বড়ো ভুল সনাক্ত করেছে শক্তে; এমতাবস্থায় পার্টির সঙ্গে তার কোনও বোঝাপড়া হয়নি, সে কেন অস্ত্র জমা দেবে? সতীর্থদের নাম কেন বলবে; পার্টি যেহেতু ভুল, চলমান সমাজ-বাস্তবতা তো আরও ভুল, ফলে ভুলের থেকে আরেকটা ভুলে যাবার মতো স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক কেন হবে? শুধুই নিজের সুখ-শান্তি?
না, মরে গেলেও তা করবে না। রণনীতি ও রণকৌশল— দুটো কথার ভেতর অনেক বড়ো ফাঁক রয়েছে। ধরি মাছ না ছুঁই পানি মার্কা বিপ্লব যারা করে তাদের জন্যে এসব কথা উপযুক্ত। বিশুরা নিজের নিয়তি বানিয়েছে কেবল প্রকৃত বিপ্লবের জন্যে, আর এইজন্যে এখন তার প্রধান কাজ পার্টির নেতৃস্থানীয়দের সাথে বোঝাপড়া করা। অস্থির হয়ে উঠেছে সে।…’
(গল্প: রক্তে যতো চিহ্ন)
সেলিম মোরশেদ সম্পর্কে এ যাবত সর্বাধিক চর্চিত শব্দের নাম তিনি প্রতিষ্ঠানবিরোধী, ছোটকাগজ আন্দোলন-এর অন্যতম পুরোধা। সত্যিকার অর্থে তিনি একজন অ্যাক্টিভিস্ট এবং অত্যন্ত রাজনীতি-সচেতন লেখক সন্দেহ নেই। কিন্তু আশির শক্তিশালী সাহিত্যিক বা মুভমেন্ট করা মানুষ বলে যে গণকাতারে ঠেলে দিই সকলে তা কোন কারণে? ধরেই নিই আমরা সাহিত্য আর ব্যক্তির কর্মকে আলাদা করে মোটাদাগে দেখব সেখানেও আলোচনার কিছু ডাইমেনশন মনে রাখা জরুরি।
যেমন—
ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচে যখন কিছু বলা হয় তখন পজিটিভ অ্যাপ্রোচ ক্রিটিসিজম, অ্যান্টি অ্যাপ্রোচ ক্রিটিসিজম, রিডাকশনিজম দিয়ে বিষয়বস্তুর সমালোচনা করার বহু প্রচলিত পদ্ধতি রয়েছে। রয়েছে সাহিত্যবিচারের নানা পদ্ধতি। কিন্তু এ সকল পন্থা বাদ দিয়ে অথবা অর্ধমনস্ক পঠন-অভ্যেস নিয়ে যারা ক্রমাগত শক্ত, ভারী নানা মন্তব্য করেন, ব্যক্তি, মানুষকে অসম্মান করতে চান। তাদের জন্য বলা—
এক. হয় তাঁরা এই তিনটি প্যারাডাইম জানেন না।
দুই. তাঁরা দায়িত্ব নিতে চান না।
এবং খুবই দুঃখের বিষয় যত বেশি আলোচনা তাঁর মুভমেন্ট নিয়ে হয়েছে ঠিক ততোটাই ম্রিয়মাণ হয়ে চাপা পড়েছে সাহিত্যিক মূল্যায়ন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির পথ খুঁজে ভালোবেসে সাহিত্য নিয়ে কাজ করেছেন বেশকিছু গুণী মানুষ। তবুও বলতেই হয় বেশিরভাগের ইচ্ছে এবং দায়টুকু যেন মুভমেন্ট-কেন্দ্রিকই বেশি ছিল। বেরিয়ে এসে সাহিত্যের নির্মোহ ও নৈব্যক্তিক, মূল্যায়ন তাঁর জন্য যেন দূরের নিয়তি।
খুবই দুঃখের বিষয় যত বেশি আলোচনা তাঁর মুভমেন্ট নিয়ে হয়েছে ঠিক ততোটাই ম্রিয়মাণ হয়ে চাপা পড়েছে সাহিত্যিক মূল্যায়ন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির পথ খুঁজে ভালোবেসে সাহিত্য নিয়ে কাজ করেছেন বেশকিছু গুণী মানুষ। তবুও বলতেই হয় বেশিরভাগের ইচ্ছে এবং দায়টুকু যেন মুভমেন্ট-কেন্দ্রিকই বেশি ছিল। বেরিয়ে এসে সাহিত্যের নির্মোহ ও নৈব্যক্তিক, মূল্যায়ন তাঁর জন্য যেন দূরের নিয়তি।
‘নদীর তৃতীয় তীর’—লাতিন আমেরিকার একজন লেখকের একটি বিখ্যাত গল্প। যেখানে পরিবারের প্রধানতম সদস্য পরিবারের অসম্ভব খারাপ সময়ে নৌকা নিয়ে পাড়ি দেন নদী। কিন্তু সঙ্গে কোনো খাবার, জল কিছুই নেননি তিনি। তাঁর সুদিনের অন্বেষণে নৌকা কখনও ওপারে পৌঁছাতে পারেনি। কিন্তু দুঃসময় বা সু-সময়ে পরিবারের মানুষেরা চাইলেই দেখতে পেতেন নৌকাটি মাঝনদীতে ভাসছে।—
সেলিম মোরশেদের গদ্য এই তৃতীয় তীর হয়েই ধরা দেয় আশ্বাস ও ভরসাস্হল হয়ে। আসে নির্মোহ জীবনের প্রতিচ্ছবি নিয়ে। তাঁর গদ্য জটিল লাগেনি কোনোদিন। বরং ভাষা বিনির্মাণ ও আখ্যানশৈলী মুগ্ধ করেছে বার বার। গল্প বা উপন্যাস, নাটক বা প্রবন্ধ, নিবন্ধে নানা নিরীক্ষা ও শব্দসচেতন পদচ্ছাপ থাকলেও তাঁর গদ্যের বিশ্লেষণে আমি অধ্যাপক মৌমিতা রায়ের সঙ্গে একমত, ‘লেখকের কোথাও বড্ড বুঝিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষা যেন’— কান্নাঘরে রোগের নাম ওষুধ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা, চিতার অবশিষ্টাংশে দিলীপের অসাঢ় শরীর বা কাটা সাপের মুণ্ডু- সর্বত্রই হেমাঙ্গিনীর মতো সাহসী জলপাই সাপকে পোড়াতে তিনি নিজে শুধু সাহসই দেন না তাঁর হোসেন ডাক্তার সহ তিনি নিজে হাতকাটা দা’ওয়ালার জন্য সহানুভূতিতে অধীর— যেন বলেই দেন আগ্রহী পাঠক, তুমি এই পথে হাঁটো। সচরাচর সমগ্র পড়ার বাতিক থাকায় দেখেছি বহু লেখকের রচনাসমগ্রে অনেক অদরকারি লেখা, বা কম গুরুত্বপূর্ণ লেখা সংকলিত থাকে যা পাঠকের অপঠিত থাকাই কল্যাণকর। সেলিম মোরশেদের ক্ষেত্রে তা আশ্চর্য ব্যতিক্রম। তাঁর নিজের লেখা গল্পের কাছে তাঁরই কম গুরুত্বপূর্ণ দুই-একটি গল্প ছাড়া আজ অব্দি দাঁড়ি-কমা বাদ দেবার মতো কিছু মেলেনি। যদিও তার পরও সেলিম তাঁর শব্দ ঝরিয়ে দেন বার বার।
কমলকুমার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, দীপেন্দ্রনাথ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পরে এই বাংলায় ভাষারীতি তৈরিতে সেলিম মোরশেদ প্রশংসার দাবিদার সন্দেহ নেই।
নিরীক্ষার দিক দিয়ে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। আপন গদ্যরীতি তৈরিতে কমলকুমার সাধুরীতি গ্রহণ করার পর আর চলিত রীতিতে ফেরেননি। কিন্তু ‘ফ্রাইডে আইল্যান্ড’ লেখার পরেও অমিয়ভূষণ বা সেলিম মোরশেদ কোনো নির্দিষ্ট ছকে নিজেদের বাঁধেননি। ‘রক্তে যত চিহ্নে’র পরে অম্লানদের মতো নিজস্ব ভাষারীতি কিন্তু ক্রিয়া-বিবর্জিত নয় এমন রচনাও রয়েছে। তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য তিনি ব্রাত্যজনের লেখক। মহাশূন্য স্টেশনে একটি মেয়ের আত্মহত্যার খবরের সঙ্গে সঙ্গে আবার তিনি খবর রাখেন সখিচানের আত্মমর্যাদার। সলোমানের বক্তব্যের মতো কথাগুলো বলা জরুরি বলেই কি উপলব্ধি হয়েছে সচেতন গদ্যের নির্মাণে কোথাও তিনি আসলে সাহিত্যের আসরে নিষ্ঠা এবং ভালোবাসায় নিজের কর্মকে সুশীলদা’র—ধুলোচ্ছাপের মতো কোমল এবং নান্দনিক একটি আড়ম্বরহীন সাধকের স্হানে রেখে যেতে চেয়েছেন। সততা, সাহিত্য স্বদেশপ্রেম এবং পরম্পরাজ্ঞান তাঁর লেখার মূল শক্তি। কিন্তু স্বদেশপ্রেম, স্ব-অন্বেষা, ঔচিত্যবোধ, সাহিত্যের কালোবাজারি রুখতে যে সুত্রমুখ তিনি রচনা করলেন। সেই সূত্রমুখই কখনও প্রবল ষড়যন্ত্রে আড়াল করে দাঁড়াল তাঁর অসামান্য শিল্পকর্ম। এ বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক।
‘লিটলম্যাগ’ শব্দটি তখনও আমাদের কাছে স্বল্পায়ু, দূরের বিষয়। এ সম্পর্কে কিছুই জানি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানান সাহিত্যপত্রিকা আসত। শিক্ষকদের কাছ থেকে কখনও সরাসরি সংগ্রহ করা হত সেইসব পত্রিকা। একদিন বিস্ময়ের সাথে আবিষ্কার করা গেল ছোটকাগজের দুরন্ত সৈনিক পরিচয় দেন এমন একজনের নিজ গোডাউনে রাশি রাশি ধুলো, বাতিল বস্তা আর কার্টুনের তলে পড়ে আছে এই সময়ে উল্লেখ করার মতো একটি লিটলম্যাগাজিনের অনেকগুলো সংখ্যা। সমসাময়িক সময়ে প্রকাশিত কাগজগুলো বিশ্ববিদ্যালয় তো দূরের কথা, সাধারণ পাঠকের হাতেও পৌঁছানো হয়নি আগে বা পরে। লেখা পড়তে মনে হয়েছিল অন্য ধরনের লেখা যেন। এবং এই পত্রিকাগুলো লুকিয়ে রাখার কোনো যৌক্তিক কারণ কোনোদিন খুঁজে পাইনি। কিন্তু লিটলম্যাগ মুভমেন্টে সেলিম মোরশেদের একান্ত যুক্ততা ও প্রাসঙ্গিকতা পরিস্ফুট হয়েছে ধীরে।
একসময় বিদ্যা আরোহণের শ্বেত অন্ধত্ব নিয়ে এল দুর্যোগের ঘনঘটা। বারবার প্রত্যাখ্যাত হচ্ছিল প্রবন্ধগুলো। অমিয়ভূষণ, আহমদ শরীফ, আহমদ ছফা। কারোর ওপরে আমার কোনো লেখাই যেন গ্রহণযোগ্য নয়। আত্মবিশ্বাসের সংকটে ভুগতে ভুগতে আবিষ্কার করা গেল কারণ ছিল অন্য। তথাকথিত কপি-পেস্টের নিয়ম অনুসৃত হয়নি। কখনও স্পষ্ট আবার ইঙ্গিতে বোঝানো হচ্ছিল গতানুগতিক হোন। কারা আবার এটাও বোঝাল, কয়েক লাখ টাকা খরচ করলে সন্দর্ভ আপনি রেডি হয়ে আসবে। সব ঘরে বসেই হয়ে যাবে। দূরবর্তী অধ্যাপক গবেষণা শেষ হবার আগেই উচ্চতর গবেষণা ও সুযোগের আশ্বাসে কামনা করেন মধ্যরাতে ইথার-সঙ্গ। ঘিনঘিনে শরীরে, করতলে কাটামাথা নাড়িয়ে দেয় ভিত্তিমূল। বিনিদ্র রাত কাটে, দিন কেটে যায় বিকারহীন বিকারে। উপন্যাস বা কথাসাহিত্যের স্বরূপ অন্বেষায়।
এই অন্বেষণে নির্বিচারে সব কিছু পড়তাম। তুচ্ছতম কাজের ফুটনোটে আগেই বলেছি নিজেই জুড়ে গেছি কবে। সেই মতোই পড়তে গিয়ে একদিন আবিষ্কার করলাম ‘কাটা সাপের মুণ্ডু’ গল্পটি নিয়ে একজন অধ্যাপক সাহিত্যের ইতিবৃত্তে উদ্ভট ব্যখ্যা করেছেন।
মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ-এর ‘সোনার তরী’ কবিতাটিতে ‘গানগেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে’ এই কে’ — নৌকার মাঝিকে বুদ্ধদেব বসু নারীরূপে কল্পনা করেছিলেন। তার অত্যন্ত স্পষ্ট আর যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়েছিলেন কেতকী কুশরী ডাইসন সতেরো বছর বয়সে। রঙের রবীন্দ্রনাথে তিনি বলছেন— ‘সতেরোর সেই পাকা বুড়িটা কোনোদিন এই সচেতন মানুষের ভুলকে মেনে নিতে পারেনি।’—চিঠিটি ছাপাও হয় তৎকালীন সাহিত্যপত্রিকায়। দীর্ঘ হলেও উল্লেখ করছি কারণ প্রকৃত লেখা লেখকের জাত চিনিয়ে দেয়। একুশেই সেলিম তাঁর পরিচয় জানিয়েছেন। আজ এত বছর পরে— জলপাই রঙের সাপকে ও স্বদেশের অন্তরীণ এই দ্রোহ অনুধাবনে আমাদের এইসব অধ্যাপকেরা! কতটা পারঙ্গম? হেমাঙ্গিনী যেহেতু ভিক্ষুক তাই অনেকেই তাকে ‘প্রাগৈতিহাসিক’ এর ভিখু’র সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন। আশ্চর্য হই তাদের সাহিত্যবোধে। আপদমস্তক ভোগবাদী ভিখু’র নিমজ্জনের সঙ্গে কোথায় হেমাঙ্গিনীর সংশ্রব বা সংগ্রাম? নাকি এ সবই বিদুরের চক্রান্ত?
এই পর্যন্ত লিখতে গিয়ে মনে হল, সেলিম মোরশেদের লেখার আখ্যানভাগ, বিষয় কিম্বা বিষয়বস্তু, ট্রিটমেন্ট, চরিত্রের পরিমিতি, মিথস্ক্রিয়া, চরিত্রচিত্রণ, ভাষাশৈলীর অভিনবত্ব তাঁকে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের যে জায়গায় নিয়ে গেছে, আগামী প্রজন্মের পাঠকের কাছে তা উপলব্ধির, ভালোবাসার ও কৃতনিশ্চয় শিক্ষারও। যদিও তিনি সাহিত্যে আদর্শবাদ প্রচার করতে আসেননি, আসেননি পাঠকপ্রিয় আপাত সহজ বিষয়কে আশ্রয় করে লোকপ্রিয়তা নিতে। স্বাধীনতা-উত্তর টালমাটাল বাংলাদেশের অস্হির, অসম অসহ সমাজব্যবস্হাকে ভাঙতে প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে স্বক্ষেত্র হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন সাহিত্যকে। কিন্তু কোথাও নষ্ট করেননি আপন শিল্পবোধ ও স্বাতন্ত্র্য। সাহিত্যের স্ব-ক্ষেত্রে তিনি বহু আগেই পেরিয়েছেন দেশ-কালের গণ্ডি।
তবু প্রশ্ন রয়েই যায়— তবে কেন স্বদেশের তথাকথিত মহলে তাঁকে ব্রাত্য করে রাখা হল এতদিন? কেন তাঁকে নবীন বলার মতো ধৃষ্টতা দেখানো হল বা অতগুলো লিটলম্যাগকে স্তূপ করে রাখা হল দিনের-পর দিন? এ কি শুধুই বিরুদ্ধ মতের ভার বইতে না জানা? এককেন্দ্রিক অসৎ রাজনীতি? না প্রতিভাহীনতার দৈন্যে কদর্য ঈর্ষা? ভাবার সময় এসেছে।
সেলিম মোরশেদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে আজ যে কোনো পরিসরে আলোচনা বা আয়োজন আশাজাগানিয়া। কারণ লেখনী ও সততায় তিনি প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মত ডাইমেনশনকে অতিক্রম করে গেছেন বহু আগেই। তাঁর সম্পর্কে রণেশ দাশগুপ্ত সম্পর্কিত আহমদ ছফা’র একটি উক্তি সমার্থক—
‘… জীবনের ক্রান্তি-লগ্নে আসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করা হইলো এ জীবন লইয়া তুমি কি করিলে? সে উত্তর করিল সমগ্র জীবন দিয়ে আমি একটা বিপ্লব সাধন করিয়া গেলাম। বিপ্লবের দেখা না মিলিতে পারে আমি আমার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইব কেন?’
আগামীর পৃথিবী তাঁর সকল রচনার যোগ্য সমাদরে নবীনতম সম্ভাবনার দিন বয়ে আনুক এই প্রত্যাশা।





