
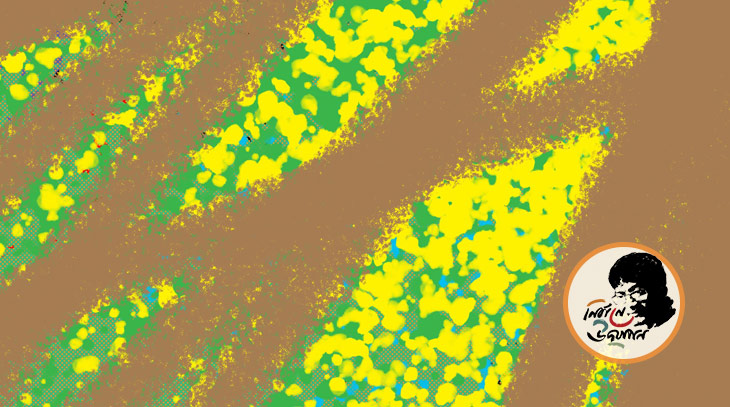
এ এক জাদুকরের খেলা
ফেলে যাওয়া ১১ পয়েন্টের খোলসে তুমি ঢুকে গেলে। তরতাজা বাতাসে চুমুক দিতে দিতে মানুষের প্রতি মুগ্ধতা ফাগুনের রাতের দাবানলের নগ্নতার নৃত্য। পাঠক হিসেবে প্রতারিত না হয়ে মরা আলোয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তীব্র ফলার দংশন। ডুবে যাওয়া আলো তার নিজের সন্তান। শ্বাসনালী বন্ধ করে আগুনের গোলক, বিদ্যের শ্লেটপাথরের স্পেসে অসংখ্য শব্দের তোড়ে অপেক্ষা করে কখন হাজার তারার দল ছুটে যাবে। আগুনের কান্নায় এ এক ঝকঝকে দিনের অবসানের মতো।
সেলিম মোরশেদ কী কারণে টানে? টেনে নিয়ে চলে উন্মুক্ত এক প্রান্তরের কাছে। একজন জাদুকর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় মনের আগুন দিয়ে বয়ান করতে থাকেন। আর আমার মতো একজন যে লিখতে চায় সে-ও তাকিয়ে থাকে মানুষটির দিকে। মানুষটির যাপিত জীবনের পাঠশালার পাঠ আমি ছাত্রের মতো অনুসরণ করি। এখানে কোনো ভনিতা নেই। নেই কোনো লবিংবাজির মধ্যে বেড়ে ওঠার ধান্ধা সেখানে। এক-একটা গল্পের টোন এক-এক রকম। মনে হয় দু-চারটে গল্প লিখলেও সেলিম মোরশেদ, সেলিম মোরশেদ হতেন। ছোট কাগজে সারাটা জীবন কাটানো এই লেখককে হেলাফেলা করলে সেটা হবে চূড়ান্ত বোকামি। সাহিত্যে ওনার ভূমিকা হেলাফেলার কোনো বিষয় নয়। জীবনের যন্ত্রণা আর সেই কষ্টের বুননে এক-একটা পাঠ। কাফকা তাঁর বন্ধু ম্যাক্স ব্রডকে বলেছিলেন সব লেখাগুলো ধ্বংস করে দিতে। পাঠক কি বই না পারফরমেন্স দেখতে চায়? অনেকে বলে, আজকালের লেখাগুলো কেমন যেন, বুঝতে পারা যায় না। চিত্রকলার পাঠের মতো অ্যাবস্ট্রাক্ট। ধরা যায় না।
অনেকে জীবনের ধারাপাত থেকে পালাতে চায়। কিন্তু আলো-আঁধারির সিস্টেমের কারণে আটকে যায় পাগলা টানের জন্য। ‘বাঘের ঘরে ঘোগ’ সেলিম মোরশেদের গল্পের বই। বইটা প্রকাশ পেলে, সেলিম ভাই আমাকে দিয়েছিলেন। আর লিখেছিলেন প্রিয় অনুজ কথাসাহিত্যিক প্রীতিভাজনেষু, নিচে নিজের নামটা লিখেছিলেন। তারিখটা ছিল ২৫.০২.০৮। আর ভেতরে অনুভব করেন বলে তিনি লিখেছিলেন। বইটা এখন যত্নসহকারে আমার কাছে আছে। পাঁচটি গল্প আছে এতে।
মৃগনাভি গল্পে ‘জোসেফ আর বিকাশ, বিকাশই প্রথম বলেছিল মৃত্যুর কথা, জোসেফ জীবন চিনেছিল তখন, বিকাশকে বুঝেছিলো, আর তাদের দেখা হয়েছিলো ধূসর খুনের ফলায় আর বৃত্তহীন গতিমুখে, পরস্পরের সঙ্গে নেয়া আর দুজনের অদৃশ্য তালুকদারিত্বে মৃত্যুকে বিস্মৃত কার অনিবার্য চ্যালেঞ্জে, কাঁটানটে, জানতো, ছায়ামৃত্যু কালো সূর্যে ফুলে ওঠা ফুটন্ত ফেনার দীর্ঘ অস্থি, হারিয়ে যাওয়া বৃষ্টির অনুস্বরে অবিরত পথরোধে ডাকা…।’ ঠিক আগের পৃষ্ঠায় কবিতার দুই লাইন: ‘সবুজ ঘাস তাকে তিরস্কার করছে— তুমি জীবিত। কালো ঘুর্ণি হাওয়ায লড়াকু গাছেরা হাত পা চুড়ে ক্রুদ্ধস্বরে তাকে বকেছে—তুমি অপরাধী! একেবারে শেষে ‘জোসেফ তীব্রলক্ষ্যটা ওই মুহূর্তে অব্যর্থ করলো; বিকাশ ছুঁড়লো ঠিক একই সময়, তারপর জোসেফের দিকে তাকিয়ে বললো: অলোকা!’
বস্তুত চাপা উত্তেজনার সমান্তরাল ভাঁজে ভাঁজে দূরবর্তী চাঁদ-সূর্য আলো-ছায়ায় আত্মাকে খুঁজে চলেছেন। শ্রেণিবৈষম্যের লাইন টেনে টেনে দ্যাখা। মৃত্যু জীবনের সাথে একসাথে চলে বলেই, হয়তো বারে বারে মৃত্যু এসেছে সেলিম মোরশেদের ভাবনার রাজ্যে।
‘বাঘের ঘরে ঘোগ’ গল্পে শুরুর লাইন ‘মৃত্যু অথবা মৃত্তিকায় এক অপূর্ণতা বা অবধারিত এরকম ধূসর বা হরিদ্রাভ সবকিছুই যেন ছিটকে পড়েছে দূর আকাশ থেকে বিস্তৃত দিগন্তে; বিরাট অরণ্য আর ধূ-ধূ ভূখণ্ড। অনুপম এই প্রান্তরে কোনো কুমারীর জাল থেকে ছিঁড়ে পড়া আহত দৈত্যের পায়ে কৃষ্ণতায় মৃত্যু আসে সোনালী শীতে…।’ গল্পে শরীরের টান উন্নয়নের স্রোতে ভেসে চলা রাজনৈতিক টানাপড়েনে হেরে যাওয়া মানুষগুলোর সামনে নাচছিল কালো পর্দার নাচ। জমাট রক্তে বইতে থাকলো নদীর কালো জল। নানা ধরনের আবেগ এখানে পেশির টানে আন্দোলিত হতে থাকে বারে বারে। এক সময় নিস্তরঙ্গ আকাশে দূরে ভেসে যাওয়া মেঘ দেখছিল বাঘি। এক তীব্র ক্লান্তি-আনা কামনায় দু’হাত বাড়িয়ে, কখনো মাটিতে পা যেন ছুঁয়ে হেঁটে চলছিল সুলতার ভঙ্গিমায়, বাঘি ছিল আনমনা। হঠাৎ সেই সময় মাটি খুঁড়ে সামনে এল। জলের মসৃণ বা হাওয়ার ছন্দে বাঘির শরীরের রেখাগুলো অপলকে দেখল, অতঃপর অনিবার্য চাঞ্চল্যে মাখনের বুকে প্রবলতায় জেগে উঠল মাংস, জল, স্বপ্ন আর গতি। আমরা দেখলাম কল্পিত চোখে মাদকতার ঘুমের ছবি। দূর থেকে বিন্দুর মতো ভেসে আসা অবিমিশ্র সত্তা অণু থেকে অংশ হয়ে গেল। এক জটিল হিসাবের মারপ্যাঁচে পুরনো ক্ষোভ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে মাখনের। একটা পট পরিবর্তন হয় মাখনের মনে। সে এখন কী করবে? বাঘির গা ঘেঁষে বসে পাতলা ঠোঁট দুটোই নিজের জোড়া ঠোঁট চাপে লালার পেলবতায়। বাঘি কুঁকড়ে গিয়ে মাথাটা নাড়ায়। সেখানে সামান্য না থাকে। মাখন বহুবার বহুভাবে অনেকক্ষণ জড়িয়ে বাঘিকে চুমু খায়। এক অসহায় ঔদ্ধত্য মাখনের ওপর ভর করে। সে বাঘির জামার ভেতর থেকে নিচের দিকে হাত ঢুকিয়ে উপর দিকে এগিয়ে গেলে অবিশ্বাস্য কম্পনে ভারসাম্যহীন হতে থাকে। কী শিহরণ? কাচ লাগানো ব্রেসিয়ারের ভেতরে হাত দিতেই এক অতীন্দ্রিয়তা হাতের তলা ভরিয়ে দিয়ে উপচে উপচে ওঠে; কোমলতাগুলো আলোর গতিতে এক সক্রিয় তালে গুরুপাক খেতে খেতে স্থানান্তর হতে থাকে বিরামহীনতায়। প্রতিমুহূর্তেই কোষের অনুভব আগ্রাসী করে তোলে। বাঘির দ্বিতীয় স্তনটি বের করে মাখন বোঁটায় মুখ রাখে। নিজের গাল ঘষে। গালের ভেতরে পোরে। স্তন: মানুষের প্রথম পিপাসা—এই দাবি! পণ্ডিত মানুষ বলে যারা নিজেদেরকে জাহির করেন আমি সেই দলে নেই। সেলিম মোরশেদের লেখা আটকে থাকা জলের থেকে বের করে আনে আমায়। শিরশির করে ওঠে শিরা, ইস্পাতের হাহাকার ব্যাধিতে লড়াই হয়ে যায় নিয়তির খেলা। গন্তব্য এখানে আমাদের অচেনা-অজানা।
‘কাটা সাপের মুণ্ডু’ সেলিম মোরশেদের অসাধারণ গল্প। ‘নির্বিকার আকাশ দেখছিলো হেমাঙ্গিনী। হঠাৎ গোলপাতার ভেতর নড়াচড়ার শব্দে দেখলো চর্বিযুক্ত পেটটি স্পষ্ট হচ্ছে আরও। তার সারা শরীর শিরশির করে উঠে মাটির উপর দুলে উঠলো। সে যেখানে শুয়ে আছে সেখান থেকে খুপরির ছাদ উঠে বসে হাত দিয়ে ধরা যায়। মাথা আর লেজ সুদ্ধ পুরো সাপটা হেমাঙ্গিনী দেখতে পাচ্ছে। পেটিটা কাঁপছে টিকটিক করে। হেমাঙ্গিনী ভয় পেলো, মনে হলো, এখন কার অবস্থান কোনো অন্ধকার শ্মশানে, সেখানে হিমচিতা জ্বালিয়েছে কেউ..’
শব্দগুলো বুক ভেদ করে চলে। জান্তব হিস হিস ভয়। একটা সময় ভয় কেটে যায় চাওয়া-পাওয়ার কাছে। ভয়ঙ্কর সাহসী হলে খেতে পাওয়া যায়, এই গল্পের শেষের লাইনগুলো এমন। ‘এটা শঙ্খচূড়। এর গলা পর্যন্ত খাওয়ায় তার দাঁতে ও মুখে বোঁটকা গন্ধ এবং মাংসের আঁশ। মুষ্টির বাইরে বেরিয়ে রয়েছে মাংসল অল্পাংশ। সে ওই শেষ অংশটুকু দাঁতে কেটে গালে লবণ ছিটিয়ে, অতি ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে খেলো। পুরো সাপটা সে একবারে খেয়েছে: তার হাতের আঙুল ও চেটোর ভেতর এখন রয়েছে কেবল দাঁতে-কাটা নিখুঁত মুণ্ডু। হেমাঙ্গিনী কাটা মুণ্ডুটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ঠাণ্ডা মাটিতে বহুদিন পর ঘুমুতে চাইলো পরম নিশ্চিন্তে।… সেই ঘুমের ভেতর হেমাঙ্গিনী জেনে গেলো, কাটা উরঙ্গের মুণ্ডুটা, হেমাঙ্গিনীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক পাক ঘুরে, জাজ্বল্যমান খুপরি ছেড়ে বেরিয়ে গেলো নিঃশব্দে।’ টিকে থাকতে গেলে সংগ্রামে জিততে হবে।
সেলিম মোরশেদ কী কারণে টানে? টেনে নিয়ে চলে উন্মুক্ত এক প্রান্তরের কাছে। একজন জাদুকর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় মনের আগুন দিয়ে বয়ান করতে থাকেন। আর আমার মতো একজন যে লিখতে চায় সে-ও তাকিয়ে থাকে মানুষটির দিকে। মানুষটির যাপিত জীবনের পাঠশালার পাঠ আমি ছাত্রের মতো অনুসরণ করি। এখানে কোনো ভনিতা নেই। নেই কোনো লবিংবাজির মধ্যে বেড়ে ওঠার ধান্ধা সেখানে।
সুব্রত সেনগুপ্ত গল্পে ‘লেখকের সঙ্গে সুব্রত’র সাক্ষাৎকার:
আত্মহত্যা বিষয়ে কী ভাবেন?
এটি একটি মুহূর্ত শুধু। এ রকম মুহূর্ত জীবনে আসতে পারে। তবে মুহূর্তটা কাটিয়ে উঠতে পারলে আবার বেঁচে থাকা যায়।
সেটি কোন মুহূর্ত?
সত্তার ভেতর যখন দ্বান্বিক পদ্ধতিটা নিশ্চল হয়।
আপনার ভেতর সেটি কি সচল?
অনেকাংশে না।
অর্থাৎ আপনি আত্মহত্যা চান?
হ্যাঁ, তবে সাহসের অভাবে পারি না।
কারণ?
নিশ্চুপ।’
কণিকা, সুকুমার, সমকাম, স্বমেহন, কাজের মেয়ের সঙ্গে সঙ্গম, ইলিয়াস চরিত্রগুলো পাপবোধ আর পাপের ফারাক দেখায়।
তবে ‘চিতার অবশিষ্টাংশ’ গল্প না হয়ে উপন্যাস হতে পারত। অনেক উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।
প্রথম পাঁচটা লাইনের পর ধরা দেয় অবয়ব। ‘সূর্য অস্ত গেলে অগ্নিময় লাল রঙ ধূসর ছাই রঙে ঢাকা পড়ে। এই সন্ধ্যামুখী চৈত্রে নজরে পড়ে সামনের ফটকমুখে পাশে ফুটে রয়েছে অজস্র লাল ফুল। চারিদিকে মোহময় গন্ধ ছড়িয়ে তারা তাদের সুদীর্ঘ বৃন্তে ঝুলছে। গোধূলীর ম্লান আলোয় তাদের গাঢ়তা লজ্জিত লালে কিছুটা ক্ষীণ, হাওয়ায় ফটকের ডানপাশের আমগাছে কাঁচামিঠে আমের হয়ে ওঠার প্রাবল্য, যেন বা দুরন্ত শৈশবের মতো, কাছে পেতে চাওয়া স্মৃতির আস্বাদ।’
জীবনানন্দ দাশ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ঘ্রাণ পাওয়া গেলে ভাবনা এলোমেলো না করাই ভালো। ব্যস্ততা ছুটাছুটি ভুলে জিরিয়ে নিলে বড্ড বেশি কি ক্ষতি হবে? কার্তিকচন্দ্র হালদার, কালিদাসী, দিলীপকুমার সেন, লিলিরানী, পুষ্পরেণু, সাঈদা, পারভীন আর শ্মশানের পরিবেশ। পুরোহিত কার্তিকচন্দ্র হালদার। ‘তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, কথা বলে সুন্দর, কাছাকাছি হয়, পারস্পরিক স্পর্শ ঘটে, কাছাকাছি বসাবসি, চুমু খায় টুপ করে, কখনও কখনও ছোটো মেয়েদের নিয়ে যায় নিজের ঘরে। পুরোহিত মানে পরের হিত করেন যিনি। শত্রুতো থাকেই, কমিটির কানেও গিয়েছে কিন্তু আশ্চর্য মেয়েদের কোনো আভিযোগ নেই, ঘৃণা নেই, বিরক্তি নেই।’
দিলীপ আর সাজাদের আলাপচারিতার শব্দগুলো দিলীপকে চিনতে কিছুটা সাহায্য করে। ‘আমার বেড়ে উঠার সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্য করেছি মেয়েরা আমাকে খুব ভালোবাসতো। আমি কখনই সেগুলো পাত্তা দেই নি। একটা সময়, যখন আমি চুড়িপট্টিতে থাকতাম সেই সময়, প্রাইভেট পড়াতাম একটু দূরে একটা বাসায়। মেয়েটির নাম অতসী। আমার সঙ্গে বয়সের ব্যবধান অনেক।’ তার কয়েক লাইন পরে দেখি অতসী জানায়, সে দিলীপকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু দিলীপের ভেতরটা সায় দিতে চায় না। আলাপচারিতা চলতে থাকে।
‘সকালবেলায় একদিন বেরিয়েছি অনেকগুলো কাজ নিয়ে। রাতে ঘরে গিয়ে খেয়ে দরোজা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ ঘুম ঘুমটা ভেঙে গেলো। চমকে উঠলাম। নিশীথরাতে নির্জন ঘরে শুয়ে কেউ যদি দেখে তার শয্যার পাশে নিঃসঙ্কোচে শুয়ে আছে এক পূর্ণ যুবতী তাহলে তার মনের ভাব কি হয়? অতসী আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। সে আমাকে চুমু খায়। আমার মাথাটা তার বুকের ভেতর রাখে।’
কিন্তু পরের দিকে আমরা দেখি অতসীর বিয়ে হয়ে যায় অন্য এক পুরুষমানুষের সাথে। সেখানে দিলীপের ভূমিকা বেশি। এক সকালে গোসল করতে নেমে পা পিছলে পড়ে গিয়ে দিলীপের দুই পায়ে বড়ো বড়ো পোকা হয়ে গিয়েছিল। একপ্রকার মাংস ছিলো না পায়ে পোকা ছাড়া। আর তখন থেকে এই শ্মশানে থাকা। শবদেহ আসলে নিচে কাঠ দেয়। এর পর শবদেহের উপর আরেক প্রস্থ, মুখাগ্নি তার পর।
সাঈদা এই গল্পের আরেক চরিত্র। ‘এখনও বিশ্বাস করে প্রেম যেখানে সেখানে সে শরীর দেবে। একমুহূর্তের জন্যে হলে সে লোকটার চোখে যদি সত্যিকার প্রেম দেখে তাহলে তার সাথে শোবে।’
প্রেম কতটা গভীর হতে পারে সেটা দীর্ঘ এই গল্পের শেষের দিকে গেলে টের পাওয়া যায়। ‘দিলীপ ঘর থেকে লোহার শিকে ভর করে কয়েক মিনিটের মধ্যে আস্তে-আস্তে ঘরের পেছনে আসেন। আমার চলে যাবার সময় হলো। সুখেন চলে আসছে দুই-একদিনের ভেতর। ফোনে জানিয়েছে-এসেই ও আমাকে খুলনায় নিয়ে যাবে… বলতে বলতে যুবতীর গলা ধরে আসে। দিলীপ সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে স্থাণুর মতো। অন্ধকারে একটা কান্নার গুমরানি ছড়িয়ে যাচ্ছে। বোঝা যায় যুবতীটি কাঁদছে। অতঃপর লোহার শিকে ভর করে ধীরে পায়ে এগিয়ে আসেন দিলীপ। দণ্ডায়মান যুবতীর একেবারে কাছাকাছি… অতসী বলে দুই হাতে দিলীপ অতসীর দুই গাল স্পর্শ করলেন। অতসীর পক্ষ থেকে কোনো বাধা নেই। কোনোকালে ছিলোও না।’
শেষের দিকে সাজাদ টের পেল। ‘সামান্য চাঁদের আলোয় যুবতী মুখটা ঘোরাতেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো সাজাদ। অতসী বলে যে যুবতীর সঙ্গে দিলীপ কথা বলছে আশ্চর্য সে—যে লিলি রানী। পরনে মেরুন রঙের শাড়ি। শাদা ব্লাউজ। কপালে খয়েরি টিপ ঠোঁটে গ্লিসারিন। খুলনা থেকে অতসীর স্বামী বিদেশে চলে গেলে অতসী এখানে লিলি রানীর নামকরণে এই সময়টুকু দিলীপের সেবা করতে এসেছে।’ একদম শেষে দিলীপের চোখ থেকে অশ্রু টপটপ করে পড়তে থাকে। সিঁদুর ভিজিয়ে দিয়ে সেই জল অতসীর মাথা থেকে অবিরত নামে। অশত্থের শেকড় ভিজে যায়। চিতার পোড়া গন্ধের মাঝে ভালোবাসার অনুভব খেলে চলে এখানে।
কার্লোস ফুয়েন্থসকে প্রশ্ন করা হল: কেউ ধরুন আপনার সামনে এসে দাঁড়াল আর আপনার চোখ দুটো বন্ধ করে দিল?
কার্লোস ফুয়েন্থস: হ্যাঁ, সেন্সর তো থাকবেই কিন্তু ফিল্মটা তখন আপনার মাথার ভেতরই পতিত হয়ে চরবে। তখন ওদের আপনাকে মেরে ফেলা ছাড়া উপায় থাকবে না। শিল্প স্বাধীনতার এই চূড়ান্ত প্রমাণ হয়ে উঠবে সেদিন।
আবারো কার্লোস ফুয়েন্থসকে প্রশ্ন করা হল: ব্যাপারটা আশ্চর্যের একটা দ্বৈত শিক্ষানবিসি যেন। লেখার প্রাথমিক পর্যায়টা যেন গর্ভধারণের মতো। তার পরই আসছে এখনকার এই যন্ত্রণাদায়ক পূর্ণতার কাল ।
কার্লোস ফুয়েন্থস: যখন আপনার জীবন অর্ধেক অতিক্রান্ত, তখন মনে হয় আপনার সামনে ভেসে উঠবে মৃত্যুর মুখচ্ছবি। মৃত্যুর মুখ ভেসে ওঠাটা দরকার বেশ গুরুত্বসহকারে লেখা শুরু জন্যেই। কিছু মানুষ আছেন যারা অন্তিমকে দেখতে পান তাড়াতাড়ি। যেমন, র্যাবো। যখন অন্তিমকে দেখা শুরু করবেন আপনার মনে হবে অতীতকে পুনরুদ্ধার করাটা জরুরি। মৃত্যু হচ্ছে সাহিত্যের বড় সমর্থক। মৃত্যুই হচ্ছে লিখনের বড়ো জীবন-দেবতা। আপনাকে লিখতেই হবে, যেহেতু আপনি আর বেঁচে থাকবেন না।
হোর্হে লুইস বোর্হেসের আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ‘ধীরে ধীরে অন্ধত্বের মতো খ্যাতিও আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি কখনোই খ্যাতি চাই নি, খুঁজি নি।’
সাহিত্যে ওনার ভূমিকা হেলাফেলার কোনো বিষয় নয়। জীবনের যন্ত্রণা আর সেই কষ্টের বুননে এক একটা পাঠ। কাফকা তাঁর বন্ধু ম্যাক্স ব্রডকে বলেছিলেন সব লেখাগুলো ধ্বংস করে দিতে। পাঠক কি বই না পারফরমেন্স দেখতে চায়?
স্ট্রাকচার অলারনেটিভ দেখার চোখ, স্পেস, সাবজেক্ট, অবজেক্ট, রিয়ালিজম, ম্যাজিক পোস্টমর্ডানিজম মিলেমিশে একাকার। ‘কান্নাঘর’ তেমনি মিলেমিশে একাকার হওয়ার মতো প্রেক্ষাপট মোশারফ, বিজয়মোহন, সদানন্দ, নিত্যনন্দ, মাধুরী, আসমাদের স্ট্রোক খেলে যাওয়ার স্থির অথচ চলমান স্ট্রিং তত্ত্ব বেমালুম চম্পট দেয় এখানে।
‘যতটুকু নগ্ন হবে তার সুরূপ ততোটুকু। বিবর্তিত প্রাণ প্রকৃতির নগ্নতাটুকু যখন দেখতে পায় তখন সে ঈশ্বর। শেষমেশ নিত্যানন্দ শহরে গিয়েছিলো, ঠিক করেছিলো কিছু খাবে না; কিন্তু একটা দামি হোটেলে রুম ভাড়া করে কিছুক্ষণের জন্যে থেকে কেঁদে আসবে।’ তাই করেছিল নিত্যানন্দ। সোনালি জীবন টেনে থাকে টান ফোর্সের মতো করে।
‘এক বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে প্রশ্ন করেছিলেন, জগতের সবচেয়ে কঠিন কাজ কী? দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান কী? আর এই মূল্যবান বিষয়টির গন্তব্য কী?
চারপাশে অসামান্য এক নিস্তব্ধতার পরিবেশ বিরাজ করছিলো। যশোদা মিনিট দশেক সময় নিলেন। নাকে এবং চিবুকে সামান্য ঘাম এসে জড়ো হলো। জগতের সবচেয়ে কঠিন কাজ আত্মপ্রেম থেকে বের হওয়া। দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান হলো প্রেম আর এর গন্তব্য আত্মতৃপ্তি।’ যশোদা আমাদের কঠিন ফিলোসফিকাল টার্মটার সহজ ব্যাখ্যা দেয়। শূন্যতার হিসেবে চলে জীবনের ভেতরগত জীবন। তাই তো দেখি কী সহজ অথচ জটিল বিশ্লেষণ! ‘শূন্যতার যে সংজ্ঞাই দিক না কেন তার পূর্বপুরুষেরা, বিজয় মোহনের মনে হয়, বোধহয় প্রথমটা যন্ত্রণা যখন সবকিছু ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিতে ইচ্ছা করে, দ্বিতীয়টা বেদনা, বেদনা কান্না তৈরি করে, সে কান্না যখন অতলস্পর্শী অগ্নিবাষ্পে রূপ নিয়ে শুষ্ক হাহাকার হয়ে ওঠে তখনই মানুষের অন্তর্গত শূন্যতা দেখা দেয়।’ যন্ত্রণার ডুবে যাওয়া শরীর ডুবতে থাকে শূন্যে।
গল্পের শেষে কান্নাদের দলাগুলো বাইরে বের হয়ে আসে। বিজয় মোহন এক-পা যেন এগিয়ে আসেন। যশোদা প্রথমে, তারপর বিজয়মোহন, সদানন্দ তার পরে, একটা সোজা মানুষদের লাইন আসতে আসতে এগোতে লাগল নিত্যানন্দের দিকে। ‘চোখে পানি আসে নিত্যানন্দের। দুজনের হত্যাকারী সে। নিজের দুই সত্তাকে দুদিক থেকে দুবার সে মেরেছে, নিজেকে এভাবে হত্যা করে নিত্যানন্দ আগত অনেক মানুষের লাইনটার দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখভরা কান্নায়।’
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার লাইন হয়তো মিশতে পারে এখানে।
‘সোনালী সুতোর ঋণে পৃথিবীকে দিয়েছো অশেষ
যন্ত্রণা, এখনো মরো, মরে যাও—শুনবে দূর থেকে’
‘রাতে অপরাজিত গাছে ফুল’ এই বইয়ের শেষ গল্পটি আমার খুব প্রিয়। এরকম গল্প আমি নিজেই লেখার চেষ্টা করি। গল্প শেষ হয়ে গেলেও যার রেশ থাকে দীর্ঘদিন। ‘মহান সূর্য আর অভিমানী মেয়েটি এবং তুচ্ছ বালির গল্প।’
‘সে এক অন্ধকার শহরের কথামালা।
সেখানে কখনও সূর্য উঠতো না, রাত আর দিন অন্ধকারে থাকতো, অন্ধকারে থাকতে থাকতে থাকতে সবাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। প্রতি রাতে সামান্য সময়ের জন্য শহরবাসীরা সূর্যকে কল্পনা করে মশাল জ্বালাতো। এই সময়টুকু ছাড়া তারা তাদের সমস্ত কাজ করতো অন্ধকারে, এমনকি তারা অংক করতো ওইভাবে। সেই শহরে একটা মেয়ে অন্ধকারে থাকতে থাকতে তার গায়ের রঙ পাকা গমের মতোন হয়। সে রাতদিন সূর্য না ওঠার জন্যে কাঁদতো আর সূর্যের উদ্দেশে চিঠি লিখতো প্রতিদিন; সে যখন চিঠি লিখতো তার চোখ থেকে অশ্রু টপটপিয়ে পড়তো চিঠির ওপর। সূর্য যেখানে ওঠে সেখানে আমি যাবো।’ — বিড় বিড় করে বলত।
‘একদিন মেয়েটি সিদ্ধান্ত নেয় শহর ছেড়ে সূর্যকে ছেড়ে সে আজই বের হবে। আপন মনে সে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে থাকে একশো রাত।’
আমরা দেখতে পাই। কেউ তাকে সাহায্য করে না। অরণ্য-পাহাড়-জলাশয় কেউ না। বালিও প্রথমে তাকে সাহায্য করে না। তবে একটা সময় বালির মন ভিজে ওঠে। অনেক রাত অবধি বালি নানানকিছু ভাবতে থাকে।
শেষের কয়েকটা লাইন হার মানায় সবাইকে। ‘ভোরবেলা ঘুম ভাঙে মেয়েটির। আশ্চর্য হয় সে। এ কি দেখছে! সে একটা ঘরের ভেতর। চারপাশ থেকে আসছে রোদ আর রোদ। সারারাত ধরে তুচ্ছ বালি নিরলস পরিশ্রমে নিজেকে আতশ কাচে রূপান্তরিত করে একটা কাচের ঘর বানিয়েছে। যার ভেতর দিয়ে সূর্যরশ্মি ভেদ করে মেয়েটিকে সূর্যমুখী করছে আর তার ভিজে চিঠিগুলো শুকিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটি চারপাশে খোঁজে। কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যে কোথাও একটা কণা বালিও সে দেখে না। অভিমানী মেয়েটি মহান সূর্যের দিকে তাকিয়ে তুচ্ছ বালির কথা ভাবে। কোনোদিন সে আর একটি বালির কণাও দেখতে পায় নি।’
অমিয়ভূষণ মজুমদার ‘কেন লিখি’ প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘কেন লিখি—এটাও একটা সমস্যা হতে পারে। এ সমস্যার অর্থ এই নয় যে লেখক হতাশ হয়ে পড়েছে লিখে কোনো লাভ নেই দেখে। বরং যেন এমন একটা ঝোঁক আছে যে হতাশা নানা রকমের থাকা সত্ত্বেও লিখছি এবং তারই কারণ খোঁজা। কোনো কোনো লেখক বলেছেন না লিখে উপায় নেই বলে লিখে থাকেন তাঁরা। তাদের এ কথা শুনে প্রথমেই যা মনে হয় সেটা হচ্ছে এই যেন কিছু একটা তাদের পেয়ে বসেছে, সেই লিখতে বাধ্য করে। এ ভঙ্গিটা পাঠকসমাজকে অতীন্দ্রিয়ার সান্নিধ্যে এনে চমকিত করতে পারে কিন্তু এ রকম প্রেরণার উৎসে মানুষ আজকাল আর বিশ্বাস করে না।’
অমিয়ভূষণ মজুমদার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, মার্কেজ, বোর্হেস, হেমিংওয়ে, জেমস জয়েস, ফুয়েন্তেস, কাফকা, হারুকি মুরাকামি, চিনুয়া আচেবে, র্যাঁবো, বিনয় মজুমদার, জীবনানন্দ দাশ সবাই লিখেছেন একেকজনের স্টাইল, ধরন, শব্দের বুনট এক এক রকম। মিল নেই কারুর সাথে। তাই তো লিখতে হয়।
জীবনানন্দ দাশের কয়েকটা লাইন—
আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হ’য়ে উঠেছে
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার
যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ তার মুখ আমি কোনো দিন দেখি নি
পরিসর, ক্ষমতা, শূন্যতার মাঝে নিজেকে দেখা, অতিচেতনায় ছবির ভেতর অন্তর্লীন হাসিতে শোকের পাঠ গোপন থাকে তবু অনেক কথা। এলিমেন্ট, নেটওয়ার্ক, ক্যাপিটালিজম ভেঙেচুড়ে অদ্ভুত অনুরণনের স্ট্রোক পাঁজরে ধাক্কা দেয়।
বিনয় মজুমদারের কবিতার মতো—
পৃথিবীতে কোনোকিছু সরল রেখায় যাওয়া পুরো অসম্ভব
ওই রেলগাড়িগুলি পৃথিবীর বাঁকা পিঠে
বাঁকা পথ ধরে চলে যায়।
সেলিম মোরশেদের লেখা তাই মাথার ভেতরে নিয়ে রোদের আলোকতরঙ্গে গিয়ে নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে হারিয়ে ফেলা।





