
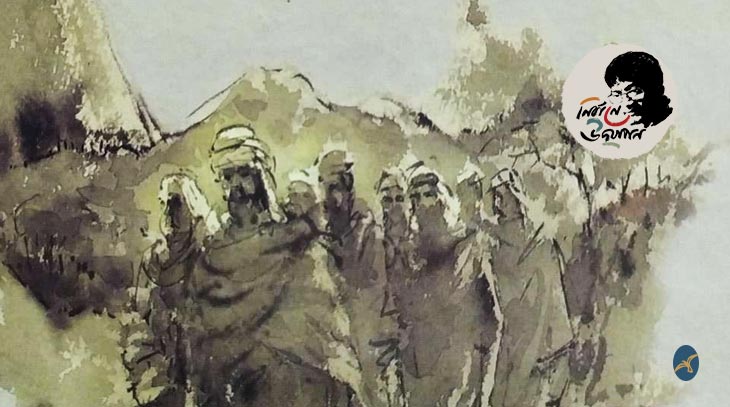
মানুষ উত্তম: পর্যালোচনা
নাটক জীবনের কথা বলে। নাটক সমাজকে প্রতিরূপায়িত করে। নাটক যেন এক দালিলিক প্রমাণ যা ইতিহাস, সমাজ, রাষ্ট্র এবং মানুষের কাছে এক আয়না স্বরূপ। আমরা যেমনটা জানি সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ অনুকরণ করতে অভ্যস্ত। আর এই অনুকরণ অভিনয়ের এক ভিত্তি স্বরূপ। আজ আমার কথা এই ‘অভিনয়’ নিয়ে নয় বরং প্রচলিতভাবে আমরা অভিনয় করার জন্য যে প্লট বা বৃহৎভাবে পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করে থাকি তা নিয়ে। নাটক লেখার বা স্ক্রিপ্টিং বহু সময়ে বহুভাবে বিবর্তিত হয়েছে, যাকে আমরা স্টাইল বলে থাকি। ধ্রুপদীবাদী নাটক থেকে বাস্তববাদী নাটক বা ত্রি-ঐক্য থেকে নিপুণ্য নাট্য যেন এক একটি সময়কে অতিক্রম করা। নাটকের বিষয়বস্তুও গুরুত্ব পেয়েছে তার সমসাময়িক অবস্থার চাহিদা মেপে। ঈশ্বর, রাজা, পরে বিজ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাস্তব সত্যকে খোঁজা যুগ বিভাজনে আমরা বহু বিষয়বস্তুর মুখোমুখি হই। তবে বিশ্বযুদ্ধদ্বয় যেন শিল্পের সকল ক্ষেত্রে এক বিশাল নাড়া দেয়। পেছনের সব ভুলে বা বাতিল করে শিল্পীরা পাড়ি জমাতে চান অন্য এক জগতে। এত নিপুণতার কিছু নেই, এত রাখ-ঢাকের কিছু নেই। চলতে হবে যা যেভাবে আছে তা নিয়েই।
নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে ধর্মকে আমরা পেয়েছি বিভিন্ন সময়ে। মঁলিয়ের রচনা করেছিলেন ‘তার্তুফ’। যেখানে নামচরিত্র ‘তার্তুফ’ ছিল এক ভণ্ড প্রতারক যে কিনা ধর্মকে সামনে রেখে তার ভণ্ডামি চালাত। আবার পরবর্তীতে বার্ট্রান্ড ব্রেখট লিখেছেন ‘মাদার কারেজ এন্ড হার চিল্ড্রেন’। যেখানে পাই ত্রিশ বছরের ধর্মযুদ্ধের এক নির্মম কাহিনি। আরও বহু নাটক রচিত হয়েছে ধর্মকে বা ধর্মীয় বিষয়কে বা ব্যক্তিকে উপজীব্য করে। আমাদের গ্রামবাংলার রামায়ণ গান, গাজীর গানেও পাই ধর্মের ছোঁয়া।
আজকে আমার যে আলোচনা, তা মূলত ‘সেলিম মোরশেদ’ ও তাঁর নাটক ‘মানুষ উত্তম’। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় তাঁর দৃপ্ত পদচারণা থাকলেও নাটকে এটাই তাঁর প্রথম। তবে একে নাটক বলতে শুধু সংলাপনির্ভর কথা নয় বরং এক গবেষণাকর্মই বলা যায়।
নাট্যকার যেমনটি বলেছেন౼ ‘মুসলমানদের পয়গম্বর ঈশার জীবন ও কর্মকে জানার প্রয়াস থেকে এই তাগিদ। এই দেখার অবকাশ হয়তো এখানে বেশি ছিলো আর এর ভেতর দিয়ে যে চাওয়াটা ছিলো, ভিন্নভাবে যিশুকেও দেখা। সম্মানিত ঈশা বা যিশু মূল পরম্পরাগত দিক থেকে একই। ধারাবাহিকতায় সংলগ্ন মানুষদের একে অপরের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ সেটাও শিক্ষণীয়।’
‘মানুষ উত্তম’ নাটকটি তেরটি পর্বে রচিত। মূল চরিত্র প্রেরিতপুরুষ ‘ঈশা’। নাটকের ঘটনা যেভাবে প্রবাহিত হয় তার সাথে আমরা পাঠককুল কোনো-না-কোনোভাবে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত থাকতে পারি। কেননা এ কাহিনি জলজ্যান্তভাবে বিভিন্ন উপায়ে আমরা জানি। কিন্তু লেখার গাঁথুনিতে এবং সংলাপের বর্ষাবাণে আমরা যা পাই তা হল শ্রেণিসংগ্রাম এবং অন্ধ অনুকরণের বদলে সত্যকে জানানোর যে আকাঙ্ক্ষা। কথাসাহিত্যিক মাসুমুল আলম তাঁর ‘আধ্যাত্মিকতা ও চিরায়ত বিশ্বরাজনীতির আগুন’ প্রবন্ধে লিখেছেন౼ ‘…নাটকটিতে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কিংবা ধর্মীয় সত্য অপেক্ষা অনেক বেশি আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা ক্রিয়াশীল এবং সে কালে আর আজকের কালের মধ্যে নাটকের চরিত্রগুলোর মানানসই চিত্রণ আর উত্তেজনাপূর্ণ অগ্নিগর্ভ সময়ে পরিবর্তন-প্রচেষ্টার প্রধানতম পথ-প্রদর্শক সম্মানিত ঈশা-কে অনুভূতিপ্রবণ একজন ‘মানুষ-উত্তম’ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।’
উপরোক্ত বর্ণনায় আধ্যাত্মিকতার বিষয়টির চেয়ে আমি মনে করি এ নাটক সকল সময়ের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সনদ প্রদানকারী যেসকল ঘটনা বা মুক্ত ব্যক্তিবর্গের কথাই বলে। মার্কস যেভাবে বলেন যে, শোষণ থেকেই শ্রেণির উৎপত্তি। যে সমাজে শোষণের অস্তিত্ব নেই, সে সমাজে শ্রেণির অস্তিত্ব নেই। ‘মানুষ উত্তম’ নাটকে শোষণ আছে তবে তার রূপ ধর্মীয় আদলে। এখানে হয়তো কোনো ভূস্বামী নেই কিন্তু আছে ধর্মীয় গুরু।
নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে আমরা বিস্তারিত বর্ণনা পাই যেখানে প্রকাশ পায় ‘দেশটা খুব অভিশপ্ত, সমৃদ্ধিগুলো কোথায় গেলো?’ মেয়েরা সম্মিলিত স্বরে সুর তোলে౼
‘দান করো জলাধার, হৃদি দ্বার খুলিয়া
দান করো জলাধার, উপচায়ে পড়িয়া
…
হৃষ্টচিত্তে করো দান, অর্পি নিজে মনপ্রাণ
এমনই তো দাতা ঈশ্বর চান প্রেমের ধর্ম দান।’
পৃথিবীর বুকে মানুষ হিসেবে আমাদের এমনই তো চাওয়া যে এ পৃথিবী, পৃথিবীর মানুষ থাকবে প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ। কিন্তু তা হয়তো হয় না তাই তৃতীয় পর্বে দেখি শান্তিপ্রিয় এসীন সম্প্রদায়ের জেলে, ধোপা ও সম্মানিত সাধু ইতিহাসবেত্তাদের আলোচনায় যে–শান্তি প্রিয় অর্থই সর্বংসহা নয়। ফিলিপের সংলাপে পাই౼
‘আমরা রক্ষণশীল (সাদ্দাসি) এবং প্রগতিশীল (ফারিসি) নই, আমরা এসীন। চার হাজার মানুষ নিয়ে এই এসীন সম্প্রদায়। আমরা ভগবচ্চিন্তায় যুক্ত থাকতে ভালোবাসি। সোনা ও রূপার আকাঙ্ক্ষা আমাদের নেই।’
ফিলিপ আরও বলেন౼
‘জর্দান নদী থেকে সাগর পর্যন্ত আমরা যখন মাছ ধরি, তখন জীবন বিপন্ন করি। বেচতে হয় সেইসব বণিকদের কাছে, যারা দাম নিজেরা নির্ধারণ করে, নামকাওয়াস্তে মাঝে মধ্যে কিছু মূলধন দেয়, এই দোহাই দিয়ে বাজারটা আটকে রাখে। আমরা তাদের যাবতীয় কাপড় পরিষ্কার করি। অথচ ন্যায্য টাকা আজ অবধি পাইনি। আমরা অল্পে তুষ্ট, তৃপ্ত౼ তার অর্থ এই না, আমাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক নিতে উদাসীন।’
উপরোক্ত সংলাপে বিপ্লবের আভাস পাই। সম্মানিত প্রেরিত পুরুষ ঈশা-কে দেখতে গিয়ে নাট্যকার তাঁর গবেষণা থেকে ফিলিপের মুখে যে সংলাপ দিলেন তা প্রতিটি শ্রেণিনির্যাতিত মানুষের মুখের কথা বলে মনে হয়। এটি কোনো অলীক আলোর বিচ্ছুরণে ধর্মের নীতিজ্ঞান নয় বরং নিপীড়িত জনগণের নিজ অবস্থা পরিবর্তনের অদম্য ইচ্ছার প্রকাশ।
ফিলিপ:
‘এই রোমানদের কোনোকালে কোনো মানবিক ধর্ম ছিলো না। আব্রাহাম থেকে এলিজা, দাউদ থেকে মূসা পর্যন্ত কোনো ধর্মকেই এরা সম্মান করেনি। এদের মন্দির থেকে শুধু প্রচারিত হয়েছে পৌত্তলিক ধর্মের দেবদেবীদের উদ্ভট সব গল্প।’
ফিলিপের সংলাপে এই ক্ষোভ এই যন্ত্রণা নিম্নবর্গীয় জনগণ আজও বয়ে চলে। ঈশ্বর থাকেন ওই ভদ্রপল্লিতে যেন। দেব-দেবীর উদ্ভট গল্প দ্বারা যে হেজিমনি তৈরি করে তাতে জনগণ আর কত দিন মজে থাকবে।
নাটকে চতুর্থ পর্বে তরুণ ঈশা-কে দেখি চোখে অফুরন্ত শক্তি, উজ্জ্বল যুক্তি বিচ্যুত হয় না, নিরুদ্দম হতাশাহীন। স্বাধীনতার স্বপ্নে উজ্জীবিত টগবগে এক প্রাণ। জেরুজালেমের এক মন্দিরে বিদ্বান পুরোহিত আর প্রবীণ পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনারত౼ যার বিষয় দাসদের মুক্তি, ব্রাত্যজনের মর্যাদা বিকাশ আর চলতি ধর্মের মৌল ব্যাখ্যা প্রদানকারী স্বার্থান্বেষী মহলের প্রতি বিদ্রোহ। এই সবই যে সাধারণ নিপীড়িত মানুষের মনের গহিনের কথা। যা তারা পারে না বলতে। খোঁজে এক নেতাকে, যে বলবে একদিন এইসব কথা। এই তরুণ ঈশা তো নয় কোনো দেবদূত, দূরবর্তী পূজনীয়। এ যে নিপীড়িত মানুষের পাশেই অবস্থান করে, কথা বলে তাদের ভাষাতেই। নিজের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে সে বলে–
ঈশা:
আমি ইমানুয়েল, ইশু (নেতা) ঈশা, *যমুশা এবং যিশু। গলিলি রাজ্যের নাসারতের লোক।
তিনি আরও বলেন,
‘সম্মানিত ইব্রাহিম (আব্রাহাম) থেকে আমার ব্যবধান খুবই অল্প। বিয়াল্লিশ পুরুষ। বনী ইসরাইল ও বনী ইসমাইল দুই গোত্রেরই আন্তসত্তা আমি। আমি তাদের ভেতর সাম্যতা রক্ষা করতে এসেছি।’
এ যে নিরহংকারী আত্মপ্রকাশ, দৃপ্তভাবে নিজেকে প্রকাশ তা যেন এক উন্মুক্ত আকাশের ইঙ্গিত দেয়। বিভিন্ন আলোচনায় ঈশা এ-ও বলেন যে, ‘ভুল বুঝলে। আমি কোনো ধর্ম দিতে আসিনি।… আমি ভোগের দাসত্ব করি না, তাই। যে ভোগের দাসত্ব করে না তার কখনো শাস্তি হয় না।’ ঈশার এ ধরণের কথায় সাইমন উৎসাহিত হয়ে বলে ওঠেন౼ ‘মা-বাপের আঁচল ধরে নিজের আশ্রয় খুঁজছে না। বরং আশ্রয়হীন মানুষকে নিয়ে ভাবে। ছেলেটার কথায় যুক্তি আছে।’ এই যুক্তির কথা মোটেও ভালো লাগে না প্রধান পুরোহিতের। তিনি ক্রুব্ধ হয়ে সাইমনকে চুপ থাকতে বলেন। বলেন౼ ‘একজন অবাস্তববাদী লোক তুমি। যুক্তিই সব না। প্রমাণের ওপর বিশ্বাস দাঁড়ায়। ওকে অযথা গুরুত্ব দিচ্ছো।’ উত্তরে ঈশা বলেন౼
‘তোমাদের কাছে গুরুত্ব পাবার জন্যে আসিনি। এসেছি, ভুল পথে চলছো তা অবহিত করতে। প্রমাণ নিয়ে যে কথা বললে তাতে মনে হয় অনেক কিছু জানো কিন্তু বোঝো না। জানা ও বোঝা এক না।’
সত্যিই তো জানা আর বোঝা তো এক নয় আর প্রধান পুরোহিতরা তাঁদের নিজস্ব হুকুমত জারি রাখতে যা জানেন তাই রাখতে চান বোঝা তো সে সূদূরে। বুঝতে গেলে বোঝাতে গেলে হুকুমতে টলমল অবস্থার আকাঙ্ক্ষা যে তাদের নিরবধি।
ঈশার কথায় রাব্বী এবং কাতিবীদের অস্থির করে তোলে౼
‘প্রমাণ যেসব পূর্বশর্তের উপর দাঁড়িয়ে সেগুলো বিনা প্রমাণে মেনে না-নিলে প্রমাণ নিজেই তখন অচল হয়ে পড়ে। কথাটা নতুন না।’
এই পর্বে মূলত আমরা দেখি প্রচলিত অবস্থা/ব্যবস্থার প্রতি ঈশার প্রাথমিক এক ধাক্কার ঘটনা যা ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।
পঞ্চম পর্বের প্রারম্ভিক বর্ণনায় দেখি দাসদের সাথে গণ্ডারের রক্তাক্ত লড়াই আর মালিকশ্রেণির আমোদ। এই পর্বে সম্মানিত ঈশা পূর্ণবয়স্ক। তাঁর মতাদর্শ, চিন্তাও যেন পূর্ণতা পেতে শুরু করেছে। দেখি যে, বার্নাবাস ঈশার আদর্শ ও কার্যক্রমের কথা চিঠির মাধ্যমে অন্যদের জানাচ্ছে। ঈশার চারিত্রিক একটি মহৎ দিক প্রকাশিত হয় এই সংলাপে যে౼
ঈশা:
‘যোহান, আমি কোনো শাসক না, নেতাও না, এমনকি ধর্মপ্রচারকও না। আমি প্রেরিত পুরুষদের ধারাবাহিকতা। আমরা আন্দোলন করছি একে অপরকে ভালোবেসে। এত ‘আপনি-আপনি’ ‘হুজুর-হুজুর’ করলে কাজ করবো কী করে। রোমানদের আভিজাত্য যদি ভাঙতে চাও, নিজেকে আগে ভাঙো। কারো প্রতি শ্রদ্ধা আসে তাঁর আত্মত্যাগ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেখে। সম্মান আসে কর্তব্যপরায়ণতা দেখে। ভালোবাসা আসে বিশ্বাস থেকে। শক্তি মনে করে আমাকে ভালোবেসো না। আমি একজন মরণশীল মহিলার গর্ভজাত সন্তান।’
যে ব্যক্তি তামাউনের কাটা হাত-পা প্রকাশ্যে জোড়া দিয়েছেন; মাটির পাখিকে প্রাণ দিয়েছেন, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করেছেন এমনকি মৃত মানুষকেও বাঁচিয়েছেন তিনি যখন নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে পরিচয় দেন তখন প্রধান পুরোহিত বা অন্যান্য কাতিব বা ধর্মব্যবসায়ীদের যে মুখোশ যাদের কর্ম সাধারণ মানুষকে বিচ্ছিন্ন রাখে পরমের থেকে তা ভেঙে যায়। এই পর্বের শেষে ঈশার মুখে দৃপ্ত বাণী౼
ঈশা:
‘আগামীকাল মধ্যাহ্নে, মসজিদই হোক বা মন্দিরই হোক বা গির্জাই হোক, যে কোনো উপাসনালয়ে যেখানে শয়তানরা থাকবে সেখানে আমি আক্রমণ করবো। এ আক্রমণ অন্যায়ের প্রতি ন্যায়ের। শ্রেণিশত্রুর বিপরীতে বিপ্লব।’
ষষ্ঠ পর্বে বাইতুল লাহামের এক উপাসনালয়ে পাঁচ হাজার লোকের সমাবেশে ঈশার সরাসরি প্রশ্ন౼
‘এবাদতের জায়গায় এসব কী হচ্ছে? যাদের দেখছি সব তো ব্যবসায়ীরা। কল্যাণমূলক কাজ কই?’
প্রশ্নের উত্তরে প্রধান রাব্বী সুকৌশলে অন্যদের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে সবার দিকে তাকিয়ে বলে౼
প্রধান রাব্বী:
‘দেখেন আপনারা, কোনো ধর্মপরায়ণ লোক, প্রভু-প্রেরিত কোনো মানুষের ব্যবহার কি এমন-আচরণ এমন হবে? ওর সঙ্গের লোকগুলোর দিকে আপনারা অনুগ্রহ করে তাকান। চেহারা এবং পোশাকের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য আছে কিনা দেখেন?’
ঈশা:
‘আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি যথেষ্ট অশালীন হতে পারিনি। যা আমাকে হতে হবে। জ্ঞানপাপীদের দুটো অস্ত্র থাকে: মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আর চুরি করা সৌন্দর্য।’
জ্ঞানপাপীদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি যে কতটা ভয়ঙ্কর তার পরিচয় ইতিহাসে সাক্ষী। এই জ্ঞানপাপীদের বিরুদ্ধে লড়াই বর্তমানেও চলমান। সাধারণ মানুষ এই জ্ঞানপাপীদের কথাই সহজে শুনতে চায়, মেনে নেয়। তবে এসবের মাধ্যমে ঈশার ভক্ত, অনুরক্ত সমর্থক যেমন বাড়ছিল তেমনি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও দানা বাঁধছিল।
সপ্তম, অষ্টম ও নবম পর্বে ঈশার কীর্তি ও মহান চিন্তার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাই। তিনি মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত এক নপুংসককে আল্লাহর ইচ্ছায় সুস্থ করে তোলেন। ব্যক্তিপূজা আর মানুষ-ভজনা নিয়ে তিনি তাঁর চিন্তা/বক্তব্য পরিষ্কার করেন।
ঈশা:
‘ব্যক্তিপূজো আর মানুষ-ভজনা এক না। ব্যক্তিপূজা পূজারিকে দাস করে। মানুষ-ভজনা ভালোবাসতে শেখায়। অনন্ত সত্তার সাথে একাত্ম হয়। যাকে তুমি পুজো বলছো এটা ভজনা। ব্যক্তির কাছে ব্যক্তির কোনো প্রত্যাশা থাকে না। এই ভজনা সমষ্টির জন্য জিকির স্বরূপ।’
লালন সাঁইজির মুখেও শুনি౼ মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।
বাইতুল লাহাম বা মসজিদ প্রাঙ্গণে বিপুল জনতা, প্রধান রাব্বী ও অন্যান্য কাতিবীদের সম্মুখে ঈশা বলেন౼
‘যদি আমি অপরাধ করে থাকি নিন্দা আমার প্রাপ্য মুকুট। সুতরাং নিশ্চয়ই আমি অবনত হবো। কেননা আমার স্রষ্টা সর্বজ্ঞ౼ তাঁরই ইচ্ছায় আপনার তিরস্কার আমার জন্য নৈতিক আমানত।’
এর উত্তরে প্রধান রাব্বীর স্বীকারোক্তি౼
‘বলতে বাধ্য হচ্ছি, রোমের সাধারণ জনতা ও সামরিক সৈন্যদের মতো আমরাও আপনাকে ভালোবাসি, বিশ্বাস করি…
আপনি যে অর্থনৈতিক সাম্যের কথা বলেছেন, সম্ভ্রান্ত সুশীল ধার্মিকদের সুবিধাবাদী চরিত্রের কথা বলেছেন তা কিয়দংশ সত্য। যদিও এই অর্থনৈতিক কাঠামো আজ পরিবর্তন তাদের নিজেদেরও ইচ্ছা-সাপেক্ষ নেই।’
কিন্তু এই স্বীকারোক্তির পরও ঈশা’র মুখে যখন ইব্রাহিমের গৌরবময় পুত্রের নাম ‘ইসমাইল’ উচ্চারিত হয় তখন প্রধান রাব্বী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বলেন౼
‘বাঁদীর পুত্র ইসমাইল? না౼আর না।’
প্রধান রাব্বীর মুখে তখন শ্রেণি বৈষম্যের কথা স্পস্ট হয়౼
‘…পাক কিতাব বলে যে, বাঁদী ও তার ছেলেকে যেন বের করে দেওয়া হয়, কারণ বাঁদীর ছেলে কোনোমতেই স্বাধীন ছেলের সঙ্গে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ পেতে পারে না।’
এ যেন এক সম্ভ্রান্ত সাম্প্রদায়িকতা। সম্মিলিত জনতাকে এক ভ্রান্ত আভিজাত্যের চাদরে মুড়ে নিজেদের অধিকারের কথা ভুলিয়ে রাখা আর যে বা যারা অধিকার আদায়ে সচেষ্ট তাদের বিরুদ্ধে জনতাকে লেলিয়ে দেয়া। এমনকি স্বয়ং রাজাও এই কপটতার কাছে নিরুপায়। তাই তো রাজা হেরোদ বলেন౼ ‘আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তার অপরাধটা কোথায়।’ অদৃশ্য কণ্ঠে সবাই শুনতে পায়౼
‘আমি সর্বদা সমাজগৃহে ধর্মধামে শিক্ষা দিয়েছি, যেখানে সকল ইহুদিরা একত্রিত হয়। আমি বঞ্চিত মানুষের পক্ষে কথা বলেছি এবং প্রভুর নির্দেশে পরবর্তী যিনি আসবেন তাঁর সর্বোচ্চ গুরুত্বের কথা বলেছি। আব্রাহামের দুই স্ত্রীকে আমি সমান মায়ের মর্যাদা দিয়েছি। গোপনে কিছু কহি নাই।’
ধর্ম দ্বারা রাষ্ট্রকে বাঁধার ফলে জনগণের যে পরিণতি এবং রাজাদেরও যে টালমাটাল অবস্থা হয় তার পরিচয় প্রকাশ পায় ইহুদিগণের সংলাপে౼
‘জনাব ফালতিস (পিলার্ত), যদি তাকে শেষ না করা হয় শুধু আমাদের ধর্মই শেষ হবে না, তোমারও হুকুমত খতম হবে। যদি আমরা তাকে ছেড়ে দেই, সমস্ত লোক তার ওপর ঈমান আনবে। তার লোকগুলো আমাদের দেশ দখল করে নিবে।’
কী ঠুনকো তাদের বিশ্বাস, কী ঠুনকো তাদের রাষ্ট্রের অবস্থা যা ভেঙে পড়বে বা দখল হবে ভেবে হাজার হাজার মানুষকে উন্মত্ত করে তোলে একজনের বিরুদ্ধে। অথচ ওই একজনের কথায় আছে যুক্তি, আছে মুক্তি। এভাবেই নাটকের শেষ এগিয়ে আসে।
মাসুমুল আলম বলেন, ‘যেহেতু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনীতি ও স্বার্থপরতায় সত্য বিকৃত হয়ে যায়, ‘মানুষ উত্তম’ নাটকে নাট্যকার সেই মিথ্যার উৎপীড়ন দেখানোর পাশাপাশি শেষতম পর্বে শুভ-অশু-অশুভ’র দ্বন্দ্ব চিহ্নিত একটা শিল্পসত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটান।’
‘মানুষ উত্তম’ নাটকটি যে সকল তথ্য-উপাত্তের ওপর ভর করে এগিয়ে যায় সেখানে চুলচেরা বিশ্লেষণ খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ যেন চিকন সুতার উপর হেঁটে যাওয়া। মুহূর্তের অসতর্কতায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা। নাটকের গল্প, চরিত্রের সংলাপ বর্তমান সময়েও সমানভাবে প্রযোজ্য দেখি কারণ এই বর্তমানেও আমরা শ্রেণিসংগ্রামে লিপ্ত এবং অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় গুরুদের হেজিমনি দ্বারা আক্রান্ত। তবে নাটকের প্লট খুবই স্পর্শকাতর।
কবি মহিউদ্দিন মোহাম্মদ বলেন, ‘মিশরে তাওফিক আল হাকিম শেষ নবীকে নিয়ে ‘মুহম্মদ’ নাটক লিখেছিলেন বিশ শতকে। তা নিয়ে বিড়ম্বনা ঝড়-ঝঞ্ঝা, অনেক ধকল। তবে শেষতক পাকিকুলে মিলল শ্রুতিনাটকের স্বীকৃতি, যথার্থ বিচার সময়ের হাতে থাকে। যিশুখ্রিস্ট বা নবী ঈশাকে নিয়ে বহুধা মত, বিভক্তি-ধর্মের দেয়াল তুলে বিভাজন। বিষয় হিসেবে একে ভিন্ন মাত্রায় পরিবেশন খুবই দুরূহ।’ তবে এই দুরূহ কাজে নিজস্ব প্রজ্ঞা আর বিশ্লেষণী মন-লেখনী দ্বারা নাট্যকার সেলিম মোরশেদ ‘মানুষ উত্তম’ নাটকটি করেছেন অনন্য।
তবে পরিশেষে একটু ভিন্ন কথার অবকাশ থেকে যায়। নাটক অবশ্যই পাঠ্য তবে তা পূর্ণতা পায় দৃশ্যায়নে, অভিনয়ে। আমার জানা মতে এই নাটকের এখনো কোনো মঞ্চায়ন হয়নি। নাটকে উপর্যুপরি বর্ণনা আর তথ্যনির্ভর সংলাপকে বাগে আনতে অভিনেতা ও নির্দেশককে বেশ বেগ পেতে হবে বলে মনে করি। তবে নাট্যকার প্রদত্ত গান, কবিতা ও নৃত্যের বিস্তারিত বর্ণনা বেশ খানিকটা সাহায্য করবে বলে আশা রাখি। বর্তমান সময়ে এমনই র্যাডিকেল প্রযোজনা দাবি করে। আশা রাখি অদূর ভবিষ্যতে এই ‘মানুষ উত্তম’ নাটকটির পাঠকসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং যেকোনো মাধ্যমেই হোক না-কেন নাটকটি অভিনীত হবে। নাট্যকারের ভাষায় বলি,
‘আমার যতো ক্ষমতা
ওই দূর্বা ঘাসের ভেতর,
কোমল সে রসে শুকিয়েছে ক্ষতগুলো
অবিরত, রাতভর।’
[নাটকটির কিছু অংশ যশোরে ‘স্বগতকণ্ঠ’ মঞ্চস্থ করেছিল। ౼ সম্পাদক]





