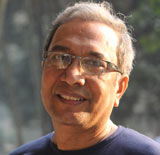সেলিম মোরশেদের ‘কাটা সাপের মুণ্ডু’
তাঁর গল্পগুলো যেন কিম্ভূত আকারের একেকটা পাত্র; ভেতরে চূর্ণীকৃত মানুষ কিন্তু কঠিন, ভাঙা কাচের টুকরোর মতো হিংস্র এবং সুন্দর এবং বহুবর্ণ-বিচ্ছুরক। মানবচরিত্রকে তিনি গল্পে এনেছেন কেটে খণ্ডবিখণ্ড করে। সমগ্র মানুষ নয়, বরং তার সমগ্র জীবনের কয়েকটি উজ্জ্বল বিন্দুকে সামনে এনে বড় করে নির্ণয় করতে চেয়েছেন তার স্বভাব-গতি ও পরিণাম-সম্ভাবনা। এবং এভাবে তিনি যাদের জঙ্গম অবয়ব স্পষ্ট করে তোলেন, তাদের মধ্যে দু’টো প্রবণতা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই: আগ্রাসন আর দ্রোহ। আগ্রাসী অবয়বটি কখনো ব্যাপ্ত ও বিমূর্ত: ব্যক্তি, সমাজ, সভ্যতা কিংবা পরিপার্শ্ব থেকে সে জেগে ওঠে, কিন্তু প্রতিপক্ষে যে বিপর্যস্ত ও কোণঠাসা সে কেবলই ব্যক্তি, সাদামাটা ব্যক্তিমানুষ এবং অধিকাংশ সময় নিঃসঙ্গ। মোরশেদের কাছে ওই নিঃসঙ্গ ব্যক্তিরা মুখ্য, তাদের সসংকোচ কিন্তু গোপন ধারালো পদশব্দে সচকিতে বেজে ওঠে তাঁর গল্পের পরিবেশ। আমরা তাদের প্রত্যক্ষ করি, তাদের অভিমুখ আন্দাজ করি, এবং সবশেষে আশাম্বিত হয়ে উঠি, এই ভেবে যে, অবশেষে তারা অন্তত জানতে পেরেছে দেয়ালটি কতদূর বিস্তৃত এবং দুর্বল অংশটিই-বা কোথায়। সেলিম মোরশেদের সাম্প্রতিক গল্পগ্রন্থ কাটা সাপের মুণ্ডু-র বারোটি গল্প পড়ে আমার এরকম উপলব্ধিই হয়েছে।
সেলিম মোরশেদ আপাদমস্তক ছোট কাগজের লেখক। প্রতিষ্ঠানবিরোধী বলে তাঁর খ্যাতি আছে। কিন্তু উপর্যুক্ত গ্রন্থের গল্পগুলো পড়ে আমার কাছে মনে হয়েছে তাঁর খ্যাতি পাওয়া উচিত ছিল একজন শক্তিশালী গল্পকার হিসেবে, টেকনিক বা শিল্পকৌশলে ইতিবাচক উদ্ভাবনা এবং অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতার কারণে। বাংলা গল্পের দীর্ঘদিনের রোগ—ভাবালুতা এবং খুঁটিনাটি বর্ণনার বিশ্রী প্রবণতাটি—তাঁকে শেষপর্যন্ত আটক রাখতে পারেনি। সম্ভবত এ-জন্য যে, গল্প লেখার সময় খুঁটিনাটি খড়কুটোর ছবি আঁকার চেয়ে মানুষের স্বভাব ও এর পরিণাম নির্ণয়ের দায়িত্বটিই তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। ফলে তাঁর ভাষা সেই সংহতির মধ্যে গতিময়তা অর্জন করে নেয় যা লক্ষ্যভেদী সৃষ্টির জন্য অনিবার্য:
‘আতঙ্কে শরীরে ঘাম ছড়িয়ে যায় পরীর। আর কোনোকিছুই ও দেখতে চায় না। দরোজার গোড়ায় তারের জালের মধ্যে দুর্গা ঘাড় কাত করে ঘুমিয়ে। নিশ্চিন্তে সেরাজও। কেবল ঘুমহীন পরী খাট ছেড়ে দরোজা খুলে বেরিয়ে আসে। বাইরে বাতাস। বড়োজোর কয়েক মিনিট দেরি হতে পারে সকালের রোদ উঠতে।’
(‘বোধিদ্রুম’: কাটা সাপের মুণ্ডু)
তিনি সময়কে জেনেছেন, মানুষের বোধকে জেনেছেন, দেখেছেন বৈরী পরিবেশ রক্তমাংসের মানুষকে কিভাবে পাথরের মতো কঠিন করে তোলে। আমরা তাই কাটা সাপের মুণ্ডু-র ভেতরে ঢুকতে গিয়ে বিক্ষত, ক্রন্দনরত, নিঃসঙ্গ ও জঙ্গম পাথরের স্পর্শ পাই, ঝিকিয়ে-ওঠা ছুরির শানানো ফলার অনিবার্য উপস্থিতি টের পাই। এভাবে এগোতে এগোতে যখন প্রান্তে পৌঁছি তখন বুঝতে পারি সেইসব মানুষকে যারা রাষ্ট্রযন্ত্রের চাপে, অর্থনৈতিক যাঁতাকলে, সামাজিক ফাঁদে আটকে পড়ে আজ বিপর্যস্ত, কোণঠাসা, ছিন্নভিন্ন। কাটা সাপের মুণ্ডু-র হেমাঙ্গিনী, পরী, ইসমাইল, শিলা এরা সেসব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে।
প্রতিষ্ঠানবিরোধী বলে তাঁর খ্যাতি আছে। কিন্তু উপর্যুক্ত গ্রন্থের গল্পগুলো পড়ে আমার কাছে মনে হয়েছে তাঁর খ্যাতি পাওয়া উচিত ছিল একজন শক্তিশালী গল্পকার হিসেবে, টেকনিক বা শিল্পকৌশলে ইতিবাচক উদ্ভাবনা এবং অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতার কারণে।
নামগল্পটিতে আমরা দেখি রাষ্ট্র আর সমাজ থেকে প্রায়-বিতাড়িত হেমাঙ্গিনী ক্ষুধার তাড়নায় কিভাবে একটি সাপের চেয়ে ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে বিষাক্ত সাপটিকে ধরে জ্যান্ত পুড়িয়ে খেলো। কিন্তু এখানেই যদি গল্পটির শেষ হত তাহলে জৈবিক প্রবৃত্তির কারণে জয়ী হেমাঙ্গিনী একটি সাপের চেয়ে যোগ্য প্রাণী হত মাত্র। কিন্তু আমরা এই গল্পের ভেতর থেকে আরেকটি প্রতীকী সত্যের আঁচ পাই। এবং আমরা সম্ভাবনা নিয়ে আশাম্বিত হয়ে উঠি যে কোণঠাসা মানুষ নিশ্চয়ই ভীতির উৎসস্থল সাপগুলোকে কব্জা করে তাদের মাংস খেয়ে স্বাধীন জীবনের শীতলতার ভেতর ঘুমুতে পারবে।
তাঁর প্রায় সবগুলো গল্পই এরকম দ্বিমাত্রিক ব্যঞ্জনায় শেষ হয়েছে। গভীরতার ভেতরেও যেন-বা আরেকটি গভীর গুহা থেকে যায়। সেখানে প্রবেশ করতেই বোধের ভেতর ঝলসে ওঠে জীবনের অন্যসব কোণ ও বাঁক। তাঁর গল্পে অবদমিত মানুষের ভেতরের অংশটিকে দেখা যায়। এজন্য সেলিম মোরশেদের কাছে জরুরি হয়ে উঠেছে আঙ্গিকের বদল ও উদ্ভাবনা। ‘সুব্রত সেনগুপ্ত’ ও ‘চেনা জানা’ সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে বিন্যস্ত। এর স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে মন্তব্য করা অসম্ভব, কিন্তু তাঁর গল্পের বেলায় যে এ কৌশল ইতিবাচক হয়ে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ‘চেনা জানা’ গল্পের একজন বদ্ধ মানুষের সত্তার বিভিন্ন প্রবণতাকে তিনি আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করেছেন; পর পর উঠে এসেছে তার জীবনের সেক্স, ভায়োলেন্স, সোশাল-ড্রামা, পলিটিক্স, কালচার প্রভৃতির পশ্চাৎপট। এবং শেষে আমরা দেখেছি নারী-শরীর অর্থাৎ যৌনতা অর্থাৎ আনন্দের ভেতর যেন আবু হোসেন তার উদভ্রান্ত অবদমিত জীবনের মুক্তি খুঁজে পেতে চাইছে।
মোরশেদের ভাষা তাঁর সম্ভাবনার আরেক ক্ষেত্র। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও বোধ যেমন মনোবিশ্বের নানান অলিগলি, গিরিপথ, গুহা পরিভ্রমণ করে হয়ে উঠেছে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী, তেমনি এই বোধকে ধরার জন্য তাঁর ভাষাও হয়ে উঠেছে অমসৃণ ও ধারালো। রূপকায়তনিক আবহ নিয়ে তাঁর শব্দ ও বাক্যমালাও দ্বি-বিধ আলোর মুখ খুলে দেয়:
‘হেমাঙ্গিনীর প্রার্থনার দশ আঙুল তখন আরশ-এর গায়ে দ্যুতিহীন জলছাপের স্থিতিকাল। নিজের ছায়া আগত প্রবাহের মতো অজ্ঞেয় মনে হলো হঠাৎ। মুহূর্তকালের উগ্র অসহায়ত্ব তাকে গ্রাস করে কোথায় যেন কড়াৎ ছিঁড়ে গেলে টের পেল হেমাঙ্গিনী।’
(নামগল্প: কাটা সাপের মুণ্ডু)
বিন্যাস ও ভাষার এ রকম নতুনত্ব তাঁকে যেমন আলাদা করেছে সমকালীনদের থেকে, তেমনি সূচিত করছে একটি সফলতার সম্ভাবনা। আমরা এ পরিণতি বুঝতে পারব না যতদিন এ দ্বি-বিধ বৈশিষ্ট্য আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে উত্তীর্ণ প্রমাণিত না হয়।
সংবেদ-৬