
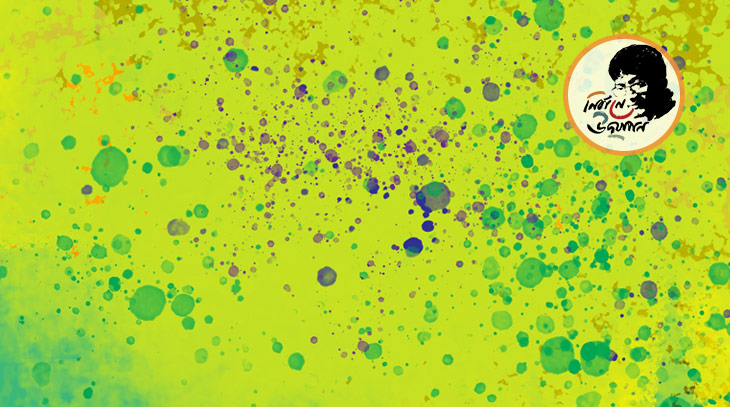
সেলিম মোরশেদের গল্পবিশ্ব
বাংলাদেশের লিটলম্যাগ আন্দোলনের অবিসংবাদিত যোদ্ধা সেলিম মোরশেদের গল্প নিয়ে যে লিখতে বসেছি, অস্বস্তি হচ্ছে। সেই অস্বস্তি থেকে লেখাটা শুরু করতে দেরিও হলো। এই অস্বস্তির কারণ সেলিম মোরশেদ নন। ব্যক্তির মূল্যায়নের যেরূপ ধারা আমাদের অপ্রাপ্তমনস্ক সমাজে প্রচলিত আছে, তার কথা ভেবেই অস্বস্তিটা ক্রমশ বাড়ছিলো। হাজার হোক, আমি নিজেও তো ‘কোন কিছুতে দ্রুত ইনভল্ভড হয়ে যাওয়া’ সমাজেরই একজন। না চাইলেও কোন না কোনভাবে সেই প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া মূল্যায়নই কি শেষমেশ এক্ষেত্রেও অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে না? আবার ‘গঠনমূলক সমালোচনা’ বলতে আমাদের মধ্যবিত্ত মানস যেই ‘সাপ মরলো, লাঠিও ভাঙলো না’ এপ্রোচকে বোঝে বা বোঝাতে চায়, তাতেও সচেতনভাবেই আস্থা রাখতে চাই না। সেলিম মোরশেদের অতি অবশ্যই এই দুই বিপদজনক প্রবণতার মধ্যবর্তী একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন প্রাপ্য। এটা তাকে কেউ দয়া কিংবা করুণা করে দেয়নি, এটা তার নিজস্ব অর্জন।
সেলিম মোরশেদের গল্পের ভক্ত পাঠক হোক কিংবা না হোক, তার সাহিত্যকর্মের সাথে পরিচিত যে কেউই সম্ভবত এই কথা স্বীকারে আপত্তি জানাবেন না যে, তার লেখা সুখপাঠ্য নয়। শুধুমাত্র লেখকের অন্তর্গত দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই নয়, তার ফর্মের কারণেও। তার গল্প ‘চেনা-জানা’ থেকে কিছু অংশ তুলে দেওয়া যাক—
‘কালচার: কৈশোরোত্তীর্ণ একসময়ে তার বন্ধু ছিলো লক্ষমণি। লক্ষমণির বাবা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত আর সংস্কৃতিমনস্ক। সভ্যতার যাবতীয় যোগসূত্র যেনো লক্ষমণি ছিলো। ওর চালচলন পোশাক-আশাক যাবতীয় অনুপুঙ্ক্ষ সে লক্ষ করতো। কখনো-বা ওদের বাসায় গেলে লক্ষমণির মা; লক্ষমণি পড়াশোনায় খুব ব্যস্ত, ওর আব্বা খুব রাগী— এই জাতীয় সংক্ষিপ্ত কথা সচরাচর বলতেন। লক্ষমণির কাছে আবু হোসেন কালচার সম্পর্কিত তথ্য পায়: বিপুল চৌধুরী নামের একজন লোক ছিলো। সে বহু টাকা উপার্জন করলো যৌবনে। বিপুল চৌধুরী চঞ্চল প্রকৃতির। লোকে তাকে বললো, বিপুল, ঘর বানিয়ে স্থির হও। বিপুল বললো যে নদীতে রুই-পুঁটি-কাতলা-বোয়াল-কুমির-কামোট কেউ কাউকে মারে না সেখানে সে ঘর বানাবে। নৌকায় করে জমানো টাকা আর লোকজন নিয়ে বিপুল দেশান্তরি হলো, খুঁজতে খুঁজতে, অবশেষে সুরত নদীতে গিয়ে সে তাই দেখলো। নদীর পাড়ে দশ বছর ধরে বিপুল সিমেন্টের পরিবর্তে ডিম দিয়ে এক বিশাল ঘর তোলে: বিপুল চৌধুরীর মাজারে লক্ষমণি তার আব্বা তার আম্মা আরও কিছু স্বজন বেড়াতে গিয়েছিলো। দেয়ালগুলো পিচ্ছিল! নানারকম মোজাইক! বড়ো বড়ো ঘর। দক্ষিণদিকে হুহু বাতাস-আসা জানলা! ছোট ছোট গাছ! ঘরের ভেতর দেয়ালে সাপ ও বাঘের হাসি হাসি ছবি! লক্ষমণি বললো, ধুর, এ-কেমন বাঘ! তার বাবা গম্ভীরভাবে বললেন, আর্টের বাঘ! আর্ট মানে আরাম: লক্ষমণি ভাবলো! লক্ষমণিরা সারাদিন থাকলো সেখানে।’
আমাদের সাহিত্যের প্রচলিত ন্যারেশন কিংবা নন্দনতত্ত্ব কোট করা অংশটিতে পুরোদস্তুর অনুপস্থিত। ব্যক্তিমানুষের যাপন উৎসারিত বিবিধ সংকটের রূপ এখানে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে; আমাদের ‘চেনা-জানা’ সাহিত্যের ন্যারেশন বা ফর্ম এই আবহকে ধারণ করতে সক্ষম নয়। বলাই বাহুল্য, সেলিম মোরশেদের প্রাতিস্বিক এই ভঙ্গি আর যাই হোক সুখপাঠ্য নয়। তবে সচেতন কোন পাঠক যদি সাহিত্যপাঠে মুগ্ধতার যেই ব্যারিয়ার তা অতিক্রম করতে আগ্রহী হন; লেখালেখি বা সাহিত্যকর্ম লেখকের বা শিল্পীর সৃষ্টিতে পাঠকের মুগ্ধ হবার চাইতেও বৃহৎ কিছু অফার করতে সক্ষম, যে সকল পাঠকের এমন উপলব্ধি হয়েছে— আমি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি যে তারা সেলিম মোরশেদের কমপ্লেক্স ন্যারেশন স্টাইলে লেখকের সময়কার প্রেক্ষিতের উপরে নির্মিত তার দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝতে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। শেষ পর্যন্ত, সাহিত্যকর্মকে যতোভাবেই উল্টেপাল্টে দেখা হোক না কেনো, তার গ্রহণযোগ্যতা কিংবা প্রাসঙ্গিকতা লেখকের যেই দৃষ্টিভঙ্গি, তার বলিষ্ঠতার উপরে নির্ভরশীল।
সেলিম মোরশেদের গল্পে আরো যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য অবলোকন করা যায় তার একটি হলো— মধ্যবিত্ত মানস কিংবা মূল্যবোধের প্রতি তার সচেতন অশ্রদ্ধা। ক্ষেত্রবিশেষে বিবমিষা বললেও বোধকরি ভুল বলা হয় না। এবং তার রূপায়ণের বেলাতে তিনি ক্রোধান্বিত নন। সচেতন, সটান। ফলে মধ্যবিত্ত মানস সম্পর্কে তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে এড়িয়ে যাবার আরামটুকু পাঠকেরা এফোর্ড করতে পারেন না। আমি মনে করি পূর্ববাংলার গদ্যসাহিত্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পরে সেলিম মোরশেদই মধ্যবিত্ত রুচি বা মানসকে সবচেয়ে সবলভাবে আঘাত করতে সক্ষম হয়েছেন। তার ‘অম্লানদের গল্প’, ‘নীল চুলের মেয়েটি যেভাবে তার চোখ দুটি বাঁচিয়েছিলো’— এমনকি আমি মনে করি ‘শিলা, অনন্তে’ গল্পের শেষে শিলার যে পরিণতি সেটাও মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের প্রতি তার যেই অনাস্থা সেটারই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। সেলিম মোরশেদের মধ্যবিত্ত মানসের বা মূল্যবোধের প্রতি যেই দৃষ্টিভঙ্গি, তার সম্পূর্ণটুকু শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিজীবন-শিক্ষাজীবন-কর্মজীবন-সমাজজীবন সর্বোপরি শ্রেণি উত্তরণের জন্য কিলবিল করে এগিয়ে যাবার অবসেশনের প্রতি ইঙ্গিতের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রেম, ভালোবাসা এসকল বিষয়েও মধ্যবিত্ত মানস যেই সঙ্কীর্ণ, দ্বিচারী অবস্থান বজায় রাখতে সচেষ্ট সেই ব্যাপারেও সেলিম মোরশেদের সচেতন দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়। তার ‘কাজলরেখা’ গল্পের কিছু অংশ সম্ভবত তা ব্যাখ্যায় সাহায্য করতে সক্ষম—
‘গাড়ির ইঞ্জিন আরেফিন ওয়ার্কশপে পাল্টাতে গিয়েছিলো দুইদিন: তারা জানিয়েছিলো ইঞ্জিনটা অনেক অক্ষত, মোটর আর সকেটজাম্পার পাল্টালে শব্দের প্রকটতা পাবে সহিষ্ণুতা। ঠিক করে দিলেও আরেফিনের মনে হয়েছিলো, আরেকটা গাড়ি দরকার পড়বে। ব্যক্তিগত ব্যাপারটা আরো ব্যক্তিক হয়ে ওঠে। ওইরাতে কাজলের কাছে হাতব্যাগ চাওয়াও ছিলো এক সরস কৌতুক; তার মাথায় চাড়া দিয়ে উঠেছিলো তা। নানাভাবে এরকমই হয়; ভারতে রমা, কোরিয়ায় সুজানা, এনাবেল-জেনিফা, উত্তরায় লুবনা, সোনিয়া, নীরা—নারী-পুরুষ সম্পর্কিত অনুভবের স্পন্দিত উদ্ভাসে তৈরি হচ্ছে অষ্টম বলয়টি? চল্লিশের কোঠায় ছোঁয়া আরেফিন তার বিদ্যমান একাধিক সংসার জীবনে কখনো আইনগত সম্পর্কের উপরিকাঠামোগুলোকেও লক্ষ করেনি, পিতা বা স্বামীর মর্যাদা ন্যূনতম বহন না করে এসেছে; অত্যুগ্র প্রেমিকসত্তা বারবার তাকে ঠেলে দেয় সবুজে, লক্ষ্য—একাধিক সত্তার ঐক্য। অনেকে বলেছিলো, নির্মল জীবনের কথা—যে জীবন বিভক্তির না, অনুক্ত উত্তেজনায় সামষ্টিক, বিস্তৃত অনুভবের চেয়ে ওয়াদার সত্যতা পরম, প্রেমের চেয়ে মমতার মূল্য বেশি, অনাগ্রহের দায় মেনে মানুষ যেখানে মহৎ হয়। যারা বলেছিলো, আরেফিন জানতো তাদের। তারা জানতো না আরেফিন চেনে।—অবদমনের বর্জ্য চিবিয়ে কষটুকু নিয়ে জাবরকাটা—কৌণিক বিন্দু ছাড়া জীবনে কোথাও সমকোণ নেই; ঐক্যের প্রতিটুকরোকণায় বহুভাবে খণ্ডিত; মায়ার নামে আছে করুণা আর ওয়াদার দায়, মমতার নামে যাপনে ধারালো চাকু। কথিত স্বাভাবিক জীবন।’
কোট করা অংশটুকুর শেষের কিছু লাইন এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যা পড়তে পড়তে আমরা যারা মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ দ্বারা পরিপুষ্ট, তারা অস্বস্তিবোধ করতে বাধ্য। পাঠকের মনে সচেতনভাবে এই অস্বস্তিকে বলিষ্ঠভাবে জাগরূক রাখতে পারা আদপেই কম কিছু নয়।
সেলিম মোরশেদের গল্পের আরেক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো নিম্নবর্গীয় চরিত্রগুলোর বৈচিত্র্যময় উপস্থাপন। তার গল্পের বিভিন্ন অন্ত্যজ চরিত্র বিভিন্নরূপে তার পাঠকদের সামনে এসে উপস্থিত হয়। ‘কাটা সাপের মুণ্ডু’ গল্পের হেমাঙ্গিনী, ‘কান্নাঘর’ এর নিত্যানন্দ, ‘সখিচান’ এর সখিচান, এরা প্রত্যেকেই অন্ত্যজ চরিত্র হলেও যার যার প্রেক্ষিত, যাপন এবং বোধের তারতম্যে বিশিষ্টতায় ভাস্বর।
সেলিম মোরশেদের গল্পের আরেক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো নিম্নবর্গীয় চরিত্রগুলোর বৈচিত্র্যময় উপস্থাপন। তার গল্পের বিভিন্ন অন্ত্যজ চরিত্র বিভিন্নরূপে তার পাঠকদের সামনে এসে উপস্থিত হয়। ‘কাটা সাপের মুণ্ডু’ গল্পের হেমাঙ্গিনী, ‘কান্নাঘর’ এর নিত্যানন্দ, ‘সখিচান’ এর সখিচান, এরা প্রত্যেকেই অন্ত্যজ চরিত্র হলেও যার যার প্রেক্ষিত, যাপন এবং বোধের তারতম্যে বিশিষ্টতায় ভাস্বর। এক্ষেত্রে যা লক্ষণীয় তা হলো তাদেরকে সহানুভূতিপূর্ণ ঝাপসা চোখে, ফলে মোহগ্রস্ত চোখে রূপায়ণের সম্ভাব্য যেই বিপদটা দেখা দিতে পারতো তা দেখা দেয়নি। তার গল্পের অন্ত্যজ চরিত্রগুলো নিজেদের সমগ্রতা নিয়ে গল্পে উপস্থিত থাকে ফলে তাদেরকে তাদের পরিপূর্ণ রূপে আবিষ্কার করার সুযোগ ঘটে। ‘চিতার অবশিষ্টাংশ’ গল্পটির কিছু লাইনের দিকে লক্ষ্য করা যাক—
”দুই-একদিন পরে স্বপন আবার চাকরিতে জয়েন করতে যাবে এরকম একদিন দুপুরবেলা ডাল রান্না নিয়ে স্বপন পুষ্পরেণুকে মারে। সে ভালো খাবার খেতে চাচ্ছিলো। পুষ্পরেণু খুব সাবধানে শরৎ-এর ব্যাপারে এগিয়েছে। কারণ পুষ্পরেণু জানতো স্বামী বাদে অন্য পুরুষের কাছ থেকে টাকা নিলে শুধু স্বামী ছোটো হয় না, ওই পুরুষটার কাছে কীভাবে যেন সমর্পিত হবার একটা ভঙ্গিমা তৈরি হয়। তাই সে শরৎ-এর কাছে কখনও কোনোদিন কিছু চায়নি। কিন্তু না পেরে স্বপনের জন্যে মাছ কেনার দরকার ছিলো বলে শরৎ-এর কাছে সন্ধ্যার সময় কিছু টাকা হাওলাত করে। ওই সময় হঠাৎ করে পুকুরপাড়ে শরৎ-এর বোন মিনু আর শরৎ-এর মেয়ে সুমি এই দুইজন টাকা নেয়াটা দেখে স্বপনের কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলে, ‘বউ দিয়ে ব্যবসা করাস আর ঘুমিয়ে থাকিস ঘরে।’ স্বপন পুষ্পরেণুকে পেটাতে পেটাতে রক্তাক্ত করে। পুষ্পরেণু পরের দিন কোর্ট থেকে স্বপনের উদ্দেশ্যে ডাইভোর্স লেটার পাঠায়। যদিও হিন্দুদের ভেতর তালাক হয় না তবুও দু’পক্ষই এই তালাকটা মেনে নিয়েছে। তবে পুষ্পরেণু সিঁথির সিঁদুরটা মোছেনি। স্বপন এসেছিলো ঘরে। পুষ্পরেণু জানিয়েছে, ‘তুমি আমার প্রেম। কিন্তু আবার সংসার করলে শরৎ-এর প্রসঙ্গটা এসেই যাবে। আমি আমার প্রেমকে নষ্ট হতে দিতে চাইনা।’ শরৎ এসেছিলো একবার, পুষ্পরেণু বলেছে, ‘আপনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র, এমন কিছু বলবেন না, যাতে আমার শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যায়। কারণ স্বপন আমার স্বপ্ন। আমার প্রেমের এবং শ্রদ্ধার—এই দুটো জায়গার কোনটাই আমি নষ্ট করতে চাই না।’ পুষ্পরেণু অদূরবর্তী সুবলের চিংড়ি মাছের কারখানায় প্যাকিং করে মাসে বারো শত টাকা উপার্জন করে। ওভারটাইমও আছে। ইচ্ছা করলে কাজ করে পয়সা বাড়ানো যায়।”
সম্ভবত শুরুর দিকে আনা যেতো এবং তা স্বাভাবিক বলেও গণ্য হতো, তারপরেও সেলিম মোরশেদের গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের একটি শেষের দিকেই উল্লেখ করতে যাচ্ছি। সেটা হলো তার রাজনৈতিক সচেতনতা। শিল্পের জন্য শিল্প বনাম শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতার এই বাইনারীতে আমরা প্রায়শই যার যার ভাবনা থেকে এমন এক অবস্থানে থাকতে প্রেফার করি, যা প্রায়শই খণ্ডিত চিত্র আমাদের সামনে এনে হাজির করে। আর্টে জীবনবহির্ভূত কোনো উপাদানই ব্যবহার করার সুযোগ নেই। আবার আর্টের বিপরীতে যা, সেটাও তো আর্ট। শিল্পসাহিত্যে রাজনৈতিক সচেতনতা মাত্রই পরিত্যাজ্য কিংবা শিল্পসাহিত্যে বাই হুক অর বাই ক্রুক রাজনীতি আনতে হবেই— এমন যে কোনো গোঁড়ামি শিল্পসাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করে না আবার রাজনীতিতেও ভিন্ন কোনো ডাইমেনশন আনতে সহায়তা করে না। আমরা যদি ‘সুব্রত সেনগুপ্ত’ গল্পটি থেকে সেলিম মোরশেদের এই বৈশিষ্ট্যের দিকে মনোযোগ দেই তবে লক্ষ করবো তার গল্পের রাজনৈতিক চরিত্রগুলোর উপস্থিতি শুধুমাত্র রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তাদের অন্তর্গত মানসিক জটিলতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, সাক্ষাৎ দেবতা কিংবা নিখাদ শয়তান এমন কোনো রূপেই উপস্থিত না হওয়া— সবমিলিয়ে চরিত্রগুলোর গতিপ্রকৃতি ও বিবর্তন আমাদের দুঃসহ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে বলিষ্ঠভাবে ইন্ডিকেট করতে সক্ষম। সেলিম মোরশেদের বিভিন্ন গল্পে কোনো চরিত্রের মাধ্যমে তা টুকরা টুকরা অবজারভেশন সম্পর্কে আমরা অবহিত হই এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট রাজনীতির ইতিহাস ও তার বিবর্তনের সাপেক্ষে অবজারভেশনগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। তার ‘বাঘের ঘরে ঘোগ’ গল্পটির কিছু লাইনের দিকে লক্ষ করি—
‘রুমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবেন। নিজেও বিভ্রান্ত, কমিউনিস্ট দলগুলোর বিভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করেন। অবশ্য তাকেও তারা হয়তো নগণ্যভাবেই দেখে। একটা ফিউডাল পিউরিটি থেকে সবাই স্যাক্রিফাইস সেল করা শুরু করেছে। দরকার তো শুধু সায়েন্টিফিক্যাল মরালিটি।’
কিংবা লক্ষ করা যাক তার ‘আদি অপেরা’ গল্পটির কিছু লাইনের দিকে—
”হোসেন ডাক্তার হাঁটতে-হাঁটতে প্রায় টুটুলকে ধরে ফেলেছে। রাস্তায় এখন যানবাহন আর লোকজনের ভিড় কম। টুটুল হোসেন ডাক্তারকে ছেড়ে মুহূর্তে এগিয়ে গেলো।
‘রাজনীতির লোকেরা সংস্কৃতিটা বুঝতে চায় না। বুঝলেন টুটুল ভাই, একসঙ্গে না হাঁটতে পারলে কথা বলবো কিভাবে?’
টুটুল গতি মন্থর করলো। সত্যি তো একটা সমন্বয় দরকার।”
সেলিম মোরশেদের যেসকল গল্পে রাজনীতি কিংবা রাজনৈতিক প্রসঙ্গ সরাসরি এসেছে, আমি মনে করি সেসকল গল্পের মধ্যে ‘বাঘের ঘরে ঘোগ’ গল্পটি পূর্ণতা কিংবা ব্যাপ্তির বিচারে সবচেয়ে পরিণত এবং শক্তিশালী। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে তার অন্য গল্পগুলোর মতো এই গল্পের প্রধান চরিত্রগুলোও ব্যক্তিগত-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের কমপ্লেক্স ডায়ালেকটিক্সে ক্ষতবিক্ষত এবং সামষ্টিক রাজনীতির অংশ হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিমানুষের ভঙ্গুরতা বা নাজুকতায় নাজেহাল; কিন্তু এই গল্পটিতে তাদের সেই জটিল রূপায়ণের সবচাইতে সংহত এবং ইঙ্গিতময়। সাম্প্রদায়িকতা থেকে শুরু করে যৌনতা, মুক্তির লক্ষে সশস্ত্র রাজনীতিকে অবলম্বন করা; মনে রাখাটা বাঞ্ছনীয় যে সেলিম মোরশেদ এমন এক রাজনীতির কথাই এই গল্পে বলতে চেয়েছেন যেই রাজনীতি সঙ্গত কারণেই স্ট্যাবলিশমেন্টের চোখে সবচাইতে ঘৃণ্য এবং দুঃখজনক ভাবে স্ট্যাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে অবস্থান করে যার রাজনৈতিক পর্যালোচনা প্রায়শই রোমান্টিসিজমের গণ্ডি অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়। এই রাজনীতির টোটালিটিকে সাহিত্যে ধারণ করতে চাওয়াটা খোদ দুঃসাহসিক এবং তাতে সফল হওয়াটা বিশেষ কৃতিত্বই বটে এই নিয়ে সংশয় পোষণ করি না। সেলিম মোরশেদের ‘বাঘের ঘরে ঘোগ’ গল্পটি সম্ভবত তার সাহিত্যদর্শনের সবচেয়ে সংহত প্রতিফলন, ‘কনশাস এফোর্ট’-এর।
সবশেষে এতোটুকু বলতে চাই যে, সেলিম মোরশেদের গল্প নিয়ে আমার এই আলোচনা যে কোন বিচারেই সম্ভবত অসম্পূর্ণ। এবং আমি একেবারেই ক্ষুব্ধ কিংবা অসন্তুষ্ট হবো না যদি পাঠকেরা এই লেখাটিকে কাঁচা কিংবা সারবস্তুহীন হিসাবে বিবেচনা করেন। তারপরেও সাহস করে এবং পরিশ্রমের সাথে লিখতে চেষ্টা করেছি কেবল একটি কারণে। সেটা হলো, পাঠক হিসাবে সেলিম মোরশেদের কাছে এই বার্তাটুকু পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছি যে— তার গল্পে কিংবা শিল্পে আমি মুগ্ধ হওয়া কিংবা ঘোরগ্রস্ত হওয়াটাকে শিল্পী হিসাবে তার প্রতি আমার মনোযোগের বা শ্রদ্ধার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে আমি মনে করতে চাইনি, চাইও না। আমি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি যে লেখক-পাঠকের মধ্যকার সম্পর্কটুকু একতরফা মুগ্ধতা কিংবা বিহ্বলতার চাইতেও অনেক বেশি কিছু। বরং তা পারস্পরিক আদানপ্রদানের। পাঠকেরও দায় থাকে, পাঠকেরও প্রস্তুত হতে হয় এবং সর্বোপরি পাঠকেরও ‘কনশাস এফোর্ট’-এর প্রয়োজন পড়ে। সেলিম মোরশেদের সাহিত্যের সাথে পাঠক হিসাবে আমি সেই সম্পর্কটুকুই স্থাপন করতে চেষ্টা করেছি। সুবিমল মিশ্রের ‘প্রেমের মড়া জলে ডোবেনা’ উপন্যাসের প্রাক্-কথনে সেলিম মোরশেদ লিখেছিলেন, ‘তিনি এমনই একজন লেখক, যে ডালে নিজে বসেন সে ডালেই প্রথম কোপটি তিনি দেন।’ মাঝেমধ্যে ভাবি, এই এসেন্স বিবেচ্য হলে তিনি নিজেও সুবিমল মিশ্রের অনুসারী কিনা!
লেখকের ঋণস্বীকার:
- লিটল ম্যাগাজিন এটিচিউড— সাগর নীল খান দীপ (ভরাট হচ্ছে অনবস্থার আঁধার)
- সেলিম মোরশেদের আখ্যানবিশ্ব: সরলচোখে তাকানোর প্রস্তাব— মাসুমুল আলম (২২ পয়েন্ট বোল্ড ও অন্যান্য)





