
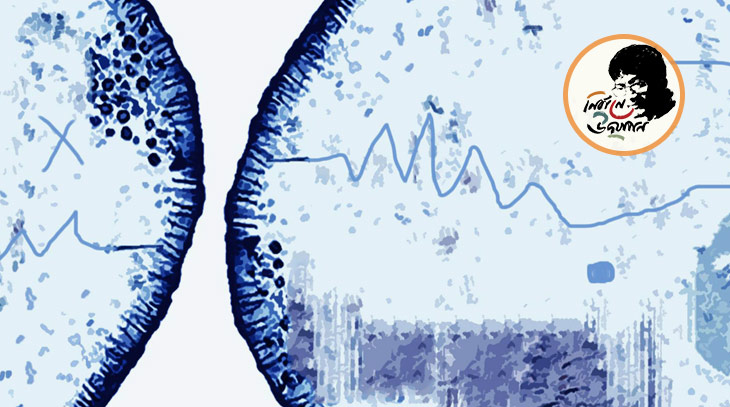
সেলিম মোরশেদের দিকে ফেরা, তাঁর গল্পের দিকে ফেরা
পনেরো বছর আগের এক শীতকাল। ইঙ্গমার্কিন বিরোধিতার বঙ্গীয় বামপন্থি আমেজ সবে থিতিয়ে এসেছে। চেরাগী পাহাড় মোড়ে হবু কবি, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রনেতারা তখনো খেটে খাওয়া আঞ্চলিক সাংবাদিক কিংবা এমএলএম কোম্পানির অলীক স্বপ্নে বুঁদ হয়নি, তখনো তাঁদের হাতে সস্তার ল্যাপটপের বদলে বইপত্র থাকতো, কারো কারো ঝোলা থেকে কবিতাবই বেরিয়ে পড়তো হামেশাই কিংবা পুঁজিমনস্ক নাগরিকদের অবাক করে দিয়ে মাও এর রেডবুক। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল তখনো সাম্যের স্বপ্নে অটুট, শিক্ষাশিবিরগুলোতে জনৈক শিবদাস ঘোষ একচেটিয়া রাজত্ব করছেন। অল্প বয়সের শরীরে অসুখ বিসুখ হতো না বললেই চলে এবং আগের বছরের অক্টোবরে হার্ভার্ডের তরুণ ফেসবুক প্রতিষ্ঠা করলেও বাংলাদেশে এক বছরের মাথায় তার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়নি অতএব আমাদের একাগ্রতা ঐতিহাসিক। এমন এক মনোরম সময়ে, আমার চব্বিশতম শীতে, এক বিকেলে, পার্টি কমরেড নিজাম ভাইয়ের বাসায় যাওয়ার আমন্ত্রণ পাই, কারণ এতোদিন পর মনে নেই। তখন তাঁর সাথে সদ্য পরিচয়, পার্টির সংকীর্ণ পড়াশোনার গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি দূরগামী— প্রথম আলাপেই মনে হয়েছিলো। আমি শুধু শরৎচন্দ্র আর বেগম রোকেয়ায় তৃপ্ত হচ্ছিলাম না, তিনি নানারকম বই, সিনেমার সাথে পরিচয় ঘটাচ্ছিলেন। সেদিন বিকেলে কথায় কথায় তিনি ‘গাণ্ডীব’ বলে একটি পত্রিকা হাতে তুলে দিলেন এবং বললেন, এখন-ই চার পৃষ্ঠার চেয়ে আয়তনে কম একটি গল্প তাঁর সামনে বসে পড়তে— গল্পটির নাম ‘রাতে অপরাজিতা গাছে ফুল’, লেখক— সেলিম মোরশেদ।
নিজাম ভাই ছিলেন গুরু আর ঈশ্বরের মাঝামাঝি কিছু একটা। ফলে আমি পড়লাম। বসার ঘরের জানালার পাশে সন্ধ্যা কখন নামলো টের পেলাম না। তাঁকে ফিরিয়ে দেবো বলে পত্রিকাটি ধার নিয়ে এলাম— আর আজ পনের বছর পর দেখি, আমার কাছে রয়ে গিয়েছে পত্রিকাটি আর ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে তিনি পৃথিবীতে নেই। এখন, পরিণত বয়সে ভাবি কেন সে সন্ধ্যায় গল্পটি অভিভূত করেছিলো— লেখকের অন্য গল্পগুলোর তুলনায় এই গল্পটি সরলরৈখিক। বিবাহিত একজন যুবক পিন্টু, স্বপ্ন দেখে জীবনে মিরাকল ঘটবে। শুরুটা আমরা আরেকবার দেখতে পারি— ‘সে অতিদূর প্রশস্ত পথ ধরে আবারও অবিরত হাঁটে। সিন্ধুর জলে পায়ে-পা রেখে হিন্দুকুশ গিরিমালা থেকে একদা চলতে চলতে সনাক্ত করে দুর্বৃত্তদের; বিরামহীন এই সতত কার্যক্রমে জেনে যায়, তার পূর্বসূরীরা জাদুর বাক্সে সযত্নে রেখেছিলো দ্রোহের নীল; পতনে লাল উলের বলের মতো যা গড়িয়ে গড়িয়ে খুলতে থাকে।’ এসব পিন্টু চরিত্রটি ভাবছে, পনের বছর আগে ইতিহাসের স্নাতকোত্তর যুবক এখনো স্বস্তিতে চলবার মতন ব্যবস্থা করতে পারেনি— অতএব তাকে বিদ্যুৎ বিল কমাবার জন্য মিটারে কারসাজি করতে দেখা যায়—দু’টো ঘর ভাড়া দেয়ার ব্যাপারটি গোপন করতে সংশ্লিষ্ট লোকজনকে উৎকোচ দিতে দেখা যায়। শহীদুল আলম পিন্টু এইভাবে, নিত্যদিন স্ত্রী মিনার ভৎসনা সয়ে যাচ্ছে, নদীর পাড়ে গাঁজা টেনে যাচ্ছে, মূল্যবোধ কিংবা কোনো আদর্শ নেই তার। ‘নদীর মাছ আর নারীর মন এতোই বিচিত্র যে বিস্মিত হতে হয়।’ কিংবা ‘চুরি সভ্যতার প্রথম প্রতিবাদ।’— এসব চিন্তা যে তার মাথায় আসে তাতেই বোঝা যায় দরিদ্র ও অলীকের জন্য প্রতীক্ষা ভারাতুর যুবকের চিন্তার গভীরতা কম নয়। হাত দেখাতে গেলে জ্যোতিষী শনির খারাপ ক্ষেত্রের কথা বলে, বলে ইন্দ্রনীলা পাথর ধারণ করতে অথবা ঘরে নীল অপরাজিতা গাছ লাগিয়ে নিয়মিত জল দিলে শনির দশা থাকবে না বলে জানায়। ইন্দ্রনীলার মূল্য চৌদ্দ হাজার টাকা, একত্রে এতো টাকা পিন্টু কখনো চোখে দেখেনি। হাতে রইলো অপরাজিতা গাছ। মনে আছে, ভাগ্যের সাথে নিয়মিত ধাক্কা খেতে থাকা যুবকের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম এবং গল্পের একেবারে শেষে গাঁজার স্টিকে শেষ টান দিয়ে লম্বা পা ফেলে পিন্টুকে বাড়ির দিকে হাঁটতে দেখে স্বস্তি পেয়েছিলাম সেই ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যায় কেননা— ‘অপরাজিতা গাছে ফুল ফুটছে।’ একটি শৈল্পিক ইঙ্গিত, পিন্টু আর মিনার যৌথ ভাগ্য হয়তো পাল্টাতে শুরু করবে এবার।
দিন যেতে থাকে। ২০০৫ সালের ‘গাণ্ডীব’ পত্রিকার সংখ্যাটি হাতে আসার পরের শীতে, ২০০৬ সালের নভেম্বর ডিসেম্বরের দিকে ‘কথা’ পত্রিকার সম্পাদক আমাকে তৎকালীন ‘বিশদ বাংলা’-য় বইয়ের ঘরে আবিষ্কার করেন, দিলেন এক রিভিউয়ের দায়িত্ব প্রথম পরিচয়েই। পরে, গভীর বন্ধুত্বের এক সম্পর্ক হয়েছিলো আমাদের, শেষবেলার কিঞ্চিৎ মতবিরোধ বাদ দিলে (বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে ‘দেশলাই’ পত্রিকার কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর সংখ্যায়, আগ্রহীদের জন্য বলা থাকলো)—এখন, ২০০৬ সালের ‘কথা’ পত্রিকার সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার উৎকীর্ণ তারিখে দেখা যাচ্ছে, সম্পাদকের সাথে পরিচয়ের কিঞ্চিৎ আগেই ‘খড়িমাটি’ সম্পাদক মনিরুল মনির আমাকে সেই বছরের ত্রিশে মে উপহার দেন। সেখানেই আরেকবার দেখা পেলাম সেলিম মোরশেদের, এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, চব্বিশ পৃষ্ঠার— নিয়েছেন ‘কথা’ সম্পাদক। পড়বার সময় কয়েকদিন স্তব্ধ হয়েছিলাম। মনে হয়েছিলো ধর্মবিশ্বাস এবং মার্ক্সবাদের মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে তিনি কোথাও গুলিয়ে ফেলছেন। বিশেষ একটি দীর্ঘ অংশ, আসুন সবাই মিলে পড়া যাক—
‘কথা হচ্ছে, আপনি যৌনতার ফিলিংস এর কথা বলছেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত মতামত, চিতার অবশিষ্টাংশ-এ তাই বললেন কিন্তু, মানে যৌনতার ভিতর দিয়ে তার অনুভূতিটা বোধের ভিতর আনবে, সেখানেই আছে সৃষ্টিশীলতা, আছে ঈশ্বরত্ব, তার মানে আপনি যৌনতাকে কিন্তু অনেক ঊর্ধ্বে নিয়ে গেলেন। আমি আবারও তাই বলতে চাচ্ছি, যেখানে ব্যক্তির রুচি, ওই রুচির নান্দনিকতাকে এত চমৎকার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন, আবার আপনিই ধর্মের মৌলিকতায় আস্থা রাখছেন! (কা জা)
হ্যাঁ, সেটা একটা ব্যাপার, আমি যা বলছি তা যে একেবারে আক্ষরিক অর্থেই সবকিছু ফলপ্রসূ করতে হবে, ব্যাপারটা তাও না। তবে নিজস্ব সিদ্ধান্তে যৌনতায় কোনো পাপ দেখি না। কথা হচ্ছে সমাজই তো ঈশ্বর, সমাজ যখন ঈশ্বরের রূপ নেয়, তখন কিন্তু এর আলাদা বিষয় থাকে। সমাজ এটা না মানলে তো এখানে করণীয় কিছুই নেই। এটা স্ববিরোধি মনে হতে পারে, তবে আমি নিজেই হয়ত একটা সমন্বয় করতে চাচ্ছি। মানুষের একদিকের কিছু ভ্যালুজ, জীবনাল্লেখ্য, এবং তার অনেক সত্য— আমার মনে হয় ধর্ম সেটা দিতে পেরেছে। আর এখন যা বলছি, তা হচ্ছে শিল্প। শিল্পই আমাকে ফিলিংস অফ ফ্রিডম দিচ্ছে। ফ্রিডমের জায়গাটা কিন্তু সেইভাবেই চলবে, এই যে আমি কথা বলছি, তা কিন্তু কোনো ইজম মাথায় রেখে বলছি না। এটা হচ্ছে যৌনতার নন্দনতত্ত্বের একটা ফিলিংস। সমন্বয়ের একটা চেষ্টা থাকতে পারে, সমন্বয়টা না-ও হতে পারে। (সে মো)
এবার আমরা সমকালীন সামাজিক- রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছু কথা বলি। জাতীয় পর্যায়ে বর্তমানে আমরা প্রায় সর্বদাই বোমাবাজি, ধর্মসন্ত্রাস, ধর্মীয় জঙ্গিত্বের আত্মপ্রকাশের ফলে সৃষ্ট মানসিক পীড়নের মুখোমুখী হচ্ছি, যা আমাদের শুভবোধকে রীতিমত তছনছ করে দিচ্ছে। সন্ত্রাসের এসব কার্যকারিতার এ ধরন দেখে মনে হতে পারে যে এটি সমগ্র জাতির জন্য, জাতির নৃতাত্ত্বিক প্রবহমানতার জন্য এক ভয়াবহ বিষয়। আপনি একজন প্রথাবিরোধী মানুষ, সেই হিসাবে এ-ব্যাপারে আপনার মূল্যায়নটা কি? (কা জা)
এ- ব্যাপারে আমার মূল্যায়ন হচ্ছে, এটি মোটেই সঠিক কাজ নয়। ধর্মের সঠিক প্রয়োগও নয়। ইসলামের কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে না। ইসলাম তার কাজটি সঠিকভাবে করতে পারলে এমন হওয়ার কথা নয়। ধর্মকে সঠিকভাবে কাজ করতে দিলে এসব হতে পারে না। (সে মো)
তাই! আপনি যা বলছেন তা কিন্তু একজন প্রতিষ্ঠানবিরোধী মানুষের কথা বলে মেনে নেয়া মুশকিল। ধর্মীয় সংগঠনের প্রতি আস্থাশীল মানুষজনও কিন্তু তাই বলে থাকেন। মনে হচ্ছে, জামায়াতে ইসলামী বা অন্য ধর্মভিত্তিক সংগঠন যেভাবে কথাগুলি বলে আপনিও সেভাবেই বলছেন। এই একবিংশ শতাব্দিতে ধর্মআশ্রয়ী প্রথার ভিতর এত পজেটিভ বিষয় কী করে দেখেন? (কা জা)
(হাসতে হাসতে) জামায়াতে ইসলামী যেভাবে কথাগুলো বলে, আমিও সেভাবে বলছি, ব্যাপারটা কিন্তু তা না। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, জামায়াতে ইসলাম ধর্মের কথা বলে ১৯৭১ সালে বা এখনও দৃশ্যত যা বলে, তা কিন্তু তারা করছে না। যাই হোক, আমি বলতে চাচ্ছি, চেতনার স্বচ্ছতা তা ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম থেকে আসতে পারে। ধর্ম নিয়ে টারানটিজম বা ধর্মের নামে চালাতে থাকা উন্মাদনা ইত্যাদি থেকে বাঁচাতে পারে কেবল ওই জনসমষ্টি থেকে বেরিয়ে আসা আরেকটা ধর্ম। সেই ক্ষেত্রে প্রগতিশীলরা ধর্মের ব্যবহার সেভাবে করতে পারেনি বলেই আমার বিশ্বাস। (সে মো)
যাই হোক, সেটা তো আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, যে-কোনো ধর্মের ইতিহাসটার দিকে তাকান, দেখবেন, দুনিয়ার সব সভ্যতা মনে হবে ওই ধর্মগ্রন্থটি থেকেই শুরু হলো। তার আগের সমস্ত সভ্যতা, আচার- নিষ্ঠা, বিজ্ঞান, দর্শন, মিথোলজি, এমনকি মানব-সৃষ্ট ভাবনাকে অস্বীকার করা হয়। এটি সব ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রযোজ্য, কারণ সেখানে অন্য সবকিছুকে সরিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার একটা ব্যাপার থাকে। অন্যকে সরিয়ে নিজের জায়গা দখল, পুনঃদখলের ব্যাপার কিন্তু কোনো ধর্মই কোনোদিন বাদ দেয় না। সাম্প্রদায়িকতার বীজটিও ওইখানেই। এতে কিন্তু মানুষের সমন্বিত কালচার বা ইতিহাসকেও বাই-পাস করা হয়। সেখানে মানুষের নান্দনিক – জাগতিক জীবনকে কুণ্ঠিত করতে করতে আপনাকে ঠেলে দিবে দোজখ না-হয় বেহেশতের দিকে। আপনার কাছে বার বার এই বিষয়টা এই জন্যই উত্থাপন করছি যে, আমার ধারণায় আপনি একজন প্রতিষ্ঠানবিরোধী মানুষ, সমস্ত মূল্যবোধকে ভাঙার ঘোষণা দিচ্ছেন, সেই হিসাবে আপনার কাছ থেকে হয়ত একধরনের ফিলজপিক্যাল কমেন্টস পাবো। (কা জা)
এ আলোচনাটা কিন্তু সাধারণ জায়গা থেকে হচ্ছে, আমার কাছে যা মনে হয়, ইহুদি—খ্রিস্টান বা অন্যধর্মের কথা বলেন, সেখানে কিন্তু তাদের সংস্কৃতি বা বাণীটাই মুখ্য। গৌতম বুদ্ধের বিষয়-আশয়কে মনে হবে একটা দর্শন, সেখানে একধরনের কালচার আছে। কিন্তু, আপনি খেয়াল করে দেখবেন, ইসলামের একটা সুনির্দিষ্ট আইন আছে, সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রকাঠামো আছে, সুনির্দিষ্ট ধর্মনীতি আছে, সুনির্দিষ্ট রাজনীতি আছে; এমনকি প্রত্যেকটা ব্যবহারিক বিষয়েই ছোটখাটো কিছু কথা আছে। যার ফলে মানবধর্মের ভিতর ধর্ম বলতে যে জিনিসটা বোঝা যায়, আপনি সেই বিষয়গুলো মানেন বা না-মানেন, বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের সেইসব জিনিসের আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে কি না প্রশ্নটি সেই দিক থেকে আসতেই পারে। ইসলাম একটা সুনির্দিষ্ট ধর্ম বলেই এরা মনে করে সভ্যতা এবং মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকাটাই অনবদ্য। এই সময়ের প্রেক্ষাপটে মানুষকে প্রলোভন দেখানোর নামে এখন যে বিষয়গুলো উঠে আসছে তা কিন্তু ইসলাম নয়। এখন ইসলামকে তিনজনে তিনদিক থেকে দেখছে, কোরান শরীফে যে রূপক এবং প্রতীকের ব্যাপার আছে তাতো অস্বীকার করা যাচ্ছে না। আমরা আসলে সবসময় ইসলামকে প্রয়োগবাদীদের আঙ্গিক থেকে বিচার করি। আমি যদি ইসলামের মৌলিক জায়গা থেকে দেখি তাহলে দেখব ইসলামের অনেক ব্যাপার আছে সেগুলি গ্রহণ না করার কোনো কারণ নেই। (সে মো)
ঠিক আছে, এখন তাহলে এসবের সূত্র ধরে আপনার গ্রন্থ ‘পাল্টা কথার সূত্রমুখ কিংবা বুনো শুয়োরের গোঁ’ নিয়েই কথা বলি। শুরুতেই বলতে হয়, বইটিতে কিন্তু ছোটকাগজ নিয়ে প্রচুর ইনফরমেশন, দরকারি মতামত, পরিকল্পনা আছে। যাই হোক, আপনি সেখানে প্রগতিশীলতার কথা বলেছেন, ক্লাশ-স্ট্রাগলের কথা বলেছেন, এমনকি মার্কসিজমের পজেটিভ ব্যাপারগুলোই সাপোর্ট করে গেছেন। আবার এখন দেখা যাচ্ছে, ইসলামের একেবারে মৌলস্বরকে পজেটিভ বলছেন। আচ্ছা, বলুন তো, আপনি আসলে কোনটা বলতে চান! (কা জা)
আপনাকে একটা বিষয় খেয়াল করতে বলব, আসলে এখন আমাদের ফাইটটা কাদের সাথে? সারাবিশ্বে কমিউনিস্ট- মুভমেন্ট হোক, সেটা আমি বলেছি, কিন্তু কথা হচ্ছে, এখন আমাদের ফাইটটা কোথায়? সেটা হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধেই তো আমাদের ফাইট? লাল পতাকার পরে সবুজ পতাকাকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভয় পায়। এখন আমার কথা হচ্ছে, সবুজ পতাকাকে যদি সুসংহত করা যায়, তাহলে সেটা কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জন্য একটা বি-শা-ল চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। রণনীতি আর রণকৌশলের ব্যাপারেই তো আছে, আপনি যদি মনে করেন, সোসাইটির ভিতরের কোনো একটা আদর্শের ভিতর দিয়ে এক হয়ে ফাইট করা যায় তাহলে সেটাই হবে সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়। এখন এটাই ওদের জিজ্ঞাস্য যে, সবুজ পতাকা আর লাল পতাকা এক হচ্ছে কি না। গণতন্ত্র তো সেই অর্থে কোনো দর্শন নয়, মানুষের চলাচলের একটা বিষয় মাত্র, মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধের একটা উৎকর্ষ পন্থা হতে পারে। সমাজতন্ত্র, ধর্ম বা অন্যান্য সমাজবাদ বলি, এইগুলির ভিতর দেখা গেছে আজকে কোনো ঐক্য নেই, ফলে ইসলাম বা ধর্মের নামে যদি ঐক্য হয়, এবং তা যদি আমরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, অল্পসময়ের জন্য হলেও মার্কসইজমের সাথে রিলিজিয়নের একটা ঐক্য কিন্তু তৈরি করা যায়। (সে মো)
কিন্তু এত সরলভাবে সবকিছুর হিসাব করাটা সঠিক হচ্ছে? ধর্মের সাথে সাম্রাজ্যবাদের একটা খাতির-প্রণয় তো আছেই, এবং তা থাকবেই। কোনো না কোনো ধর্ম তো ওই সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধবেই। ধর্ম একটা পর্যায়ে তাদের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবেই। (কা জা)
এটা সত্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড এক নয়, আবার তারা যেভাবে পুঁজি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাতে মুসলিম ওয়ার্ল্ড দ্বারা সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করার কোনো অবকাশই আর দেখা যাচ্ছে না। তবে একধরনের সমন্বয় থাকলে তা হয়ত হতে পারত। আমি এভাবে ভাবি আর কি। বিরোধটা কার সাথে করব এটা যদি ক্লিয়ার থাকে, তাহলে বিরোধিতা কিভাবে করব সেটা তখন আর ফ্যাক্টর হয় না। (সে মো)
আপনার কথা থেকেই তো বোঝা যাচ্ছে, লগ্নি-পুঁজিই মুসলিম-বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তাহলে সেখানে বিরোধটা হয় কী করে? (কা জা)
হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে আমি মনে করি, রিলিজিয়নের এমন কিছু আদর্শ আছে যা নিয়ে কিছু হতে পারে, সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, ইসলাম এন্টিক্যাপিটাল। এরচেয়ে বড়ো কোনো এন্টিক্যাপিটাল শক্তি পৃথিবীতে নেই। নিজে খেলেও পাশের প্রতিবেশিকে তুমি খাওয়াও, এটা আর কোথাও নেই। (সে মো)
সেইভাবে বললে, অন্যধর্মেও অনেককিছু আছে, খ্রিষ্টধর্মে আছে খ্রিষ্টীয় সমাজবাদ, বৌদ্ধধর্মে আছে বিজ্ঞানমনস্কতার মানবিক উপাদান, সনাতন ধর্মে আছে শ্রুতি-স্মৃতি-মিথের সমন্বয়ে ঐশ্বরিক বিধান, আছে নান্দনিক আচার- নিষ্ঠা। আর সেমেটিক গ্রন্থের ধারাবাহিকতা তো ইসলামে আছেই। ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রোজা-নামাজ, এসব কিন্তু অন্যসব সেমেটিক ধর্মে অন্যভাবে আছে। তাহলে বিভিন্ন মতাদর্শে পরিপূর্ণ এই জনপদে একটা ধর্মকেই কেবল আলাদাভাবে কী করে দেখবেন! (কা জা)
আলাদা করে দেখব এজন্য যে, ইসলামে সবকিছু রিফাইন্ড ফর্মে আছে। (সে মো)
আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য যেভাবে এখানকার আবহাওয়া, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, এমনকি আমাদের জীবনভঙ্গির সাথে মিশে আছে তা কিন্তু কোনো সেমেটিক ধর্মের ট্রাডিশনাল ফর্মের সাথে মিলছে না, মনে হয় এসব অনেকটাই চাপিয়ে দেয়া ব্যাপার। এখানে যেটা গড়ে উঠছে… (কা জা)
আমি সেইভাবে বলতে চাইছি না, আমি বলতে চাইছি মানুষের স্বজ্ঞার ফল, প্রজ্ঞার ফল, এইসবের একটা বিষয় আমি ধরতে চাইছি। আপনি খেয়াল করলে দেখবেন, বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে সেন্সগুলো কিন্তু বিলুপ্ত হওয়ার পথে। আমি তাই বলতে চাইছি, বিষয়গুলো আমি সেইসব ইনটুইশন থেকেই দেখি আরকি। ইন্টেলেকচুয়াল দিক থেকে বিষয়গুলো দেখতে চাই না এইকারণে যে, আমি মনে করি মানুষের এখনকার যে জ্ঞান, ধারণা, সেই ধারণা বা জ্ঞান একটা বিশেষ অবস্থান থেকেই শুধু আমরা দেখি, তার খুব বড়ো একটা ব্যাপ্তি আমি দেখি না। যতই আবিষ্কার হোক, যতই মানুষ ছুটুক, ব্যাপ্তির সেই জায়গাটা কিন্তু নেই। আবার আমার এও মনে হয়, সভ্যতার এই প্রথার ভিতর আমি পড়ে গেলাম কিনা? আমি প্রথাবিরোধী, তার মানে এই নয় যে অতীতের সমস্ত কাজকে আমি ভেঙে ফেলতে চাইছি, প্রাচীন যা কিছু দেখছি, তাকেই আমি উপড়িয়ে ফেলছি! আমি প্রথাবিরোধী, কিন্তু প্রগতির, সভ্যতার, বা দর্শনের যে প্রথা কয়েক শ বছর ধরে তৈরি হয়েছে, সেই প্রথারও তো আমি বিরোধী। এসব মিলিয়ে আমার মনে হয় যে, শাশ্বত বিষয়ের সাথে সাম্প্রতিক বিষয়ের একটা মূল্যায়ন হওয়া দরকার। যার জন্যই একটা ধর্মকে এ-কে-বা-রে উড়িয়ে দেয়া বা নাকচ করার পক্ষে আমি নই। (সে মো)’
সাক্ষাৎকারটিতে বিজ্ঞানের অগ্রগামীতার ফলে মানুষের অনুভূতি হারিয়ে ফেলার যে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ তিনি তুলেছিলেন, ইন্টেলেকচুয়ালিটি নয় ইনটুইশন বা ইনার সেন্সের দিকেই যেতে চাইছিলেন সেলিম মোরশেদ, মাত্র পঁচিশের যুবক সেটি বুঝতে পারেনি বরং মার্কসবাদী রাজনীতির প্রকোপে উপরিকাঠামোর কথাটুকুকে নিজের মতো বুঝে নিয়ে সেলিম মোরশেদের উপর রাগ করেছিলো, মনে মনে গোঁড়া মোল্লা বলে গালাগালও করেছিলো, তখন তো ফেসবুক ছিলো না আমার, থাকলে হয়ত একটা পোস্টও দিয়ে বসতাম। তাঁর লেখাপত্র পাঠ, একটি গল্প ও একটি সাক্ষাৎকারেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো।
বাসদবিপ্লবের সূর্য আস্তে আস্তে রং হারালেও নিজাম ভাইয়ের সাথে বন্ধুত্ব আরো জমে উঠেছিলো। ততোদিনে বয়স আরো বেড়েছে— তিনি তিন তলা থেকে ছাদের ঘরে চলে এসেছেন, চারদিকে বিশাল কাচের জানালা, খুলে দিলেই অনন্ত বাতাস আর সাদা শেলফে অসংখ্য বই— অনেক সময় বিকেল বেলা তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। আমি তাঁর কোনো এক বই নিয়ে পড়তে থাকি। এভাবেই একদিন এক ছোটোকাগজে তারেক মাসুদকৃত ‘সুব্রত সেনগুপ্ত’ চিত্রনাট্য পাঠ। সেলিম মোরশেদ আবার ফিরলেন তারেক মাসুদের হাত ধরে। এবার খুঁজে পেতে তাঁর গল্পগুলো পড়তে থাকি, পূর্বধারণা আস্তে আস্তে ভাঙতে থাকে।
‘ভয়ঙ্কর সাহসী হলেই খেতে পাওয়া যায়।’—এই বাক্যটি বিশ্বায়নের মহানাগরিক লেখক-ই লিখতে পারেন কারণ ক্ষুধার মানচিত্রের দাগ, খতিয়ান একমাত্র তাঁর পক্ষেই ঠিকঠাক উপলব্ধি সম্ভব।
এসব করোনাহীন পৃথিবীর গল্প। উহানে প্রাণ সংহারী ভাইরাস আবিষ্কৃত হওয়ার পরেও আমরা বেশ নেচেকুঁদেই ছিলাম, কোনো সতর্কতা নেয়া হয়নি আমাদের দেশে কেননা পরবর্তী মাসগুলোতে আস্তে আস্তে পৃথিবীর লোকজন এই দেশের বেহাল স্বাস্থ্যব্যবস্থার কথা জেনে যাবে, এটি নিয়তিনির্ধারিত। এইরকম সময়ে ‘মেঘচিল’ থেকে আমন্ত্রণ পেলাম সেলিম মোরশেদ ক্রোড়পত্রে লেখার, ততোদিনে বাঙালির ঘরে ঘরে স্টে এট হোম, কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলেশন শব্দগুলো জনপ্রিয় হয়েছে, মানুষ মানুষকে স্পর্শ করতে ভয় পাচ্ছে, মৃত্যুর সংখ্যা আস্তে আস্তে ভীতি জাগাচ্ছে, তখন আমি মেঘচিলের বিজনদাকে জানালাম, কোনো বইপত্র হাতে নেই, উলুখড়ের শ্রেষ্ঠ গল্প এক অতিপ্রিয় অনুজকে উপহার দিয়েছি, এই পরিস্থিতিতে তার কাছে যাওয়ার উপায় নেই। শ্রেষ্ঠগল্পের জেরক্স পাঠানো হলো আমাকে, ফলে সুযোগ ঘটলো দশ ফর্মায় বারোটি গল্প আরেকবার চেখে দেখবার, নিবিড়ভাবে ও ধীরে।
‘কাটা সাপের মুণ্ডু’ তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গল্প, উপরোক্ত সাক্ষাৎকারে জানতে পারি ওটা লেখকের অল্প বয়সের রচনা। এবং মিথ্যে না বলতে কি, আরেক অল্পবয়সী লেখক রচিত ‘অতসী মামী’ গল্প থেকে কোনো অংশে কম মনে হলো না। হেমাঙ্গিনীর মায়ের জরায়ু ঝুলে পড়েছিলো ‘তামাম দুনিয়ার মতো’, গোপনে শরীর বেচতো সে-ই মা, তার-ই সন্তান এখন ভিখিরি। বাম পায়ের সব আঙুল তার মায়ের পেটে থাকতেই গলে গিয়েছে। খুপরি ঘরে ‘…আলো নেই, অন্ধকার প্রকট, বিড়ির আগুনে রাতের অন্ধকার গোমেদ-কালচে হিম’—ক্ষুধার তীব্রতা আতংককে আচ্ছন্ন করে আর সে প্রতিবেশে দু’টো মশা উড়ন্ত দশায় সঙ্গমে বিভোর। একদম ছেলেবেলায় হেমাঙ্গিনীর বাপ গোটা তিনেক কমলালেবু কিনে দিয়েছিলো, ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটি বিষাক্ত সাপের দিকে মনোযোগী দশায় তার মনে পড়ে সে স্মৃতি, বাবার ও তিনটি কমলার। ‘হেমাঙ্গিনী ক্ষিপ্রকারী মুহূর্তে মরিয়া হয়ে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনীর মূল সহায়তায়, ছোবলে, এক ঝটকায় গোলপাতা থেকে সাপটাকে টেনে আনলো।’ সাপ তার গোটা বামহাত পেঁচিয়ে ধরতে চাইলো, সে মুষ্টিবদ্ধ সাপ আগুনের বেশ ভেতরে ঢুকিয়ে অপেক্ষা করছিলো। ‘প্রায় আধঘন্টা পর পোড়া কাঁচকলার মতো সিদ্ধ সাপ হেমাঙ্গিনী পেট পুরে খেতে খেতে ভাবলো— ভয়ঙ্কর সাহসী হলেই খেতে পাওয়া যায়। এটা শঙখচূড়।’
‘ভয়ঙ্কর সাহসী হলেই খেতে পাওয়া যায়।’—এই বাক্যটি বিশ্বায়নের মহানাগরিক লেখক-ই লিখতে পারেন কারণ ক্ষুধার মানচিত্রের দাগ, খতিয়ান একমাত্র তাঁর পক্ষেই ঠিকঠাক উপলব্ধি সম্ভব।
‘সখিচান’—সখিচানের ডোমের কাজ থেকে বিদায়ের গল্প। স্ত্রী, কন্যা ও বন্ধুরা মিলে বসেছে পানাহার ও গানের আসরে। সখিচান ‘মাসে কম করে দশটা অর্থাৎ বছরে একশো বিশটা লাশ, ট্রেনে কাটা, গাছ থেকে পড়া, ছুরিতে মরা, কারেন্টে শক, আগুনে পোড়া, গলায় দড়ি দেয়া, এন্ড্রিন খাওয়া—কতো মৃত্যুই সে নাড়াচাড়া করলো অথচ মরণ কী বুঝলো না?’ এই মরণ না বোঝা সখিচানকে ঘিরেই গল্পটি ঘুরতে থাকে। মৃত্যু বিষয়ক একটি দার্শনিক গল্প। রূপ, রূপবাসনা অমর, লেখক জানেন, আমাদের জানান— ‘ডাক্তার সাহেবদের পাশে লাশ কাটার সময় তাকে খুব সতর্ক থাকতে হয় কেননা সে মালঝোল খেয়ে থাকে। ভুল কথা যদি বলে ফেলে কখনও। যদি সামান্যও আউট হয়ে যায়, সর্বনাশ! যদি ডাক্তার সাহেব তার উপর অসন্তুষ্ট হয় এই ভয়েই থাকে। তবুও একদিন মদের আবেগে নেশাগ্রস্ত হয়ে মতিভ্রমে কীসব দেখে যা সে করলো তাতে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলো।—ধবধবে শাদা রঙের এক মেয়ে, রূপসী, সদ্যপ্রসূত এক বাচ্চা রেখে এন্ড্রিন খেয়েছে—স্তনযুগলে ফুলে ফেঁপে উঠছে তৃষিত মেঘনা; অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার আহবানে ক্ষেত্রপট থেকে টপটপিয়ে বেরিয়ে পড়ছে অজস্র শ্বেতবিন্দু। হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো সখিচান, ‘রূপ, কী রূপ!’ মরবো তো আমি, তুই ক্যান? লাশ আমি কাটতে পারবো না’ বলে সখিচানের হাউমাউ কান্না— থামায় কে? রাতে দুলারী জিজ্ঞেস করেছিলো, ‘ও তো মাসুম বাচ্চা না (দুলারী জানতো বাচ্চাদের লাশ কাটার সময় সখিচান কষ্ট পায়)। তুমি কাঁদলে কেন?’ সখিচান সাফ জানিয়েছিলো, ‘কেঁদেছিলাম রূপ দেখে। রূপ তো আলো। মরে কেন?’ সখিচান গল্পে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র একটি পাখি যে বসে আছে পিলারের উপর, আগুনের শিখার মতো সে পাখি, ওড়ার দহন নেই নড়ার কাঁপন থাকলেও। সে পাখির কাছে যেতে গিয়েই গল্পের অন্তিম ঘটে যায়, আরেকটি মৃত্যু ঘটে ‘পাখির পায়ের মতো তীক্ষ্ণ অথচ কোমল’ সুরের আবহে।
সুব্রত সেনগুপ্ত একজন দ্বিধাগ্রস্ত যুবক, সাত পৃষ্ঠার এই গল্প এখন চলচ্চিত্রায়িত হওয়ার জন্য অপেক্ষমান। যুদ্ধবিরোধী অথচ হত্যাকারী সুব্রতের এই সংক্ষিপ্ত জীবনের গল্পটি নিয়ে মন্তব্য না করি, এতো সংহত গল্প সম্পর্কে কিছু বলা বিপজ্জনক।
চৌত্রিশ পৃষ্ঠার এক মহৎ উপন্যাসপ্রতিম গল্প ‘চিতার অবশিষ্টাংশ’। সাজাদ নামের এক যুবক একটি শ্মশান ও শ্মশানসংশ্লিষ্ট এলাকায় ঘুরে ফিরে বেড়ায়। নানাজনের সাথে তার কথা হয়। হিন্দু পুরাণের নানা অনুষঙ্গ ও নানা ধরনের মানুষের গল্পকথায় ঠাসবুনোট এই গল্প আলাদা প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে।
সাজাদের ভাবনাটি আসলে লেখকেরই౼ ‘… প্রাচীনকে নিঁখুতভাবে নকল করে কতোদিন? তাদের ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো শিল্প আজ নেই, মূল্যবোধ নেই, কেননা প্রেম নেই, আত্মরূপ আত্মস্থ করার আকাঙ্ক্ষা নেই।’ এই ভাবনা আছে বলেই দক্ষ ভাস্করের মতন ধীরে ধীরে এমন এক ভাস্কর্য নির্মাণ করেন লেখক যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে নেই। ঈশ্বরবিশ্বাস ও প্রেম, যৌনতা ও মানুষে মানুষে সম্পর্ক নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে নানা চরিত্রের মুখ দিয়ে। যেমন একটি প্রশ্ন : ‘… ঈশ্বরের এই আরাধনা আত্মনিমগ্ন করে হয়তো, কিন্তু সমাজ-সংসারের ভেতরে কি আত্মবিস্মৃতি করতে পারে?’ যেমন, অতসী এক হয়ে উঠতে থাকা নারী যে আসলে ‘একটুকরো মিছরি। দাঁতের ভেতরে নিত্য চূর্ণ হতে চায়।’ এমন অনেক চরিত্র, চরিত্রের অন্তর্গত দর্শনের অসংখ্য প্রশ্ন ও অমীমাংসিত রহস্যে গল্পটি… থেমে যেতে হয় বিশেষণ অনুসন্ধানে, হয় না এমন মাঝে মাঝে প্রিয়তম গল্প আত্মার বন্ধুদের ফোটোকপি করে পড়াতে ইচ্ছে করে, এ তেমন গল্প। শ্রেণিদৃষ্টিকোণ আমরা কোনো গল্পেই লেখককে হারাতে দেখি না। একটি জরুরি অংশ উদ্ধৃত করি : ‘দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলোর পাশে কোনো সুন্দর ভবিষ্যতের তত্ত্ব, কোনো বুকভরা ভালোবাসা, নিত্য বেঁচে থাকার জন্যে প্রজেক্ট এমনকি পর্যাপ্ত আপ্যায়নের খরচ যোগালেও কোনোদিনই তাদের সাথে তোমার সত্যিকারের সম্পর্ক হবে না যদি তুমি ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক থেকে না বেরিয়ে আসতে পারো। তুমি সম্মান পাবে, তুমি সম্ভ্রান্ত হবে, তোমার প্রায় ৮০ভাগ চাওয়াই পূর্ণ হবে। নৈতিক আর অনৈতিক বিষয় বলে তোমার জীবনে কিছু আছে কি না তা নিয়ে ভালোমন্দ কেউ প্রশ্ন তুলবে না। মানুষের ভালোবাসাও কিনতে পারো কিন্তু ভালোবাসা নিয়ে যে বিশ্বাস তা তুমি কখনোই পাবে না। মানুষের শ্রেণিবৈষম্য কোনো প্রশ্নেই মানুষকে পারস্পরিক প্রেমিক করে না।’ এবং সেলিম মোরশেদ একজন কবিও, তাঁর একটিমাত্র কবিতার বইয়ের কথা আমরা অনেকেই জানি, সেকারণেই বোধ করি গল্পের শরীরে কবিতা ফুটে ওঠে প্রায়ই। যেমন: ‘খয়েরি আর গাঢ় বাদামি সাতটা পুষ্ট হাঁস গেরিলা ভঙ্গিতে ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে একটা পথ বের করে ঘরমুখো অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে সারি সারি এগোচ্ছে। একটা বাঁক নিতে গিয়ে যখন ওরা কিছুক্ষণ থামে, সাজাদের ভেতরে বলে, আহা! স্বতোপ্রণোদিত মৃত্তিকার সপ্তর্ষি যেন-বা।’
‘চেনা-জানা’- গল্পটি আবু হোসেনের কিন্তু তার কোনো উজ্জ্বল উদ্ধার নেই। সে একলা একজন মানুষ, সন্ত্রাস ও যৌনতার রাজত্বে বসবাস, মানসিক শান্তির কোনো ব্যবস্থা সে করে উঠতে পারে নাই, আমাদের তৃতীয় বিশ্বের একজন রিপুতাড়িত মানুষের মতো।
‘কাজলরেখা’ বাঙালি লোককথার এক চমৎকার পুনর্নির্মাণ। কাজল জানে, জন্মদাগ দু-একজনের চামড়ার তলে থাকে, মরণের সময় দেখা যায়। সে জন্মেছে কি না তার জানা নেই।
চতুর্থ গল্প ‘মৃগনাভি’। জোসেফ আর বিকাশ দুই বন্ধুর, পরস্পরে মিশে যাওয়া কিংবা পরস্পরকে ছিন্ন করবার গল্প কেননা জোসেফ জানে, ‘ সেক্স এমন একটি পয়েন্ট যেখানে ডায়ালেকটিকস স্বয়ম্ভু।’
সেলিম মোরশেদ চাইলে লিখতে পারতেন জনপ্রিয় ঘরানার থ্রিলার গল্প। ‘রক্তে যতো চিহ্ন’ গল্পে একজন চরমপন্থি বিপ্লবীর অন্তর্জিজ্ঞাসা ও আত্মবিলুপ্তি বয়ান লিপিবদ্ধ করা দেখেই আমরা বুঝতে পারি, তিনি পারতেন। বিশু, বন্দী, শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনীতিতে বিশ্বাসী বিপ্লবীর সংসার, নিজের মনের প্রশ্নগুলো যা পার্টিতে কখনোই পাত্তা দেয়া হয়নি, পড়তে পড়তে আপামর বামপন্থি দলগুলোর কথা-ই মনে পড়ে আর মনে পড়ে রবীন্দ্রনাটক ‘রক্তকরবী’-র বিশু পাগলের কথা। কেন মনে পড়ে সে কথা বিশ্লেষণ করে বলতে পারবো না। মন বিশ্রি রকমের জটিল বস্তু, কখন যে কী মনে পড়ে!
‘লাবণ্য যেভাবে এগিয়ে’ গল্পটি স্পষ্টত রবীন্দ্রপ্রণীত লাবণ্যেরই একটি অন্য নির্মাণ। এখানে এমনকি অমিতকেও দেখা যায়। এই লাবণ্যের মা জানেন, সে ‘ফিরোজা আর সবুজের মধ্যবর্তী রঙের সালোয়ার-কামিজ পরলে বৃষ্টি হয়’, অল্প বয়সেই লাবণ্য কলেজের শিক্ষক আর অমিত জানে: ‘একুশ শতক কোক আর কমিকস-এর’, গল্পে আছে নক্ষত্রজগতের কবিতাময় চকিত উপস্থাপন আর দার্শনিক আলোচনা যা তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য।
‘দি পার্ভার্টেড ম্যান’ আমাদের চারপাশের শত শত মানুষের মধ্যের একটি মানুষের গল্প। নৈতিকতা ও যৌনতার চিরন্তন প্রশ্ন আলাপের গল্প। এখানে আমরা একজন প্রেমিকার দেখা পাবো যে শ্যামল মিত্রের সাথে এক রাতের জন্য হলেও শুতে চেয়েছিলো। সাড়ে তিন পৃষ্ঠার চেয়েও ছোটো আয়তনের গল্প ‘নীল চুলের মেয়েটি যেভাবে তার চোখ দুটি বাঁচিয়েছিলো’ একটি রূপক, জাদুবাস্তব গল্প। বিস্তারিত রস আস্বাদন পাঠবিনা প্রাপ্তি অসম্ভব।
‘কান্নাঘর’—বাইশ পৃষ্ঠার গল্প, বইয়ের শেষ। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে। ‘কান্না সমর্পণের পহেলা পথ’– এই বাক্যটিই এ গল্পের মূল কথা। এই খানে লেখক সমর্পিত সত্তা, ‘চিতার অবশিষ্টাংশ’ গল্পের সেলিম মোরশেদ যেমন, এখানে ব্রাত্য লোকায়ত মানুষের ভেতরে ঢুকতে চেয়ে লিখছেন: ‘মানুষ নিজেকে যতোটুকু লুকাবে তার সৌন্দর্য ততোটুকু। প্রকৃতি যেন ঠিক তার উল্টো। যতোটা নগ্ন হবে তার সুরূপ ততোটুকু। বিবর্তিত প্রাণ প্রকৃতির নগ্নতাটুকু আড়াল করে এগোলেই মানুষ, প্রকৃতি মানুষের নগ্নতাটুকু যখন দেখতে পায় তখন ঈশ্বর।’
আপাতত পনেরো বছর পর সেলিম মোরশেদের দিকে, সেলিম ভাইয়ের দিকে, তাঁর গল্পের দিকে যেতে যেতে অল্প বয়সের রাগটুকু ভেঙে যাচ্ছে সশব্দে। তাঁর অক্ষরের সন্ততিদের প্রণাম! ভাবি, যারা তাঁর সাথে পরিচয় করিয়েছিলেন তাঁরা— নিজাম ভাই, জাহাঙ্গীর ভাই আর তারেক মাসুদ আজ আমাদের মধ্যে সশরীর নেই। এই লেখার মধ্য দিয়ে তাঁদের স্মৃতির প্রতিও ভালোবাসা জানাই। তাঁরা এই লেখা দেখলে হয়তো খুশি হতেন।
প্রিয় পাঠিকা, কৃতজ্ঞতা সময় দিলেন, তাই…





