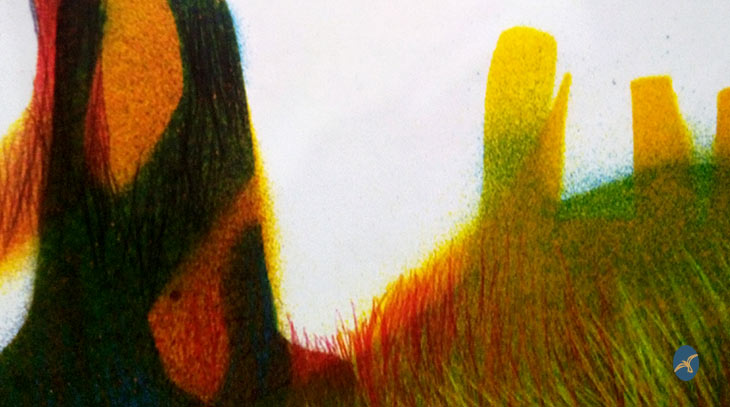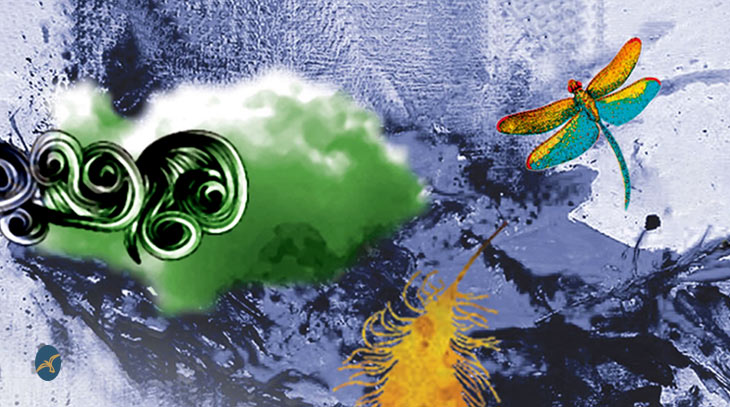একথা সেকথা
কবিতায় সুফিবাদ
শাহবাগে গিয়ে ওপার বাংলার লিটল ম্যাগাজিন দেখছিলাম। ‘যৌথ খামার’ নামে একটি সংকলন [জানুয়ারি, ০৯] ওল্টাতে গিয়ে কৌতূহল বোধ করলাম। ওতে রণজিৎ দাশের একটি সাক্ষাৎকারে চোখ আটকে গেল। লেখাটার শিরোনাম ‘কবিতা মানেই সুফি কবিতা।’
রণজিৎ দাশের কবিতার প্রতি আমার অনুরাগ রয়েছে। তাঁর কবিতার ভেতরে একপ্রকার নিবিষ্টতা আছে। ‘নির্বাচিত কবিতা’র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, ‘কবিতা একটি দৃষ্টিভঙ্গি। যে দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুত, এই মহাজগতে হৃদয়ের অন্বেষণ।’ তাঁর এই উপলব্ধি গভীর সংবেদনশীলতাসম্পন্ন। তাঁর কিছু প্রবন্ধও পড়েছি। বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং ভাবনার গভীরতার কারণে সেগুলো ভালো লেগেছে।
যে-সাক্ষাৎকারটির কথা বলেছি, তাতে তিনি বলেছেন, ‘এটা তো প্রায় অলঙ্ঘনীয় কথা যে সুফি ভাবধারার দ্বারা কোনো না কোনোভাবে প্রাণিত না হলে কবিতাই লেখা বোধ হয় সম্ভব নয়। ফলে আমি মনে করি, এমনকি আধুনিকতম কবি পর্যন্ত সকলের কবিতাতেই সুফির একটা টাচ পাওয়া যাবে। কারণ, সুফি দর্শনের মূল ভিত্তি ব্যক্তিমানুষের ধ্যানস্থ কল্পনা। কাব্য সৃষ্টির মূল ভিত্তিও তাই। তদুপরি মিল রয়েছে আশিক-মাশুকের মিলনতত্ত্বে। যে কারণে সুফিধর্মের একমাত্র প্রবক্তা সুফি কবিরা। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, সুফি সাধনার মতো কাব্য রচনাও একটি মিস্টিক প্রক্রিয়া, একেবারেই ভাবকল্পনার টেকনিক্যাল অর্থে। তাই আজকাল আমি ভাবি যে কবিতা মানেই সুফি কবিতা।’
এখন এই সুফি ভাবধারা বিষয়টি নিয়ে আমরা কিছু কথাবার্তা বলতে পারি। প্রথমেই দেখা যেতে পারে সুফি ভাবধারা বা সুফিবাদ বিষয়টা কী?
সীমিত অর্থে, সুফিবাদ হচ্ছে ইসলাম ধর্মের কাঠামোয় মর্মবাদ তথা আত্মস্বরূপে পৌঁছাবার সরণি। আবার অন্যভাবে বললে, এটি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উপায়।
এই পর্যন্ত লিখেই থমকে যেতে হলো। কারণ, আমরা এমন এক দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থান করছি, যখন বিপুল সংশয়-অবিশ্বাস-বিভ্রান্তি-আবর্
ধর্মের কথা বললেই আধুনিক শিক্ষায় বিদ্বানেরা অনেকেই হয় নাক সিঁটকাবেন, নয় তো সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাববেন, নব্য কোনো মৌলবাদীর আগমন ঘটল নাকি! আবার নির্দিষ্ট কিছু আনুষ্ঠানিক এবাদত ও মোল্লা-কথিত ‘হারাম-হালাল-সওয়াব’-এর মধ্যেই যারা ধর্মের পরিধি আঁকেন, তাঁরা ভাবতে চাইবেন : এসব কথা কি শরিয়তসম্মত, নাকি কোনো ভণ্ডামি বা বিভ্রান্তি?
আধুনিক মানুষেরা অনেকেই আল্লাহ-খোদা-ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না এবং অধিকতর মানুষ সংশয়বাদী অথবা এ বিষয়ে নিস্পৃহ। এর একটি কারণ, সেমিটিক ধারণা যেভাবে প্রচলিত তাতে মনে হয়, আল্লাহ নামক কোনো এক সত্তা (নিরাকার বলা হলেও বোঝা যায়, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন) সাত আসমানের ওপরে বসে মানব ও বিশ্বজগতের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণের খেলায় মশগুল। অথচ একটি হাদিসে কুদসি (সেই হাদিস যার মর্যাদা সাধারণ হাদিসের ওপরে, কোরআনের ঠিক পরই)-তে বলা হয়েছে : আমি ছিলাম গুপ্ত ভাণ্ডারে নিহিত। আমি চাইলাম নিজেকে প্রকাশ করতে, তাই সবকিছু সৃষ্টি করলাম এবং প্রকাশিত হলাম। এই ধারণা ভারতীয় দর্শনের সাথেও মেলে। স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যেই নিজেকে বিবর্তিত করেছেন ‘সিফাত’ বা গুণরূপে আর তার ‘জাত’ বা মূল সত্তা মানবের অন্তরে অবস্থান করে বিশুদ্ধ স্বরূপ বা পরমাত্মারূপে। সুতরাং জাত ও সিফাত মিলে অর্থাৎ বস্তুবিশ্ব, প্রাণবিশ্ব ও চেতনাবিশ্বের সমবায়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে সমগ্রতা, তারই অপর নাম ঈশ্বর-আল্লাহ-খোদা-ভগবান– যা-ই বলি না কেন। বৈদিক ঋষিরা সেই কবেই বলে গেছেন: সত্য এক, ঋষিরা তাকে বিভিন্ন নামে ডাকেন।
তবে এই বিশ্বজগতের বাইরে খোদা নেই? থাকতে পারে। কিন্তু অতিবর্তী সে ঈশ্বরকে আমরা বিজ্ঞানে পাই না। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এখন অবধি সবচেয়ে অধিক গৃহীত যে মতবাদ, সেই বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুসারে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে এক পরম ক্ষুদ্র বিন্দু, যার নাম এককত্ব বা সিঙ্গুলারিটি তথা তওহিদ, তা থেকে। তার আগে? ‘তার আগে’ বলে কোনো কিছু বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে (এখন পর্যন্ত) নেই, কারণ ত্রিমাত্রিক দেশ ও সময় সৃষ্টি হয়েছে এই বিগ ব্যাং থেকেই ‘তার আগে’ বলে কিছু থাকবে কেমন করে? কাজেই তার আগে যা আছে, তা অবোধগম্য– বুদ্ধি তা জানতে পারে না, কিন্তু মন অনুভব করে যে নিশ্চয়ই তার আগেও ‘একটা কিছু’ আছে।
সেই খোদা, যিনি পরম সত্তারূপে মানুষের ভেতরে বিরাজ করেন। [ধর্মশাস্ত্রের সাক্ষ্য : কোরআন বলছে, ‘আমি তোমার শাহারগের নিকটেই আছি’, ‘আমি তোমার নফসের সঙ্গেই মিশে আছি, তুমি কি দেখছ না’, ‘আমাকে ডাকো, আমি জবাব দেব।’ এবং হাদিস বলছে, ‘মোমিনের হৃদয়ে আল্লাহর আরশ,’ ‘যে নিজেকে চিনেছে, সে প্রভুকে চিনেছে।’ ইত্যাদি।]
তার খোঁজ পাই না কেন? কারণ, আমরা নফসের বশীভূত। বোধগম্য অর্থে, নফস হচ্ছে প্রবৃত্তি-আবেগ-বুদ্ধিবৃত্তির সমগ্রতার সাথে চেতন-অচেতন-নির্জ্ঞান মনের সঙ্গমিত অবস্থা। আসলে প্রাণই হলো নফস। নফস তথা জীবাত্মার কেন্দ্রে আছে ‘আমিত্ব’ বা ইগো। এটি সব সময়েই নিজের চাওয়া-পাওয়া স্বার্থ নিয়ে তাড়িত। সুতরাং আকর্ষণমূলক (কাম, লোভ, মোহ, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা…) ও বিকর্ষণমূলক (ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্ষা, দ্বেষ, ভয়…) মানসিক ভাব ও ভাবনাপ্রবাহে নিমজ্জিত থাকে আমাদের মনোজগৎ। এগুলোকে উসকে দেয় আমিত্ব এবং এরাও প্রভাবিত করে আমিত্বকে। এই আমিত্বর রূপকে ধ্যান সাধনার মাধ্যমে চিনে নেওয়ার ও তাকে অতিক্রম করে শুদ্ধ সত্তাকে উদ্ভাসিত করাই সুফির লক্ষ্য। চেতন-অচেতন-নির্জ্ঞান মনের অবস্থাসমূহকে পর্যবেক্ষণ করে এগুলোর বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত হওয়া হলো সুফির আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য। এই আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে তার ‘কাঁচা আমি’ (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) বা ‘ছোট আমি’ (রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভাষায়) ক্রমে ‘পাকা আমি’ বা ‘বড় আমি’তে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ সাধক নফসানিয়াতের শৃঙ্খল হতে রুহানিয়াতের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হন। তার জীবাত্মা বা নফস তখন পরমাত্মা বা রুহের সাথে মিলিত হয়। অর্থাৎ আমিত্বের বন্ধন হতে মুক্ত হলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে অখণ্ড অদ্বৈত রূপ আছে, তা তার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়। সেই অদ্বৈত অবস্থায় সে তার সত্তার মধ্যে পরমকে উপলব্ধি করে, আর সাধক তখনই বলে ওঠে, ‘আনাল হক’, অর্থাৎ আমিই পরম সত্য।
এখন বুঝতে হবে, নমরুদও নিজেকে ‘খোদা’ বলে দাবি করেছে, আবার মনসুর হাল্লাজও তা-ই বলেছেন। ব্যাকরণের দিক থেকে দুটো বাক্যই এক ও অভিন্ন। কিন্তু তাৎপর্যের দিক থেকে একজন বলেছে আমিত্বের বাসনায় ক্ষমতার দম্ভে, আর অন্যজন বলেছেন হৃদয়ে পরম সত্তাকে অনুভব করে। সুতরাং আপন আপাতখণ্ডিত সত্তায় তথা অন্তরে পূর্ণ সত্তাকে অনুভব করাই একজন সুফির আকাঙ্ক্ষা। এই অনুভবের মাধ্যমে সে দৈনন্দিন অহংকেন্দ্রিক ভোগলিপ্সার জগৎ হতে দিব্য, আনন্দময় প্রজ্ঞা ও প্রেমের রাজ্যে অধিবাসী হন।
প্রেমের বিষয়টা কীভাবে এল? প্রেমকে তো আসতেই হবে। কারণ, সুফির প্রধান অবলম্বনই প্রেম। পরমের জন্য তার আকুতি। যিনি পরমকে লাভ করেছেন, তিনি তো বিমূর্ত পরমের বাস্তব প্রতিরূপ। এমন একজন মানুষকেই গুরু হিসেবে বরণ করতে হয়। কেন মানতে হবে গুরু? উত্তর পাই রবীন্দ্রনাথে। গুরুদেব লিখেছেন যে একটি হালের অধীনতা স্বীকার না করার অর্থ লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের দাসত্ব করা। এই গুরুর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয় এবং তার নির্দেশিত সাধন-ভজন করতে হয়; কারণ,
‘সর্ব সাধন সিদ্ধ হয় তার
ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার।’
এই প্রেম জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্কের বাইরের বিষয়। এই প্রেমের চর্যার মাধ্যমেই সুফি মানবিকতার উচ্চতর পর্যায়ে আরোহণ করেন, তিনি অসাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠেন, সৌভ্রাতৃত্বের বোধে সিক্ত হন, সর্বজনীন হয়ে ওঠেন।
কিন্তু এর সাথে কবিতার সম্পর্ক কী? হ্যাঁ, সেই সম্পর্কের কথাই বলেছেন রণজিৎ দাশ। প্রক্রিয়াগত মিল। সুফিকে ধ্যানসাধনা করতে হয়। ধ্যানসাধনার মাধ্যমে সে নিজের চেতনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। নিজের মনকে সে দেখে। নিজের ভাবনারাশি ও ভাবসমূহকে সে দেখে। অবচেতনাকে সে দেখে। নির্জ্ঞান হতে উঠে আসা বিষয়গুলোকে সে দেখে। অজস্র চলচ্চিত্রের মধ্যে সে অবস্থান করে। ঠিক এইখানে কবি ও চিত্রকরদের জন্য অসীম সম্ভাবনার জগৎ রয়েছে। এখানে কল্পনাকে খেলতে দেবারও অবকাশ আছে। এ হচ্ছে সৃজনের প্রক্রিয়ার খুব নিকটে পৌঁছে যাওয়া।
জালালউদ্দীন রুমির পীর শামসে তাবরিজ বলেছেন: ‘আমি ইহুদি নই, খ্রিস্টানও নই, অগ্নি উপাসকও নই, এমনকি আমি মুসলমানও নই।’ সুফি যখন সত্য লাভ করেন, তখন তিনি সর্বজনীন হয়ে ওঠেন। তিনি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় সাইনবোর্ডের নিচে আর থাকেন না। তিনি ধর্মকে অতিক্রম করে যান। আর তাই তো ‘সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।’
এ হলো সৃজনক্ষেত্রে ধ্যানকে ব্যবহার করার সামান্য বক্তব্য। আর সুফি দৃষ্টিভঙ্গি যে দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি এ লেখার শুরুর দিকে বলেছি ‘ইসলাম ধর্মের কাঠামোয় মর্মবাদ’, সেটা আসলে একই সঙ্গে একটি ধর্মীয় ও ধর্মোত্তর ভাবধারা।
আবার সুফি ভাবধারা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে একটি সর্বকালীন ও সর্বজাতিক দৃষ্টিভঙ্গি। দেশ-কাল-সমাজ-সংস্কৃতিভেদে কেবল তার নাম ভিন্ন হয়। এই হেতু যে-কোনো ধর্ম কাঠামোয় আত্মদর্শনের ধ্যানপন্থী ধারাকেই সুফিবাদ বলা যেতে পারে। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এই অর্থে চর্যাপদের কবিতা সুফিবাদী, নাথপন্থী কবিতা সুফিবাদী, বৈষ্ণব কবিতা সুফিবাদী, শাক্ত কবিতা সুফিবাদী, রবীন্দ্রনাথ সুফিবাদী, নজরুল ইসলাম সুফিবাদী, ডিএল রায়-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ সুফিবাদী, ফকির-বাউল-কবিরা সবাই সুফিবাদী। যে-কেউ এ ধারায় কবিতা লিখেছেন, তিনিই ওই পরপ্রেক্ষিতে কবি হিসেবে সুফিবাদী। আবার যে-কোনো কবিই কোনো না কোনো সময়ে সুফিবাদী হয়ে উঠতে পারেন। শামসুর রাহমান যখন লেখেন :
‘বুক পাঁজরের ঘেরা টোপে
ফুচকি মারে আজব পাখি।’
কিংবা
‘বৃক্ষের নিকটে গিয়ে বলি :
দয়াবান বৃক্ষ তুমি একটি কবিতা দিতে পারো?
বৃক্ষ বলে, আমার বাকল ফুঁড়ে আমার মজ্জায়
যদি মিশে যেতে পারো, তবে
হয়তো বা পেয়ে যাবে একটু কবিতা।’
তখন তিনি সুফিবাদী। কিংবা মাসুদ খান যখন এক বন্ধুর স্মৃতিতে উদ্বেল হয়ে ওঠেন অথবা ‘দূরের গ্রহে বসে’ কবিতা লেখেন, তখন তিনিও সুফিবাদী। তবে এসব প্রকাশ আংশিক ও সাময়িক।
সুফিবাদ একটি উচ্চতর মানবিক ভাবধারা। পরম সত্তা এখানে মনের মানুষ হিসেবে মানুষের মধ্যেই বিরাজ করেন। সমস্ত সৃষ্টিজগৎ সেই সখারই বিচিত্র প্রকাশ। এখানে পরিবেশবাদীর জন্যও ভাবনার উপাদান আছে। সকল মানুষ পরস্পরের ভাই। সমস্ত সৃষ্টিজগৎ ব্যক্তির অবিভাজ্য অংশ। বিচ্ছিন্নতাবোধ হতে মুক্তির একটি উপায় হলো সুফিবাদ।
এই মানবিকতার যদি বিকাশ হয়, তবে সামাজিক অর্থে যেমন তা কল্যাণকর, তেমনি সৃষ্টিশীলতার জন্যও তা ইতিবাচক। সুফিবাদের মধ্যে রুমি, হাফিজ, সাদি, জামি, আত্তার, খৈয়াম, ইকবাল, মীর তকি মীর, আবদুল লতিফ ভিটাই, বুল্লে শাহ, আমির খসরু প্রমুখ ধ্রুপদি কবিদের নাম যেমন আছে, তেমনি সুফিবাদের পরিধিতে মনসুর হাল্লাজ, রাবেয়া বসরি, বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী, বু আলী শাহ কলন্দর, শেখ ফরিদ এবং এ রকম আরও অনেকেই কবিতায় প্রকাশ করেছেন আধ্যাত্মিক সত্য ও সৌন্দর্য। এ দেশের সুফি কবিরাও কবিতার ব্যাপক ঐতিহ্য রেখে গিয়েছেন।
এ কালের বাংলা কবিতার দিকে তাকালে দেখতে পাই, ত্রিশোত্তর কবিতায় আধুনিকতার অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ভাবদর্শন পাল্টে গিয়েছে; কবিতা তখন বিদগ্ধ হয়ে উঠেছে; বিষয়বস্তুতে, প্রকরণে ও শৈলীতে আধুনিকতাবাদ সাড়ম্বরে প্রবেশ করেছে। কবিতা অবশ্য বিদগ্ধ হয়ে উঠেছিল অনেক আগেই আর তা হবেই : লোকসাহিত্য আর নাগরিক সাহিত্য এক রকম হয় না। রবীন্দ্রনাথ এলিট অবশ্যই। মধুসূদনও। কিন্তু ত্রিশোত্তর কবিতা উল্লম্ফন। তবে ত্রিশের কবিতাকে যতখানি উন্মূল বলে নিন্দা করা হয়, তা বোধ হয় নয়। সম্প্রতি সৌভিক রেজা ‘ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতায় অধ্যাত্মচেতনা’ নামে একটি গবেষণামূলক বই লিখেছেন। এর উপসংহারে তিনি বলেছেন : “আধ্যাত্মিকতা জীবনের কিংবা শিল্প-সাহিত্যের বিপরীত কোনো বস্তু নয়। আর ভারতীয় সংস্কৃতিতে তো এটি নির্দিষ্ট কোনো ধর্মবিশ্বাসের ফল নয়; বরং এটি হচ্ছে মানবীয় চৈতন্যের অন্তর-অনুভূতির বহুমাত্রিক প্রকাশ। যার কারণে এখানে আত্মজ্ঞানকে, আত্মশুদ্ধিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এসবের শুরু অবশ্য আত্মজিজ্ঞাসা থেকে। আর এই আত্মজিজ্ঞাসা থেকেই আত্মোপলব্ধির জন্ম। আত্ম-আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে যে পথ চলা শেষ পর্যন্ত একটি পরিপূর্ণতা অর্জন করে। এই পরিপূর্ণতার মধ্যে রয়েছে সত্তার সারাংশ, মানুষের অন্তরস্থ সর্বসত্তা। এই পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য মনের দিক থেকে শ্রেয়োবোধের প্রাধান্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন জীবনের শাশ্বত সত্যকে আবিষ্কারের চেষ্টা। এই সব প্রচেষ্টাই আমরা বিভিন্নভাবে দেখতে পাই আমাদের আলোচিত পাঁচ কবির কাব্যে, তাঁদের জীবনচেতনায়।’
তারপরও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, ‘চর্যাপদ’ থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং তারপরও নজরুল ইসলাম ও ডিএল রায়-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্ত প্রমুখের আধ্যাত্মবাদী রচনা পর্যন্ত যে সাবলীল ভাবধারা প্রকাশ পেয়েছে, তা এই সময়ে নেপথ্যে চলে গেছে।
বাংলাদেশের কবিতায় বিভাগপূর্ব কালেই চল্লিশের দশকের শুরুর দিক থেকে রাজনৈতিক প্রণোদনায় ইসলামি জাতীয়তাবাদের ধারা শুরু হয়, যার প্রধান নায়ক ছিলেন ফররুখ আহমদ।
তিনি অবশ্যই শক্তিশালী কবি। কিন্তু অচিরেই রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়; পাকিস্তানি ইসলামি জাতীয়তাদের ওই ধারা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফররুখ আহমদ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অসহায় শিকার হয়ে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ‘অনাহারে-অর্ধাহারে বিনা চিকিৎসায় মারা যান।’ (এ প্রসঙ্গে ব্রাত্য রাইসু চমৎকার একটি প্রবন্ধ লিখেছেন সম্প্রতি। তাঁর রচনার নিস্পৃহ ভঙ্গিটি লেখাটিকে অসাধারণ করেছে।)
তিনি (ফররুখ আহমদ) অবশ্যই শক্তিশালী কবি। কিন্তু অচিরেই রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়; পাকিস্তানি ইসলামি জাতীয়তাদের ওই ধারা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফররুখ আহমদ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অসহায় শিকার হয়ে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ‘অনাহারে-অর্ধাহারে বিনা চিকিৎসায় মারা যান।’
৪০-এর আহসান হাবীব, আবুল হোসেন এবং পরিবর্তিত সৈয়দ আলী আহসান থেকে শুরু করে ৫০ ও ৬০-এর দশকের কবিতায় জাতীয়তাবাদের আবেগে বাংলার ঐতিহ্য ও ভাবাদর্শের অনেক উপাদান-উপকরণ প্রবেশ করে। এ নিয়ে আলাদা গবেষণা হতে পারে। কিন্তু তা কখনো সাহিত্যিক উল্লেখ হিসেবে, কখনো আবেগ প্রকাশের উপকরণ হিসেবে এসেছে; পরিপূর্ণ দার্শনিকতা নিয়ে তা আসেনি।
তবে একটু ব্যতিক্রম আছে। ষাটের দুজন কবিকে নিয়ে কিছু বলবার আছে। আমার সাম্প্রতিক কবিতার বই ‘মগ্ন তখন মোরাকাবায়’-এর গৌরচন্দ্রিকায় আমি লিখেছি, ‘আধ্যাত্মিক ধারার চেতনাপ্রবাহ এখনো একেবারে হারিয়ে যায়নি বাংলা কবিতা থেকে। সাম্প্রতিককালে, উদাহরণস্বরূপ ‘’এবাদতনামা’’ ও ‘’সকল প্রশংসা তাঁর’’-এর মতো কবিতামালায় তার প্রকাশ, তা সে যে-যে মাত্রায়ই হোক না কেন, আমরা দেখতে পাই।’ এই উক্তিটিকে এখানে একটু বিশদ করতে পারি। ১৯৯০ সালে বই আকারে প্রকাশ পায় ফরহাদ মজহারের কবিতার বই ‘এবাদতনামা’। তখন থেকেই এই বইটি আমার খুব প্রিয়। যতবার আমি এটা পড়ি, ততবারই নতুন করে আনন্দ পাই। যখন প্রথম বইটি পড়ি, সে সময় আমি নাস্তিক্যবাদী ছিলাম। কিন্তু তখন যেমন আনন্দ পেতাম, এখন সুফিবাদী বীক্ষায় নিষিক্ত হবার পর সেই আনন্দ না কমে বরং বেড়েছে। এ গ্রন্থকে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে আমি মনে করি। এ গ্রন্থ থেকে বাংলা কবিতায় নতুন একটি ধারা সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব অন্তত পরবর্তী কবিদের অনেকভাবে প্রাণিত করতেই পারে।
তবে এই বইকে পড়তে বলা হয়েছে ‘প্রজ্ঞার প্রেমে পড়ে।’ এটা লেখাও হয়েছে সেই অবস্থান থেকেই। তাই ‘এবাদতনামা’র কবিতা প্রধানত বুদ্ধিবাদী। এতে অনেক দার্শনিক মজা আছে, ফাজি লজিক আছে, ধর্মের অনেক অসংগতিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, এতে অনেক পরিহাস রয়েছে। তা ছাড়া সুফিবাদের কিছু উপাদানকে যে সাফল্যে ব্যবহার করা হয়েছে, এই কবিতাগুলোতে সেটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।
কিন্তু তিনি যতই ‘এশক’-এর কথা বলুন, তিনি ভক্তবাদী কবি নন; আত্মসমর্পণের আকুতি নেই তাঁর মধ্যে। তিনি ‘প্রজ্ঞার প্রেমে’র কথা বলেছেন, কিন্তু প্রেমেরও প্রজ্ঞা আছে, সেটা পায় সমর্পিত জন। সেই অর্থে একে অধ্যাত্মবাদের বিপরীত ধারার কবিতা বললেও ভুল হয় না। কিন্তু যে অর্থে আধ্যাত্মিকতা সৌন্দর্যভিসারী, যেই অর্থে তা মানবকেন্দ্রিক, যে অর্থে জ্ঞান অনূদিত হয় কবিতায়, সে অর্থে আধ্যাত্মিকতার বিভা নিশ্চয়ই এ বইয়ের কবিতাবলিকে আলিঙ্গন করেছে।
আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতার বই ‘সকল প্রশংসা তাঁর’ প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে। ফরহাদ মজহারের বইটি প্রকাশ হবার পর সেটি কিছু বিতর্ক সৃষ্টি করে। স্মৃতি থেকে লিখছি, সে সময় সৈয়দ আবুল মকসুদ এক আলোচনায় বলেছিলেন যে, যদি উপযুক্ত কারণ না দেখানো হয়, তবে ওই বইটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। আবদুল মান্নান সৈয়দের বইটিও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ দেশের একজন প্রধান কবিকে আমি বলতে শুনেছি; ‘সে রাজাকার হয়ে গেছে।’ এ রকম সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন চঞ্চল আশরাফ। ‘বাংলাদেশের কবিতা: ষাটের দশক’ শিরোনামের প্রবন্ধে চঞ্চল আশরাফ লিখেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পর্কে, “কিছু অসামান্য কবিতায় বাংলা ভাষার ঋদ্ধি ঘটিয়ে নিজের পতন স্পষ্ট ও নিশ্চিত করে রেখেছেন ‘সকল প্রশংসা তাঁর’ লিখে: রবীন্দ্রনাথ যেমন হারিয়ে গিয়েছিলেন জীবনদেবতায়, কিন্তু তিরিশি কবিদের সম্মিলিত মোচড় তাকে ফিরিয়ে এনেছিল ওই কুসংস্কার থেকে।”
চঞ্চল আশরাফ আমার স্নেহভাজন; তার মেধাকে আমি শ্রদ্ধা করি; তার গদ্য ঋজু ও সাবলীল; কিন্তু ইদানীং লক্ষ করছি, শিল্প-সাহিত্যের মতো বিষয় নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে চরমপন্থী মতামত প্রকাশ করেন : এটি সাহিত্যিক মৌলবাদিতার লক্ষণ; এই প্রবণতাটি স্বাস্থ্যকর নয়। তো যাকে তার কুসংস্কার বলে মনে হয়, তাকে অবিশ্বাস করাটা মডার্নিস্ট সিনড্রোমের একটি উপাদান। রণজিৎ দাশ তাঁর সাক্ষাৎকারটিতে এই বিষয়ে বলেছেন, ‘আধুনিকেরা মনে করেন ঈশ্বর নেই। আপাতভাবে আমিও তাই মানি, কিন্তু আমি সৃষ্টিরহস্য নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে বুঝেছি যে, বিজ্ঞান এটা বলে না যে সৃষ্টির পিছনে কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। এটা সম্পূর্ণ আধুনিক মানুষের ভুল ধারণা।’ যাকে চঞ্চল আশরাফ কুসংস্কার বলে ভাবছেন, তাকে উপলব্ধি করতে হলে প্রয়োজন হয় ‘হৃদয়ের চোখ’-এর। আলোচ্য বইতে আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন: ‘তাঁকে পেতে হলে, প্রিয়, মুক্ত করো তোমার হৃদয়।’
কুসংস্কার হোক বা সত্যদর্শন হোক, সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষণীয় যে উপাদানটি সাহিত্যের রস সৃষ্টিতে সফল হয়েছে, না হয়নি; পাঠকের সংবেদন তা স্পর্শ করছে, না করছে না; আর এ বিষয়টির কোনো পরম মানও নেই; পাঠকই শেষ মানদণ্ড।
‘সকল প্রশংসা তাঁর’কে অনেকে আবদুল মান্নান সৈয়দের পূর্বাপর কবিতার ধারায় উটকো বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে এই ভাবধারা অনেক আগে থেকেই আছে। ১৯৮২-৮৩ সালে ‘আমার বিশ্বাস’ শিরোনামের প্রবন্ধগুচ্ছ লিখলেন তিনি, ত্রিশোত্তর বয়সে। এ বই থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিই:
* মননই জানিয়ে দিয়েছে, মননের পথে মুক্তি নেই,
মুক্তি হৃদয়ের রাস্তায়।
* লেখাও সাধনাসাপেক্ষ…অর্জন করার পদ্ধতি একটিমাত্র : ধ্যান। লেখককেও (গদ্য-লেখককেও) হতে হয় ধ্যানী।
* ঐ অজ্ঞাতের উদ্দেশে আমার কল্পনা ছুটে যেত।
* সব কবিকেই ব্যক্তিগত তমসা থেকে নিষ্ক্রমিত হতে হয় ব্যক্তিগত সূর্যের উদ্দেশে।
* আমি বাঙালি এবং আমি মুসলমান।
* আমি দেশের অতীত, আমি ধর্মের অতীত।
* আমাকে অনেকেই আধুনিক বলে ভুল করেন; আমি আসলে আধ্যাত্মিক।
* আমি অসীমের কণ্ঠস্বর।
* আমি প্রিয় বাক্য বলতে চাই না। আমি সত্য বাক্য বলতে চাই।
* আমার আরাধ্য স্থিরতা। আমি চাই ধ্যান।
* শুধু কর্মেই আমার অধিকার। ফলে নয়।
‘সকল প্রশংসা তাঁর’ গ্রন্থের কবিতা সাত্ত্বিক রসে সিক্ত। সম্প্রতি একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে আবদুল মান্নান সৈয়দকে আমি লিখেছিলাম যে তার যৌবনে এক ‘সু’, সুররিয়ালিজম, তাকে দিয়ে সোনা ফলিয়েছে; এই উত্তর বয়সে অপর এক ‘সু’, সুফিবাদ, তাকে নতুন মাত্রায় সৃষ্টিশীল করতে পারে। আমার মনে হয় এ বইয়ের পর আবদুল মান্নান সৈয়দের আরও অগ্রসর হবার সুযোগ আছে।
আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতার বই ‘সকল প্রশংসা তাঁর’ প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে। ফরহাদ মজহারের বইটি (এবাদতনামা) প্রকাশ হবার পর সেটি কিছু বিতর্ক সৃষ্টি করে। স্মৃতি থেকে লিখছি, সে সময় সৈয়দ আবুল মকসুদ এক আলোচনায় বলেছিলেন যে, যদি উপযুক্ত কারণ না দেখানো হয়, তবে ওই বইটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। আবদুল মান্নান সৈয়দের বইটিও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ দেশের একজন প্রধান কবিকে আমি বলতে শুনেছি; ‘সে রাজাকার হয়ে গেছে।’
আর একজন সম্পর্কে কিছু না বললে খুবই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি আল মাহমুদ। ‘সোনালি কাবিন’-এর কবি আল মাহমুদ একসময় ‘ইসলামি’ ঘরানায় অভিষিক্ত হলেন। কিন্তু তিনি সুফিবাদের দিকে যাননি। যদি যেতেন, তবে তাঁর হাতে আমরা অসামান্য উপহার পেতাম। আল মাহমুদ সম্পর্কে চঞ্চল আশরাফ বলেছেন, ‘পতনের উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে রয়েছেন আল মাহমুদ, যার পরিত্রাণের কোনো সম্ভাবনাই নেই।’ আমি এতখানি নৈরাশ্যবাদী নই। রহমতের দরজা কখনোই চরম বন্ধ হয়ে যায় না। আল মাহমুদ একজন খাঁটি কবি। নিশ্চয়ই সুফিবাদের সত্যতা, সৌন্দর্য ও সম্ভাবনা তিনি অনুভব করতেও পারেন।
গত কয়েক দশকের কবিতার দিকে তাকালে দেখা যায়, ৭০ দশকের আবেগ-উচ্ছ্বাস-ভাবালুতা ও স্টেটমেন্টধর্মিতার পর গত তিন দশকের কবিতায় বাংলা কবিতার দার্শনিক ভাবধারার কিছু কিছু কখনো প্রকাশ পেলেও পত্রপত্রিকা খুললেই দেখা যায়, এখন কবিতার প্রধান প্রবণতা হচ্ছে শব্দ ও রেটরিকের নানাবিধ খেলাধুলা, কসরত, কলাকৈবল্যবাদ আর অন্যদিকে প্যাঁচাল, প্রলাপ ও ঠাট্টা-মশকরা-ইয়ার্কি। এসব কবিতা পাঠকের মনে কিছুই উৎপাদন করে না বিরক্তি ছাড়া।
আমার এ বক্তব্য অবিশ্যই সরলীকৃত। প্রচুর ব্যতিক্রমও আছে এবং মাঝে মাঝেই হৃদয়ছোঁয়া কোনো কোনো কবিতা সমকালীন কোনো কোনো কবির কাছে পাওয়া যায়। কিন্তু তা বেগবান ধারা না হবার প্রধান কারণ হচ্ছে, যাকে বলে ভাবসম্পদ, তার নিদারুণ ঘাটতি। আর জীবনদর্শন না থাকলে এমন হওয়াই সম্ভব। জীবনদর্শন একটি ভাবগত সার্বিক বিষয়, যা কেবল বুদ্ধিবৃত্তির বা খণ্ডকালীন চর্চার অবলম্বন নয়, বরং সার্বক্ষণিক যাপন ও অনুভবের সাথে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো মিশে যাওয়া একটি বিষয়। আর এ রকম কোনো ভাবধারা না থাকলে কবিতা ঋদ্ধ হয় না।
বেশ কিছুকাল ধরে বাঙালির দর্শন নিয়ে ভাবা হচ্ছে, বাঙালির ভাবান্দোলনের সূত্র খোঁজা হচ্ছে, বাংলা কবিতাকে মূলধারার সাথে পুনর্যোজিত করার প্রয়াস পাচ্ছে। নানা রকম তত্ত্ব ও তৎপরতা প্রকাশ পাচ্ছে। এ রকম পরিস্থিতিতে বাংলার আবহমান ভাবধারার সাথে সংযোগ ফিরিয়ে আনতে (পেছনমুখী হাঁটবার সলা-পরামর্শ হচ্ছে না, পুনরাবিষ্কারের ও সংশ্লেষণের সম্ভবনার কথা বলা হচ্ছে) এবং সমকালীন কবিতার উৎকর্ষ সাধনে এবং ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে গভীরতম মানবিকতার চর্যার জন্য সুফিবাদ একটি উন্মুক্ত দরজা হতে পারে; ভাবাদর্শ বিকাশের জন্য এটি একটি উর্বর ক্ষেত্র হতে পারে; এবং এ সম্ভাবনার নানা রকম অঙ্কুর ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে।
কবিকে সমাজের অ্যান্টেনা হিসেবে দেখেন কেউ কেউ। ঠিকই দেখেন। কারণ, কবিরা সংবেদনশীল। আমাদের সমকালীন কবিদের কারও কারও মধ্যে এই সব ভাবাদর্শের প্রতি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। সরকার আমিন অনুবাদ করছেন লাওৎ-সের ‘তাও তে চিং’; মুজিব মেহদী অনুবাদ করেছেন ‘জেন কাহিনি’, যাকে ‘কোয়ান’ বলে; সাইমন জাকারিয়া এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ করছেন; তার কবিতা-প্রবন্ধ-নাটক-অনুবাদ-উপন্
সুফিবাদ এমন একটি প্রণোদনাদায়ক ও সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র, যা বিভিন্ন মানুষকে আকর্ষণ করে। এ কারণেই যতীন সরকারের মতো বাম ঘরানার লেখক জালালউদ্দীন খাঁর মতো ফকিরের গীতিকবিতা সমগ্র সম্পাদনা করেন, সলিমুল্লাহ খানের মতো ধীমান লেখক লালনকে নিয়ে ডিসকোর্স রচনা করেন, ফরহাদ মজহার বাংলার ভাবান্দোলন সম্পর্কে নানাবিধ রচনা ও তৎপরতায় সক্রিয় থাকেন।
পশ্চিম বাংলায়ও দেখতে পাচ্ছি নানা রকম কাজ হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, মুরারী সিংহের ‘পোস্টমডার্ন ও চর্যাপদ’ বইটির কথা ধরা যেতে পারে।
এসব লক্ষণ দেখে আমার মনে হয়, বাংলা কবিতায় ও বাংলার মানসে অচিরেই সুফিবাদ ভাবাদর্শ হিসেবে এবং সৃজনশীলতার উৎস হিসেবে এবং মানবিক উৎকর্ষের প্রেরণাবিন্দু হিসেবে দেখা দিতে পারে। এই মৌলবাদী অপতৎপরতার যুগে, এই জঙ্গিবাদী নৃশংসতার যুগে, এই সামাজিক-রাজনৈতিক নতুন নতুন সংকটের যুগে, সুফিবাদী ভাবধারার প্রেমবাদী ও চেতনার মুক্তিকামী দর্শন সভ্যতার ও সাহিত্যের শিরায় নতুনভাবে প্রাণরস বইয়ে দিতে পারে। বাংলা কবিতাকে সুফিবাদ বিপুলভাবে ঐশ্বর্যময় করতে পারে।
এখানেই আমার কথকতায় যতি টানব। যার বক্তব্যকে উপলক্ষ করে এতক্ষণ ভাববিস্তার সম্ভবপর হলো, সেই কবি রণজিৎ দাশকে ধন্যবাদ।
১৬ জুলাই ২০১০
নতুনধারা
গত পর্বে পড়ুন- অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক