
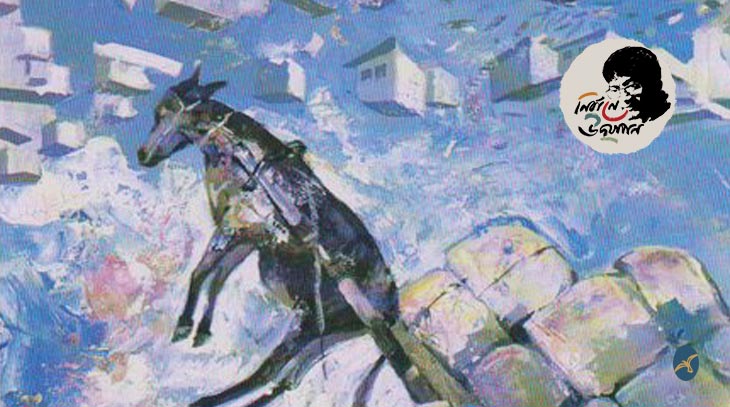
সেলিম মোরশেদের ‘অমায়িক খচ্চর’: কিংবা মতাদর্শভিত্তিক শিল্পাখ্যানের উপাখ্যান
অত্যধিক আত্মকেন্দ্রিকতার কারনে বিশ্বজনীন ভাব উপেক্ষা করে শিল্পী যদি সর্বক্ষণ নিজের ভাবেই বিহ্বল হয়ে থাকেন তাহলে তিনি শিল্পভোক্তার মনের ওপর কোনো রেখাপাতই করতে পারবেন না। শিল্পীর ব্যক্তিচেতনা যতই প্রবল হোক, সামাজিক মানুষ হিসেবে সমাজচেতনার প্রতি তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না।… বস্তুত শিল্পীকে বলা যায় সমাজের প্রতিভূ, সমাজের হৃৎস্পন্দন তাঁর শিল্পকর্মে সমধিক স্পষ্ট অনুভূত হয়। তিনি সমাজের দ্বারা প্রভাবিন্বত হন আবার সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তারও করেন। সর্বসাধারণের বিশৃঙ্খল ভাবগুলো তাঁর শিল্পকর্মে সুসম্বদ্ধ হয় এবং তখন লোকে যেন নিজেদেরই ঠিকমতো চিনতে পারে। প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী অবশ্য শুধুমাত্র সমাজের মুখপাত্র নন। সমাজমনের ভাবগুলো ব্যক্ত করলেই তাঁর কর্তব্য সমাধা হয়ে যায় না। কারণ সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের চিত্তজয়ই শিল্পের স্থায়িত্বের পক্ষে যথেষ্ট নয়। শিল্পীকে সময় তথা কালেরও ‘হৃদয় হরণ করতে হয়’ এবং সে উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে তাঁকে স্বধর্মনিষ্ঠ হতে হবে অর্থাৎ অনায়াসলভ্য খ্যাতির মোহ ত্যাগ করে শিল্পসত্য অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। শিল্পীর পক্ষে ব্যক্তিচেতনা অথবা সমাজচেতনা কোনোটিকেই বেশি প্রশ্রয় দেওয়াটা শোভন পরিণতি হিসেবে দেখা দেয় না। সমাজর সঙ্গে পরিপূর্ণ অসহযোগ এবং পরিপূর্ণ সহযোগ─ দুইয়েরই ফল মূলত অভিন্ন। প্রথম ক্ষেত্রে ভাবসঞ্চারণের সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে ভাব সঞ্চারিত করে তার সঙ্গে রসের কোনো সম্পর্ক থাকে না। ─ ফরীদুল আলম, শিল্পের দর্শন: ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিরই দ্বারা।
১.
শিল্প-সাহিত্যের দার্শনিক ভিত্তি থাকলেও স্বতন্ত্র দর্শন বিদ্যমান। প্রাণধর্মের অনুশাসন থেকে মুক্তির নিমিত্তে দুটি পথের সন্ধান মানব করতে পেরেছে౼ দর্শন ও শিল্পকলায়। দর্শন বিশুদ্ধ concept সমূহের মধ্যে অন্তঃসঙ্গতি নিয়ে কাজ করে, আর শিল্পীর দেন-দরবার image-কে ঘিরে। শিল্পের উদ্দেশ্য কোনো ধর্ম নীতি-বোধের প্রচার নয়, তবে প্রমাণিত যে শিল্পের মূল্য (value) অনেক পরিমাণেই নৈতিক মানবেতিহাস আমাদেরকে সেই শিক্ষাই দেয়।
এই মূল্যসাপেক্ষ শিল্পচর্চার যৌক্তিকতম দার্শনিক ভিত্তিভূমি লিটল ম্যাগাজিন মুভমেন্ট, সেলিম মোরশেদ এমনটাই মনে করেন, অভিজ্ঞতার নিরিখে আমরা সেটাই দেখেছি। যেহেতু তিনি শিল্পী, তাঁর ভাষায় ‘আমার স্বক্ষেত্র গদ্য’(পৃ.১৭)౼তাই তাঁর ভাবনাচিন্তাতে দার্শনিক বিশুদ্ধতা সর্বক্ষেত্রে খুঁজতে যাওয়া তেমন কাজের কথা নয়। কেননা শিল্পীর মন তো মরুভূমিতে পানির উচ্ছল ঝরনাধারা দেখতে চাইতেই পারে। দার্শনিক নির্মোহতায় আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে কেন সেখানে পানির এত অভাব, তারপর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এর প্রতিকারে সচেষ্ট হওয়াই কাজের কথা। এরপরও আমরা সেলিম মোরশেদের লিটলম্যাগাজিন সংক্রান্ত ভাবনাগুলো বিস্তারিত দেখে নেব, কেননা আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি তাঁর এই ভাবনা তিনি যথেষ্ট পরিমাণ সৎভাবে ভাবতে সচেষ্ট এবং দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি এই ভাবনা ও এর নিরিখে কর্ম-তৎপরতায় নিয়োজিত রয়েছেন।
তাঁর মতে౼
…আশির দশক থেকে বাংলাদেশে শক্তিশালী অর্থে লিটলম্যাগাজিন মুভমেন্ট শরু হয়, যার পেছনে ছিলো রাজনীতিক বিশৃঙ্খলা, সামাজিক শাসন, ধর্মীয় উন্মাদনা, ভৌগোলিক বিবর্তন, দুর্বৃত্ত পুঁজির ভারসাম্যহীনতা এবং মাতৃভাষা-কেন্দ্রিক স্মরণীয় কিছু ঘটনাপ্রবাহ। ঐতিহাসিক এই বিবর্তনগুলোর কারণে বাংলাদেশের লিটলম্যাগাজিন মুভমেন্ট এতো সক্রিয় আর শুদ্ধ হয়ে হলো রূঢ় আর বিশ্লেষণাত্মক। আর সেই লিটলম্যাগাজিন মুভমেন্ট অসংখ্য বিষয় ধারণ করে এগিয়েছে, শুধু নান্দনিক দিকটাই দেখেনি রাজনৈতিক মনস্ক লেখাও প্রচুর প্রকাশিত হয়েছে। এই টোটালিটি এবং পূর্বের সকল কাগজের তুলনায় এর স্বাতন্ত্র্য বেসিক দুটি নীতির ওপর থাকে। ১. অন্যায্য মুনাফায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাপক প্রচারিত ছাপা কাগজে না লেখা এবং প্রচার অর্থেই ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে বর্জন করা (তথ্য জানানো অর্থে নয়)। ২. নিজের চিন্তায় আত্মস্থ হয়ে লেখায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। উল্লেখ্য, পশ্চিম বাংলার লিটলম্যাগাজিন-এর একটা পরোক্ষ প্রভাব নিঃসন্দেহে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের লিটলম্যাগাজিন মুভমেন্টকে অনুপ্রাণিত করেছে। রাজনীতির ও অর্থনীতির নব প্রেক্ষিতে ‘৮০-র শেষ দিক থেকে বাংলাদেশের ছোটকাগজগুলোর ভেতর স্ব—চরিত্র-অন্বেষণ প্রবণতা তৈরি হতে থাকে। পরবর্তীকালে অধিকাংশ ছোটকাগজ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে এগিয়েছে। [পৃ. ২০—২২]
…বাণিজ্যসর্বস্ব মিডিয়া বর্জন করে ছোটকাগজে লিখে অস্তিত্ব রক্ষা করা সামষ্টিক স্বার্থে দুরূহ হয়ে ওঠে। … আশ্চর্য অনাদর্শিকতায় কেউ কেউ বড়োকাগজের সঙ্গে যুক্ত থেকে আবার ছোটকাগজও করেন এবং লেখকদের পেছনে পেছনে নিয়ে ঘোরেন। ছোটকাগজ যে একটা আদর্শ, একটা জীবনপ্রক্রিয়া, যার লক্ষ্য সামষ্টিক স্বার্থের প্রশ্নে রাষ্ট্রকাঠামো পাল্টানো, আর তৈরি করা উদ্বৃত্ত পুঁজিহীন প্রতিষ্ঠানবিরোধী কাঠামো, এসবের ধারে কাছে এখানকার লেখকরা নেই। ফলে আমার সঙ্গে অন্যান্য লেখকদের নান্দনিক বিশ্বাসের ঐক্য নেই বরং আছে ব্যাপক ফারাক এবং বিরোধ। আমি প্রতিষ্ঠানবিরোধী একজন লেখক হবার চেষ্টা করি। অনেকাংশে যেটা আমার মেধা-মননে গাঁথা, এক দুর্বিনীত গতি আমাকে সচল করে। প্রকৃত প্রতিষ্ঠানবিরোধী সে-ই, যে যন্ত্র এবং প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত মানুষ হয়েও নিজের বেনিয়াবৃত্তিকে আক্রমণ করে। এক্সপ্লয়েটেশনের বিরোধী হয়— এই সিস্টেমকে সে ঘৃণা করে। যদিও সে সচ্ছল ও পরিচ্ছন্ন জীবনের কামনা করে। [পৃ. ৪৭—৪৮]
আর, তাঁর প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার সংজ্ঞা তিনি নিজেই দিচ্ছেন—
…দুটি পরস্পর বিপরীত মত যুক্তিশাস্ত্র স্বীকার করে না (প্রিন্সিপ্যাল অব ননকন্ট্রাডিকশন)। আবার দুটি বিষয়ের ওপর একটা প্রাধান্য দেয়া ন্যায়শাস্ত্র অনুমোদন করে না (প্রিন্সিপ্যাল অব সাফিসিয়েন্ট রিজন)। আমজনতা বসে থাকে না। সে তার প্রেক্ষিত অনুসারে কাজ করে। কিন্তু যে বিচক্ষণ হতে চায়, শিল্পী হতে চায়, মানবিক মানুষ হতে চায় তার জন্য কী? …এইগুলো নিয়ে আর অসমসমাজে সমসত্তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়া কিছু স্ববিরোধিতা নিয়ে যে নিরন্তর কোশ্চেন, এই টোটাল সবকিছু নিয়ে ভাবনা, যাপন, লেখা আর এই এলোমেলো তৎপরতার শেষমেষ যে যোগফল তা হয়ে ওঠে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা। [পৃ. ২৯—৩০]
সেলিম মোরশেদের শিল্পদর্শনের এই ভিত্তিভূমি বেশ স্পষ্ট। তাই তাঁর সঙ্গে সহমত বা বিপরীত মত পোষণ করা, তাঁর মতের শক্তিশালী কিংবা দুর্বল দিকের অনুসন্ধান করা, যোগ্য আলোচক-সমালোচককের জন্য বেশ সহজ। তিনি নিজেই এক লিখিত বক্তব্যে স্বীকার করছেন ‘…অনেকে হয়তো আমার বিশ্বাসকে অতোটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখেন না’ (পৃ. ৪৯)। আবার কেউ কেউ যে দেখেন তা ও তিনিই লিপিবদ্ধ করছেন রেখো মা দাসেরে মনে-তে (পৃ. ৩২—৩৫)। এখানে তাঁর শিল্পদর্শন বাস্তবায়নে নীতি ও কৌশলের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ হবে তা কিছুটা প্রত্যক্ষে, কিছুটা পরোক্ষে জানিয়েছেন।
সেলিম মোরশেদরা প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার কথা বলেন, দূরবর্তী অর্থে ‘সামষ্টিক স্বার্থের প্রশ্নে রাষ্ট্রকাঠামো পাল্টানো’র কথাও বলেন। একই সঙ্গে কিন্তু ছোট কাগজ নিয়ে বাংলা একাডেমির বইমেলায় অংশগ্রহণ করেন, একাডেমিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেন, কেউ-বা আবার জীবিকার তাগিদে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কাজ করেন। ফলে তাঁদের এই ‘প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা’র মানে প্রতিষ্ঠানকে অস্বীকার করা নয়; বরং প্রতিষ্ঠানের ঋণাত্মক ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করা, অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদিকেই বোধ হয় বোঝায়।
তাঁর শিল্পের দার্শনিক ভিত্তিভূমি’র স্বরূপ আমরা দেখলাম। এইবার তাঁর শিল্পদর্শনটা একটু দেখা যাক।
২.
শিল্প-সাহিত্য জীবনের সমান্তরালে প্রবহমান। কেননা মানুষ শুধুমাত্র জৈবিক প্রয়োজনেই বাঁচে না। তার যাপিত কিংবা কাঙ্ক্ষিত জীবনের চিত্র সে শিল্প-সাহিত্যে তুলে আনতে চায়। এই তুলে আনার প্রকৃতসারে সে কী বলল তার চেয়ে কীভাবে বলল সেখানেই শিল্পের মুন্সিয়ানা। শিল্পের, সৃজনের বিন্যাসে রয়েছে নানা দার্শনিক মতবাদ— অনুকৃতিবাদের বয়স তুলনামূলকভাবে কম তবু সে তাত্ত্বিক পরিণতি লাভ করেছে শ্রেয়তর পূর্বে। শিল্পের মূল্য বিচারেও রয়েছে বিভিন্ন মত— শিল্পের জন্য শিল্প, জীবনের জন্য শিল্প ইত্যাদি। প্রথমোক্ত মতের অনুসারীদের সঙ্গে দ্বিতীয় মতের অনুসারীদের সম্পর্ক যেন অনেকটাই অহি-নকুল। মার্কসবাদী শিল্প-সমালোচকেরা (দ্বিতীয় মত) শিল্পের বিশ্বজনীন ভাবের সঙ্গে যুগধর্মের অভিব্যক্তি বা সমাজচেতনাকে (তাঁরা একে শ্রেণিসংগ্রাম হিসেবে অভিহিত করতেই বেশি সচেষ্ট হবেন) সংযুক্ত করতে চান। ক্ষেত্রবিশেষে এতে ব্যক্তির মানসিক চাহিদা পদ্ধতিতে আরোপিত হয় (সর্বক্ষেত্রে নিশ্চয়ই নয়!), ফলে শিল্পের মূল্যবিচারে গড়বড় বাধে। অনুমিত হয় এই কারণেই নীরেন্দ্রনাথ রায়ের মতো সামর্থ্যবান সমালোচকও ‘মেঘদূত’-এর শিল্পমূল্য বিচারে ক্ষমার অযোগ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছিলেন।
আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শিল্পের সৃজন ও মূল্যবিচারের ব্যখ্যায় কোনো বাদের বাদী নন বলেই প্রতীয়মান হয়। অত্র গ্রন্থে বিভিন্ন Text-এর যে ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন স্থান পেয়েছে তাতে এ বিষয়টি বেশ স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত। অবশ্য লেখক কর্তৃক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নকৃত Text-সমূহের ভেতর যে Text-গুলো বর্তমান লেখকের পাঠ করা আছে তার নিরিখে এই মূল্যায়ন। তাছাড়া তাঁর যে কয়টি বক্তব্য আমাদের আলোচিত Text-এ সন্নিবেশিত আছে ওদের মর্মও আমাদের সিদ্ধান্তের সপক্ষেই কথা বলবে নিশ্চয়ই!
বিভিন্ন Text-এর যে আলোচনা কিংবা মূল্যায়ন তিনি জারি করেছেন সেখানে এক ধরনের Authoritative প্রবণতা বিদ্যমান। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে না গিয়ে সরাসরি সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন; যেখানে Text-গুলো আবার অন্তর্নিহিত গঠনপ্রণালী অনুসারে বহুধা অভিধায় বিভক্ত। কোথাও কোথাও আবার তিনি একটি Text-এর ওপর আলোচনা জারি করতে গিয়ে লেখকের পূর্বে রচিত সমস্ত Text-র ওপর, পরোভাবে সমস্ত লেখককৃতি কিংবা লেখকজীবনের ওপরই মূল্যায়ন করেছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, যাদের ক্ষেত্রে তিনি এরকম ঘটনা ঘটিয়েছেন তাঁরা তেমন অখুশি হবেন না, বরং খুশিই হবেন। কিন্তু যারা কিঞ্চিৎ জ্ঞানতত্ত্ব-এর (Epistemology) অধ্যয়ন করেছেন, এর কিছুটা হয়তো তাঁদের অধিকারেও এসেছে, সুনির্দিষ্ট হয়েছে তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান, সতর্ক হওয়াই বরং তাঁদের জন্য শ্রেয়! কারণ— অত্র Text-এর লেখক একই সাথে একজন সৃজনশীল ব্যক্তি। একজন শিল্পী অন্যের শিল্পকর্মের বিচারে এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রকাশ্যে উপস্থাপনে কতটা নির্মোহ হতে পারেন কিংবা হবেন সে ব্যাপারে নিঃসংশয় হতে জ্ঞানতত্ত্ব বারণ করে বৈকি। এই প্রসঙ্গে আমরা প্লেটোর রিপাবলিক-এর দশম পুস্তক ও শিবনারায়ণ রায়ের কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা’র শরণ নিতে পারি। এখানে ব্যক্তির ক্ষমতা বা তার মানবীয় গুণাবলির চাইতে জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতির ওপর অবস্থা রাখাই শ্রেয়। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয়।
৩.
অত্র Text-এর লেখক সপ্তসিন্ধু-দশদিগন্ত পরিভ্রমণ শেষে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। ফলে তা অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। উপস্থাপিত বক্তব্যে এটা প্রতিভাত যে, তাঁর দেখার মতো চোখও তৈরি হয়েছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দেখে নেওয়া যাক─
…মধ্যবিত্ত চায় একটা ভারসাম্য। ভারসাম্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে একজন পণ্যজীবী। শিল্পী কি পারে? সামাজিক প্রবোধে কত উপলক্ষকে দায়ী করে মূল সত্যকে ঢাকা হয়। [পৃ. ৩৯]
…অন্ধবিশ্বাসের পথ ধরে বড়জোর নিজেকে শুদ্ধ রাখা যেতে পারে কিন্তু ব্যাপ্তির সঙ্গে যুক্ত থাকা যায় না। ঐতিহ্য কখনো একক বিষয় না। পারস্পরিক বিনিময় ছাড়া পৃথিবীর আদি সেরা পাঁচটি সভ্যতারও একক ঐতিহ্য নেই। ব্যাপ্তিময় ঐতিহ্য মানে চারপাশকে আত্মস্থ করা। ইতিহাসে কী দেখি? এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মাবলম্বীকে যতোটা ক্ষতি করেছে, স্বধর্মের নিপীড়ন তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। ইসলামে আছে হাজারটা বাহাস। একমাত্র আবুবক্কর সিদ্দিকী (রা.) ছাড়া খোলাফায়ে রাশেদীনের বাকি তিনজন খলিফাকেই খুন করা হয়েছিলো। নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল সম্মানিত মোহাম্মদের মানবিক মূল্যবোধকে তছনছ করেছে।…স্বধর্মের ভেতর এতো অমিল, একত্রিত হতে পারে না, সেখানে ধর্মের ওপর বিদ্বেষ করা, আধিপত্য করতে চাওয়া কতোটা যৌক্তিক? স্ব-অশিক্ষা থেকে অহম আর আপন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পুরুষতান্ত্রিক দাপট ছাড়া কোন দর্শন কাজ করে? ধর্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চেয়েছে কিন্তু দাপটকে অভিশপ্ত করেছে পদে পদে। [পৃ. ২৪]
এমনকি আরেকটু অগ্রসর হয়ে তিনি বলেন─
…ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ধর্ম, ধর্মতত্ত্ব, ধর্মবিধান কোনকিছুই কমবুদ্ধির মানুষের জন্য প্রযোজ্য না। যেহেতু ধর্মের সঙ্গে তীক্ষ্ণপ্রবণ মনন ও সুগভীর ভাব আছে। ধর্মবিধান, ন্যায়-অন্যায়ের প্রাথমিক স্বচ্ছতাটা একজন নির্মীয়মাণের জন্য হয়তো-বা জরুরি। কিন্তু তার গোটা জীবনের ক্ষেত্রে এটা টোটাল পলিসি হবার অবকাশ যদি থাকে౼ কী ভয়ঙ্কর তা আমরা লক্ষ করেছি। [পৃ. ২৬]
এরকম আরো বেশ কয়েকটি উদ্ধৃতি আমরা চাইলেই নির্বাচন করতে পারব। সময় ও স্থানাভাবে আমরা আপাতত সেটি মূলতবি রেখে তাঁর Way of Re-presentation-টা সাবধানে নিরীক্ষণ করব౼
ক. বক্তব্য উপস্থাপনকালে౼ ক্ষেত্রবিশেষে শব্দের নির্বাচনে তিনি আরেকটু সাবধানী হতেই পারতেন। এতে তাঁর উপস্থাপিত বক্তব্যের way of truth-টাও শ্রেয়তর শক্তিশালী হত। যেমন, ‘বিবর্ণ বাংলাদেশ’ (পৃ. ৬৮) ও ‘দ্বন্দ্ব ও দ্বৈরথে’ (পৃ. ৬৯) শিরোনামের অধীনে লেখা দুটোর ‘সত্য’ ও ‘অলৌকিক’ শব্দদুটোর প্রয়োগ নিয়ে ভাবনা-চিন্তার অবকাশ রয়েছে বৈকি।
খ. কোথাও কোথাও তাঁর উপস্থাপিত বক্তব্যে স্ববিরোধ গোচরীভূত হয়। যেমন: পৃষ্ঠা চুয়ান্নতে তিনি বলছেন ‘একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের সংকেত বহন করা এশিয়ার মানচিত্রে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সফলতা।’ আবার পৃষ্ঠা পঁয়ষট্টিতে তিনি আমাদের জানাচ্ছেন, ‘যুদ্ধোত্তর দশকে বাংলাদেশের কথাসাহিত্য গুটিকয় লেখকের হাতে বাঁক নিয়েছিল… একটি পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবের আপেক্ষিক সফলতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে ক’জন লেখকের অন্তঃমননে…।’ অর্থাৎ এখানে একই ঘটনাকে তিনি-‘পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবের আপেক্ষিক সফলতা’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।
গ. হাতে গোনা দু’একটি ভ্রান্ত সরলীকরণও দৃশ্যমান। যেমন, ‘…সমস্ত যুদ্ধেরই অপর নাম প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা।’ কেউ কারুর ওপর (ন্যাচারাল অথবা লজিকাল যে কোনো Being) অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে সেটা কীভাবে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা হয়?
ঘ. দু’একটি অতিকথনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন: তিনি আবৃত্তিকে মৌলিক শিল্প বলতে চান। কিন্তু জগতের সকলেই জানে এটি স্বনির্ভর শিল্প নয়। যা স্ব-নির্ভর নয় সেটি মৌলিক হয় কিভাবে?
ঙ. নেহায়েত দু’এক জায়গায় নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানের অন্বেষণে তিনি ব্যক্তিক ফ্যান্টাসি কিংবা ফিউশনের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন: বাঙালির নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তির নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি আমাদের জানাচ্ছেন, ‘রিজলী-র মতে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি মোঙ্গলীয় ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে। একাধিক শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিকের মতে আধুনিক বঙ্গজাতির এই পর্যন্ত উৎপত্তি এবং বিকাশ আদি-অস্তাল এবং দ্রাবিড়দের দ্বারা। প্রমাণিত ধারা এই। সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় অবশেষে, দূর থেকে ছুটে আসা আগত এক তাজা ঘোড়া আর লাফ দিতে দিতে এগিয়ে আসা এক কোমল গাধা─ এই দুয়ের সংমিশ্রণে দুর্দান্ত গতিশীল এবং কঠোর আত্মত্যাগ নিয়ে এই ‘অমায়িক…খ’…বা হাজার বছরের বাঙালি এবং তার সত্তা (পৃ. ১৬-১৭)।’
বাঙালিত্বের ধ্বজাধারী রবীন্দ্রনাথ নিজে ‘বাঙালি’ আর ‘মানুষ’ শব্দ দুটিকে সমার্থক মনে করেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বাঙালি নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। আর হাল আমলে হুমায়ুন আজাদ থেকে শুরু করে অনেকেই এই কর্মটি কথায় কথায় সংগঠিত করেছেন। লক্ষ করার মতো বিষয় হল, তাঁরা এটি করেছেন কর্মের নিরিখে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ ‘রবীন্দ্রনাথের’ ‘বিদ্যাসাগর’ প্রবন্ধ থেকে কিয়দংশ দেখে নেওয়া যাক౼
আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; অনুষ্ঠান করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরি পরিমাণ বাক্যরচনা করতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করতে পারি না, আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না, আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তি বিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।
আর আমাদের আলোচ্য Text-এর লেখক বাঙালির কর্মের সাথে তাঁদের ‘নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি’-কে-ও সংযুক্ত করে তার ওপর জারি করেছেন। একজন শিল্পী কিংবা অ্যাক্টিভিস্ট সেটা করতেই পারেন, সে স্বাধীনতা কিংবা অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু আমরা যেন কিছুতেই ভুলে না যাই, মানবজ্ঞানের নির্দিষ্ট শাখার বিশেষজ্ঞরাই ওই বিষয় সংশ্লিষ্ট কোনো ঘটনার বিশ্লেষণে, সিদ্ধান্ত প্রদানে সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি౼ অন্য কেউ নন।
৪.
আশি-পরবর্তী সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহে বিকল্প প্রকাশমাধ্যমে সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সেলিম মোরশেদের ভূমিকায় যেন অনেকটাই Trend Setting Tendency বিদ্যমান। আমাদের আলোচ্য Text হতে জানা যাচ্ছে জনৈক গবেষক ‘বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ’ নিয়ে গবেষণা করে উক্ত Topic-এর ওপর একাডেমি স্বীকৃত দার্শনিক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন, সেখানে তিনি সেলিম মোরশেদের সৃষ্টিকর্মকে বিবেচনায় নিয়েছেন। কিন্তু গবেষক সাহেব যাঁর কিংবা যাঁদের অধীনে গবেষণা করলেন সেই পক্ককেশ পণ্ডিত অধ্যাপকপ্রবরেরা কেন সেলিম মোরশেদদের (তাঁরা সংখ্যায় হাতেগোনা কয়েকজনই হবেন) ব্যাপারে নীরব, নিশ্চুপ! সেলিম মোরশেদরা প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার কথা বলেন, দূরবর্তী অর্থে ‘সামষ্টিক স্বার্থের প্রশ্নে রাষ্ট্রকাঠামো পাল্টানো’র কথাও বলেন। একই সঙ্গে কিন্তু ছোট কাগজ নিয়ে বাংলা একাডেমির বইমেলায় অংশগ্রহণ করেন, একাডেমিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেন, কেউ-বা আবার জীবিকার তাগিদে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কাজ করেন। ফলে তাঁদের এই ‘প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা’র মানে প্রতিষ্ঠানকে অস্বীকার করা নয়; বরং প্রতিষ্ঠানের ঋণাত্মক ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করা, অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদিকেই বোধ হয় বোঝায়। আর তাঁদের সৃষ্টিকর্মের প্রকাশমাধ্যম হিসেবে তাঁরা অন্যায্য মুনাফায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাপক প্রচারিত কাগজে ও বৃহত্তর প্রচার অর্থে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দ্বারস্থ হতে চান না, বরং এর শক্তিশালী প্রতিবাদ জারি রাখতে চান। বিদ্যমান বাস্তবতায় এইসব কথা বলা সহজ, করা কঠিন। কিন্তু যাঁরা দীর্ঘ সময়ব্যাপী কিছুটা ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে হলেও তা করে যাচ্ছেন, তাঁদের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়াটাই যৌক্তিক।
অতএব আমাদের আলোচ্য Text-টি ব্যাপক মানুষের কাছে পৌঁছাক তা চাই, ‘প্রচার অর্থে নয় প্রজ্ঞা অর্থে, প্রমাণ অর্থে নয় স্মরণ অর্থে, মহিমা অর্থে নয় মনন অর্থে।’
মূল গ্রন্থ: অমায়িক খচ্চর, লেখক: সেলিম মোরশেদ, প্রকাশক: প্রতিশিল্প, ঢাকা ২০১১, মূল্য: ১৩০ টাকা
প্রচ্ছদ: ময়েজুদ্দীন লিটন
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১১





